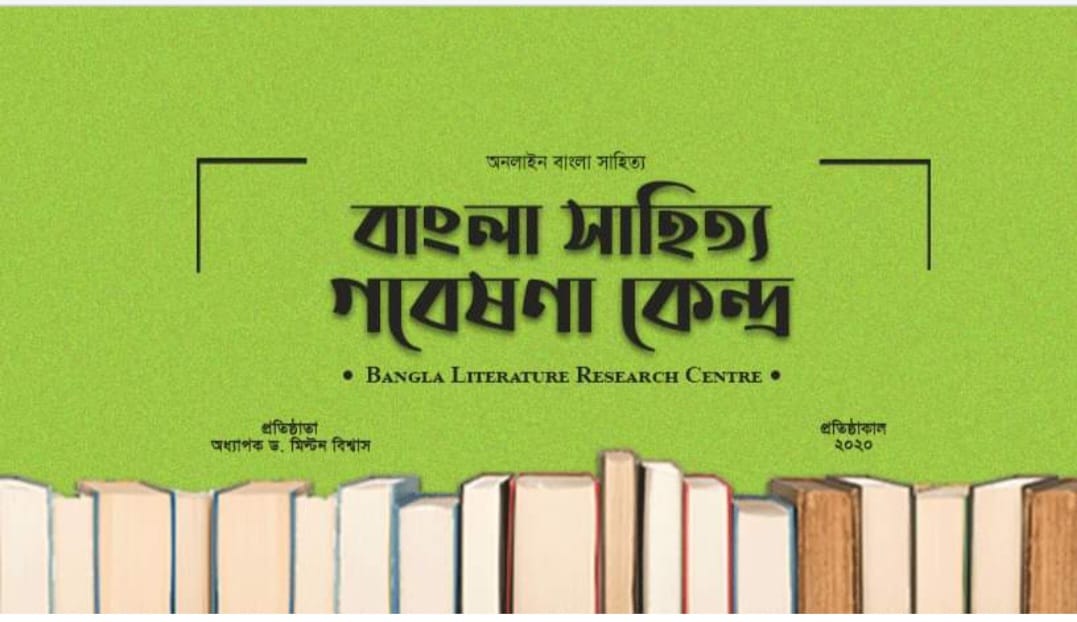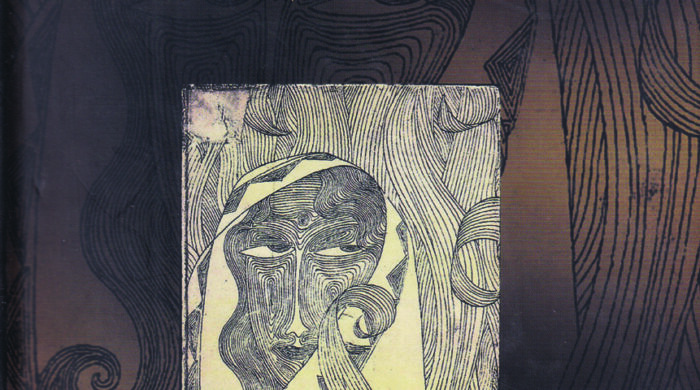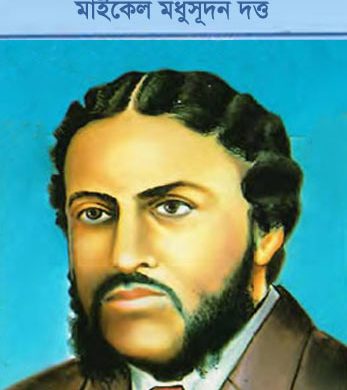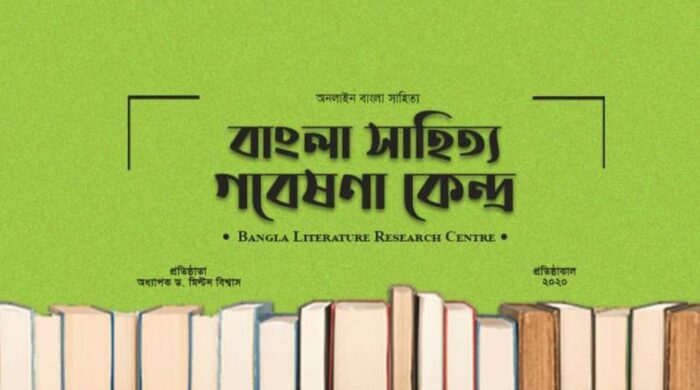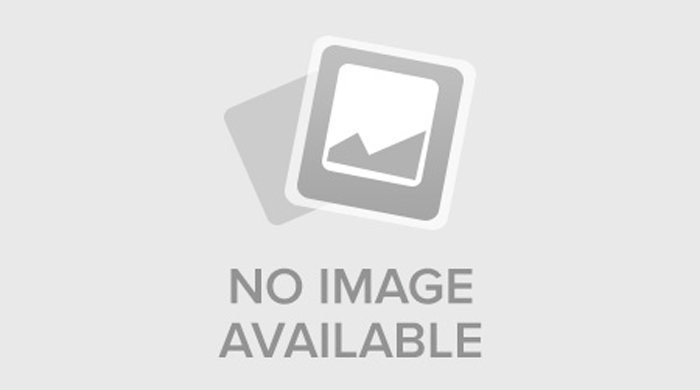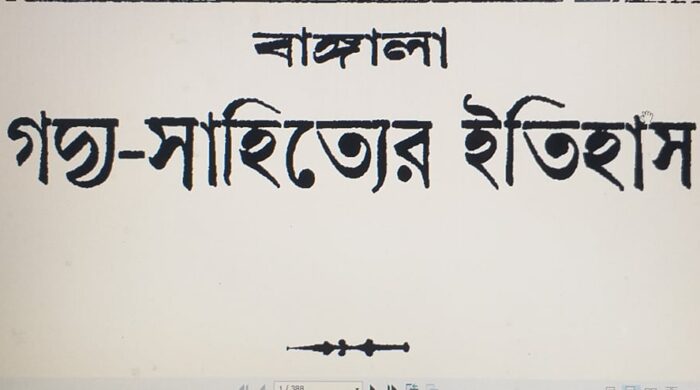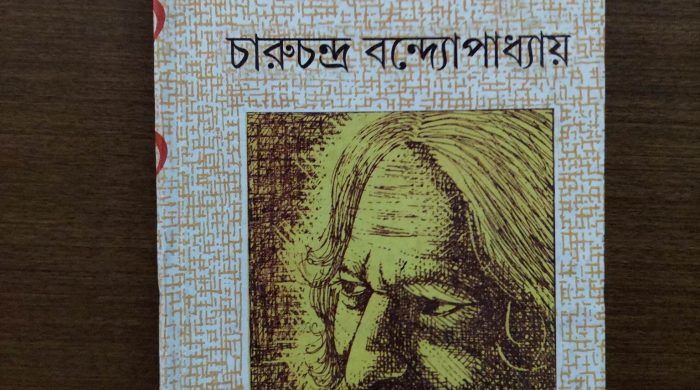কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিভা অবশ্যই ছিল বহুমুখী, কিন্তু তাঁর মূল পরিচয় এটি যে তিনি কবি, যদিও কেউ কেউ বলেছেন যে কবিতা নয় সঙ্গীতের জন্যই তিনি স্থায়ী হবেন। নজরুল নিজেও মনে করতে যে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলে গেছেন যে বাঙালীকে তাঁর গান গাইতে হবে; সে-দাবিতে কোনো অত্যুক্তি ছিল না। এবং রবীন্দ্রনাথও যে মূলত কবি এ বিষয়ে যেমন সন্দেহ নেই, তেমনি এটাও নিঃসন্দেহ যে নজরুল ও মূলত কবিই। আসলে এঁদের দু’জনের ক্ষেত্রেই কবি-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গীত রচয়িতা-পরিচয়ের কোনো বিরোধ নেই। বাংলা গানে কবিতা থাকে, এবং অন্যসব ভাষার কবিতার মতোই বাংলা কবিতাতেও গান থাকে। নজরুলের গানেও কবিতা আছে, এবং তাঁর গানগুলো উচ্চমানের কবিতা বটে। তিনি যে কবি সে-পরিচয় তাঁর কবিতা পড়লে তো অবশ্যই, গান শুনলে এবং গদ্যরচনা পাঠ করলেও বোঝা যায়। প্রশ্ন দাঁড়ায় কোন ধরনের এবং কোন মানের কবি।
নজরুল যে অত্যন্ত বড় মাপের কবি সেটা যাঁরা তাঁকে পছন্দ করেন নি তাঁরাও মানতে বাধ্য হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের মহত্তম কবি যিনি সেই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁকে তাঁর আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে চিনতে পেরেছিলেন সেটা নিশ্চিন্তে জানা গেছে যখন তিনি কারাবন্দী নজরুলকে ‘শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু’ বলে সম্বোধন করে ‘বসন্ত’ গীতিনাটকটি তাঁকে উৎসর্গ করলেন। কেবল তাই নয়, নজরুল অনশন ধর্মঘট করলে তাঁকে ‘তোমার কাছে আমাদের সাহিত্যের দাবী আছে’ বলে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। সাহিত্যের প্রয়োজনের কথাই বলেছিলেন, অন্যকিছুর নয়। স্মরণীয় যে ওই দু’টি ঘটনার সময় নজরুলের বয়স মাত্র চব্বিশ। তাঁর অনেক রচনাই তখনো প্রকাশের অপেক্ষায়। অন্যদিকে সাধারণ পাঠকের তো কথাই নেই, তাঁরা তো তাঁকে পাওয়া মাত্রই লুফে নিয়েছেন। সে-জনপ্রিয়তা কখনোই নিম্নগামী হয় নি। এবং এখনো অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সাহিত্যে জনপ্রিয়তা উৎকর্ষের প্রতিপক্ষ, এই মতকে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেবার কোনো কারণ নেই, বিশেষ করে সেই সাহিত্য যদি সমসাময়িকতাকে অতিক্রম করে যেতে পারে।
‘বর্তমানের কবি আমি ভাই ভবিষ্যতের নহি নবী’, এমন ঘোষণা নজরুল নিজেই দিয়েছেন; বলেছেন ‘পরোয়া করি না, বাঁচি না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে।’ যুগের কবি তিনি অবশ্যই ছিলেন, হুজুগকে তিনি লেখায় ধারণ করেছেন এও সত্য, তাঁকে যুগপ্রবর্তক কবিও বলা হয়েছে, তবে সত্য এটাই যে তিনি বেঁচে আছেন, এবং থাকবেন। কারণ তাঁর কবিতায় নান্দনিক সৌন্দর্য যেমন আছে, তেমনি রয়েছে দার্শনিক গভীরতা। কোলাহলকে তিনি শিল্পের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিলেন, এবং তাঁর এমন স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টি ছিল যার সাহায্যে সমসাময়িককে গভীর এবং ভবিষ্যতকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পেয়েছেন। বাঁশের বাঁশি ও রণতূর্যকে নির্ভুল দক্ষতায় বাঁজাতে তাঁর কোনো অসুবিধা ঘটে নি।
কবি কে? এই প্রশ্নের জবাবে মাইকেল মধুসূধন যে বলেছেন, শব্দের সঙ্গে শব্দের বিবাহসংঘটনের ঘটক মাত্রেই কবি নন, কবি হবার জন্য কল্পনাশক্তি অত্যাবশ্যক, সে-কথা খুবই সত্য। নজরুলের লেখায় কল্পনাশক্তির অসামান্যতার প্রমাণ রয়েছে। সামান্যকে তিনি অসামান্য করে তুলেছেন, সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা তো বটেই, এমনকি চা-পান, বন্ধুর দাঁড়ি কর্তন, কচুরিপানার উপদ্রব, খুকুর সঙ্গে কাঁঠবিড়ালির ঝগড়া এসব তাঁর হাতে পড়ে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। সাধারণ পাঠকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষও তাঁকে অনতিবিলম্বে চিনে ফেলেছে, একের পর এক তাঁর সাতটি বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার প্রকাশনাও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ তাতেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা কবিকেও কারারুদ্ধ করেছে। একবার তিনি জেল খেটেছেন, আরেকবারও খাটতেন যদি কংগ্রেসের সঙ্গে বড়লাটের চুক্তি না হতো। ‘আমার কৈফিয়ত’-এ নজরুল তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় লিখেছেন,

বন্ধু! তোমার দিলে না ক’ দাম
রাজসরকার রেখেছে নাম
যাহা কিছু লিখি অমূল্য বলে অ-মূল্যে নেন। আর কিছু
শুনেছ কি, হুঁ হুঁ, ফিরিছে রাজার প্রহরী সদাই পিছু পিছু।
নজরুলের রচনার ওপর ওই নজরদারি ও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ কেবল বক্তব্যের কারণেই ঘটে নি, ঘটেছে আবেদনের কারণেও। তাঁর লেখা মাত্রই পাঠককে আনন্দিত, বিচলিত ও উদ্বেলিত করেছে, বক্তব্যের সঙ্গে নান্দনিকতার সম্মিলনের কারণে। রাষ্ট্রের শাসনকে যিনি নির্ভয়ে অবজ্ঞা করেছেন শিল্পের শাসনের কাছে তিনিই অত্যন্ত নত থেকেছেন। লিখেছেন, ‘যাহা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পায় না, তাহা স্থায়ী সাহিত্য নহে। খুব জোর দু’দিনের আদর লাভের পর তার মৃত্যু হয়।’ (‘বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান’) স্নেহভাজন তরুণ কবি আজিজুল হাকিমের রচনা পাঠে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ছন্দ ও ভাষা, এই দুই ঘোড়া কবির বশে এসেছে, এখন ধৈর্য ধরে চেষ্টা করতে হবে ‘ভাবের নীহারিকা লোকে’র সন্ধান পাবার। বে-নজীর আহমদের ‘বন্দীর বাঁশী’ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য : ‘আবেগ যেদিন সংযত হইবে, ছন্দের দুই কূলকে স্বীকার করিয়া এই কবির কাব্যস্রোত সেদিন অপূর্ব সঙ্গীতে বাজিয়া উঠিবে।’
মানতেই হবে যে, বাংলা ভাষার প্রধান কবিদের ভেতর রবীন্দ্রনাথের পরেই নজরুল আসেন, যদিও দু’জনের মাঝখানের ব্যবধানটা অত্যন্ত প্রশস্ত। নজরুলের সাহিত্যজীবনে রবীন্দ্রনাথের বিস্তর প্রভাব, তাঁর বন্ধুরা জানিয়েছেন ‘গীতাঞ্জলী’র প্রায় সব কবিতাই নজরুলের মুখস্থ ছিল, সে-কেবল অসামান্য স্মৃতিশক্তির দরুন নয়, আকর্ষণের কারণেও। রবীন্দ্রনাথকে তিনি আত্মস্থ করেছেন, করে তবেই স্বতন্ত্র হয়েছেন। নজরুলের কাছাকাছি কবি জীবনানন্দ দাশ, জন্ম তাঁদের একই বছরে। নজরুলের মতো জীবনানন্দ ও পুরোপুরি মৌলিক। আরেকজন অত্যন্ত উঁচু মানের কবি মধুসূদন দত্ত, যাঁর সঙ্গে নজরুলের সময়ের ব্যবধান অনেকটা। এই চারজন কেউই একে অপরের মত নন, তবে প্রত্যেকেই খাঁটি বাঙালী, ইতিহাস-সচেতন ও আন্তর্জাতিকতার বোধসম্পন্ন।

রবীন্দ্রনাথের মতো জীবনানন্দেরও নজরুলকে শনাক্ত করতে ভুল হয় নি, প্রমাণ আছে তাঁর প্রথম কবিতার বই ‘ঝরাপালক’-এ (১৯২৭)। সেখানে নজরুলের প্রভাব বেশ স্পষ্ট। জীবনানন্দ অবশ্য এর পরেই তাঁর নিজের পথ ধরে এগিয়েছেন, যেটা ছিল অনিবার্য। নজরুল এবং জীবনানন্দ উভয়েই রোমান্টিক, এবং দু’জনেই একটি অন্তর্গত বোধের দ্বারা পরিচালিত। এই বোধের কারণেই তাঁরা উভয়েই ছিলেন খাপ-না-খাওয়া মানুষ। তবে জীবনানন্দের ক্ষেত্রে বোধটি অন্তর্মুখী বিপন্ন বিস্ময়ের, নজরুলের ক্ষেত্রে সেটা বিদ্রোহের তো অবশ্যই, তারও অধিক; সেটি সমাজ বিপ্লবের। এ ঘটনা মোটেই তাৎপর্যহীন নয় যে, ‘শনিবারের চিঠি’র রক্ষণশীলেরা প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই নজরুল এবং জীবনানন্দকে আক্রমণ করতেন; কারণ তাঁরা দু’জনেই ছিলেন আধুনিক। জীবনানন্দ সম্পর্কে নজরুলের কোনো উক্তি আমরা পাই না, যদিও নজরুলের লেখা সম্পর্কে পরবর্তীকালের জীবনানন্দের মূল্যায়নের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। তবে নজরুল তাঁর কর্মজীবনের শেষ দিকে ‘মক্তবপাঠ’ নামের একটি পাঠ্যবইতে জীবনানন্দের মাতা কুসুমকুমারী দাশের সুপরিচিত কবিতা, ‘আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে’, সংকলিত করেছেন। কবির নামোল্লেখ অবশ্য করেন নি, কুসুমকুমারী যে জীবনানন্দের মাতা এ-তথ্য হয়তো তার অজানাই ছিল। তবে কবিতাটির প্রতি নজরুলের আকর্ষণের কারণটি বোঝা যায়। তিনিও ওই ধরনের ছেলেদেরই চাইছিলেন।
মধুসূদনের সঙ্গে নজরুলের পার্থক্য অনেক দিক থেকেই; কিন্তু মিল এইখানে যে সাহিত্যসৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে তাঁরা উভয়েই ছিলেন বিদ্রোহী। পুরাতনকে প্রত্যাখ্যান করে মধুসূদন সাহিত্যের অঙ্গনে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসেন; জীবনাচরণে তিনি ছিলেন পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক, এবং সেই ছোট কিন্তু আশ্চর্য রচনা, ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’তে তিনি নিপীড়িত হিন্দু মুসলমান প্রজা কীভাবে মিলিত হয়ে জমিদার ভক্তপ্রসাদকে লাঞ্ছিত করেছে তেমন ছবি উপহার দিয়েছেন; যে-কাজ তাঁর সময়ে অন্য কেউ করেন নি। এখানে নজরুল ও মধুসূদনের অবস্থান নিকটবর্তী; কিন্তু ভাষা ব্যবহারের বেলায় তাঁদের দূরত্বটা অত্যন্ত পরিষ্কার। ‘বুড় শালিক’-এ মধুসূদন যে-ভাষা ব্যবহার করেছেন সেটি এসেছে প্রহসনের প্রয়োজনে; নইলে ওই ধরনের লোকজ ভাষার ব্যবহারে তাঁর মোটেই আস্থা ছিল না। আলাপী ভাষা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, সংস্কৃত ভাষা থেকে যত দিন না প্রচুর শব্দ আমদানি করা যাচ্ছে ততদিন আলাপী ভাষা মেছুনীদের ভাষা বৈ অন্য কিছু নয়। তাঁর আস্থা ছিল যে-ভাষা তিনি নিজে তৈরি করবেন তার ওপর, ভরসা ছিল সেটি চিরস্থায়ী হবে। তেমনটা ঘটে নি। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কারণে। মেছুনীদের ভাষা ব্যবহারে মধুসূদনের আপত্তির পেছনে সম্প্রদায়ের বিবেচনা না-থাকলেও শ্রেণীর বিবেচনা নিশ্চয়ই রয়েছে। তাঁর আগেই ভারতচন্দ্র কাব্যে আরবি-ফার্সি শব্দের ‘যবনী’ মিশাল ঘটিয়ে গেছেন, মনে করেছেন সেটি না-ঘটালে কবিতা না হবে প্রসাদগুণসম্পন্ন না হবে রসাল। ভারতচন্দ্র এবং প্যারীচাঁদ মিত্র কারো ভাষা ব্যবহারেই সাম্প্রদায়িকতা বলতে যা বুঝি তার কোনো কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। সাম্প্রদায়িকতা রাজনৈতিক ব্যাপার, সেটা পরে এসেছে। নজরুলের সময়ে কিন্তু ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার হস্তক্ষেপটা বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।
নজরুল যখন তাঁর ভাষায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করছিলেন তখন তিনি সাহিত্যিক, সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণী, এই তিন আপত্তির বিরুদ্ধেই এক সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ওই ধরনের শব্দ ব্যবহারে তাঁর রচনা কেবল অভিনব নয় সুন্দরও হয়েছে; এবং সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্য প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র তৈরিতেও সহায়তা করেছে। কেবল শব্দ ব্যবহারের বেলাতেই নয়, সংস্কৃতির অন্য একটি ক্ষেত্রেও নজরুল যে কাজটি করেছেন সেটি হলো মুসলিম পুরাকাহিনী ও হিন্দু পুরাণকে এক সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া, একধারায় প্রবহমান করা। একাধারে অসম্ভব ও জরুরি এ রকমের একটি কর্তব্যপালন তাঁর আগে অন্য কেউ করেন নি, পরেও করতে পারেন নি। এখানে তিনি সাম্প্রদায়িক ছুৎমার্গের ব্যবধানটা ভেঙে দিয়েছেন।
অর্থনৈতিকভাবে মুসলিম সমাজ যে পশ্চাৎপদ ছিল তাঁর একটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তো খ্যাতিবান সাহিত্যসেবীদের সঙ্গে নজরুলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পার্থক্যে দৃশ্যমান। বাংলা সাহিত্যে প্রধান লেখকদের কেউই তাঁর মতো সহায়সম্বলহীন দুর্দশা থেকে উঠে আসেন নি। এবং সম্প্রদায়গতভাবে তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। নজরুলই ব্যতিক্রম- যেমন বিত্তগত পরিচয়ে, তেমনি সম্প্রদায়গত পরিচয়ে। তথাকথিত মুসলমান উপাদানকে সাহিত্যের অঙ্গাঙ্গী অংশ করে দেওয়ার মধ্যে শ্রেণী-বিভাজনের বিরুদ্ধেও একটি বিদ্রোহ ছিল বৈকি।
একই সঙ্গে সাহিত্যিক, সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণী পার্থক্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর এই ব্যাপারটা বেশ সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে লেখা প্রবন্ধ ‘বড়র পীরিতি বালির বাঁধ’-এ। যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার কোনো অবধি ছিল না, যাঁকে তিনি কবিগুরু, বিশ্বকবি ও কবিসম্রাট বলতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং ‘সঞ্চিতা’ কাব্যসঙ্কলনটি যাঁকে তিনি উৎসর্গ করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে এখানে তিনি সরাসরি অবস্থান নিয়েছেন। রচনাটি যেন আরেকটি জবানবন্দী, যেটি তিনি উপস্থিত করেছেন রাষ্ট্রীয় নয়, সাহিত্যিক, সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত বিভাজনকে সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত সামাজিক আদালতে।
উপলক্ষটা ছিল কবিতায় ‘খুন’ শব্দ ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের আপত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের। বাঙালী সমাজে ‘জল ও পানি’র অত্যন্ত হাস্যকর বিরোধ সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেবার ক্ষেত্রে কাজে লেগেছে; রক্ত ও খুনের ব্যবধান নিয়েও তেমনি একটা বিরোধ বাঁধলে উভয় পক্ষের সাম্প্রদায়িকেরাই খুশি হবেন, কিন্তু সেটি সূচনাতেই বিনষ্ট হয়ে গেছে নজরুলের এই অত্যন্ত যৌক্তিক ও সবল জবানবন্দীর কারণে। এ যেন কবির নয়, দক্ষ আইনজীবীর বক্তব্য। নজরুলের বলবার কথাগুলোর মধ্যে রয়েছে :
১. ‘কবির চরণে ভক্তের নিবেদন, তিনি নিজেও তো টুপি পায়-জামা পরেন, অথচ, আমরা পরলেই তাঁর এত আক্রোশের কারণ হয়ে উঠি কেন, বুঝতে পারি নে। […] সম্ভ্রান্ত হিন্দুবংশের অনেকেই পায়-জামা শেরওয়ানী টুপি ব্যবহার করেন, এমন কি লুঙ্গিও বাদ যায় না। তাতে তাদের কেউ বিদ্রূপ করে নি, তাদের ড্রেসের নাম হয়ে যায় oriental. ওইগুলো মুসলমানেরা পরলে তারা হয়ে যায় মিয়া-সাহেব’।
২. ‘আদালতকে না হয় বিচারালয় বলবো, কিন্তু, নাজির-পেস্কার-উকিল-মোক্তার-কে কি বলবো?’
নজরুলের সন্দেহ ‘খুন’ নিয়ে যিনি আপত্তি তুলেছেন তিনি যেন চিরচেনা রবীন্দ্রনাথ নন, অন্য কেউ। নজরুলের বক্তব্য এটাও যে, ‘খুন আমি আমার কবিতায় মুসলমানী বা বলশেভিক রং দেওয়ার জন্য নয়। হয়ত কবি ও দুটোর একটারও রং আজকাল পছন্দ করেন না।’
নজরুল জানাচ্ছেন যে তিনি বর্জনবাদী নন, এবং বিশ্ব কাব্যলক্ষীর একটা মুসলমানী ঢংও আছে, এ সাজে কাব্যলক্ষীর শ্রীহানি হয়েছে বলেও তাঁর জানা নেই। তিনি বলছেন যে, তাঁর লেখাতে আরবি-ফার্সি শব্দ জোর করে চাপানো হয় নি। স্বাভাবিকভাবে এবং সাহিত্যিক প্রয়োজনেই তারা এসেছে : “যেখানে রক্তধারা লিখবার সেখানে ‘খুনধারা’ লিখি নাই। তাই বলে ‘রক্তখারাবি’ও লিখি না, হয় ‘রক্তারক্তি’ না হয় ‘খুনখারাবি’ লিখেছি।”
তবে কেবল সাহিত্যিক নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবেচনাও রয়েছে। এটা এই রকমের যে বাংলা কবিতার অর্ধেক পাঠক মুসলমান এবং তারা কোকিলের গানের বিরতিতে বুলবুলের সুর শুনলে খুশি হন। “এতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা সাহিত্যসভায় ভিড় না করে হিন্দু-সভারই মেম্বার হন।” ১৯২৬-এর ভয়ঙ্কর দাঙ্গার পরে হিন্দু-সভার উল্লেখটা যেমন সঙ্গত তেমনি দূরদৃষ্টিপ্রসূত। নজরুল কথাটা বলেছেন ১৯২৭ সালে; এর ঠিক বিশ বছর পর ১৯৪৭-এ দশভাগ হয়, এবং সেই রক্তারক্তি খুনোখুনির ঘটনার ব্যাপারে সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ ছিল যার প্ররোচণা সেই রাজনৈতিক দলটির নাম হিন্দু-মহাসভা বটে। সাতচল্লিশে নজরুল জীবন্মৃত, তাই সাম্প্রদায়িক হানাহানির পরিণতির দৃশ্যটা দেখলেও তার তাৎপর্যটা বোঝেন নি, বুঝলে সেটি সহ্য করা তার জন্য যে কঠিন হতো তাতে সন্দেহ কী!
১৯৭২-এর দিকে হিন্দু-মুসলমানের মিলন বিষয়ে ইব্রাহিম খানকে লেখা এক চিঠিতে নজরুলের বক্তব্য :
বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেবদেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায় হিন্দুর তেমনি মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে নিত্যপ্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোচকানোও অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী।
এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রটিতে তিনি মুসলমান নন, হিন্দু নন, এমনকি অসাম্প্রদায়িকও নন, তিনি ধর্মনিরপেক্ষ। নজরুল ধর্মে অবিশ্বাসী নন, কিন্তু ধর্মকে তিনি মনে করেন ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার, সেটিকে তিনি সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতির ক্ষেত্রে নিয়ে আসবেন না, ওই সব ক্ষেত্রে ধর্মকে ধর্মব্যবসায়ীদের ক্রীড়নক ও মানুষের জন্য মিলনের অন্তরায় হতে দেবেন না। ধর্মকে রাখবেন ধর্মের জায়গায়, সমাজ, সংস্কৃতিক ও রাজনীতিকে তাদের জায়গায়; সংমিশ্রণের অনাচার করতে দেবেন না।
তাঁর এই অবস্থানে কোনো রকমের কৃত্রিমতা নেই, এটি সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত এবং পরিপূর্ণরূপে আন্তরিক। কবির ব্যক্তিগত জীবনেও এই ধর্মনিরপেক্ষতা আমরা দেখেছি। তিনি বিয়ে করেছেন হিন্দু পরিবারে, পুত্রদের নাম রেখেছেন অরিন্দম খালেদ, কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ; নজরুলের শ্বাশুড়ী নজরুলের সঙ্গেই থাকতেন, এবং নিজের মতো ধর্মাচরণ করতেন, কোনো অসুবিধা ছিল না।
ছোট্ট একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়, যা থেকে বোঝা যাবে নজরুলের ভেতর অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার স্পৃহা ও ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ কেমন প্রবল ছিল, এবং তদ্বিপরীতে তাঁর সময়ে সাম্প্রদায়িকতা কতটা প্রকট হয়ে উঠেছিল। কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা একটি চিঠিতে নজরুল জানাচ্ছেন যে, একটা মজা হয়ে গেছে; পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বের হয়েছে এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক মৃত্যুশয্যায় রয়েছেন, কোনো সুস্থ যুবকের রক্ত পেলে তিনি বাঁচতে পারেন। যুবক নজরুল ঠিক করেছেন তিনি রক্ত দেবেন। বন্ধুকে লিখছেন, ‘সময় নেই, অক্ষুণি বের হব ডাক্তারের কাছে।’ কয়েক দিন পরে ঢাকার বন্ধুকে তিনি হতাশ কণ্ঠে জানাচ্ছেন, রক্তদান করিনি। ডাক্তার শালা বলল হার্ট দুর্বল। ‘শালার মাথা’। “মনে হচ্ছিল একটা ঘুষি দিয়ে দেখিয়ে দিই কেমন হার্ট দুর্বল। ভিতরের কথা তা নয়। ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক মুসলমানের রক্ত নিতে রাজি হলেন না। হায়রে মানুষ, হায়রে ধর্ম। কিন্তু কোন হিন্দু যুবক আজও রক্ত দিল না। লোকটা মরবে তবু নেবে না নেড়ের রক্ত।”
খুন নিয়ে সেই সাহিত্যিক মামলার নিষ্পত্তিতে প্রমথ চৌধুরী এগিয়ে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি যে নজরুলকে লক্ষ্য করে নয় এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন,
আরবি-ফার্সি শব্দ যদি ত্যাগ করতে হয়, তাহলে আমাদের সর্বাগ্রে ‘কলম’ ছাড়তে হয়। কারণ ও শব্দটি শুধু আরবি নয় এমন অনির্বচনীয় আরবি যে ও শব্দ হা করে কণ্ঠমূল থেকে উচ্চারণ করতে হয়।
কিন্তু হায়, ওই লেখাতেই, নজরুলের নামের বানান করেছেন তিনি ‘নজরউল’ হিসাবে; বোঝা যায় কথিত আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন বীরবলের পক্ষেও প্রতিবেশী মিয়া সাহেবদের দিকে ভালো করে তাকানো সম্ভব হয় নি। সম্প্রদায় ও শ্রেণী উভয় দূরত্বই ছিল।
বীরবলের মধ্যস্থতার ব্যাপারে নজরুলের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় নি, তবে ‘বড়র পীড়িতি’ বিষয়ে তাঁর নিজের প্রবন্ধে নজরুল একটি বিশেষ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন; সেটি শ্রেণীর। সে-বিষয়ে তিনি কবিগুরুর ‘খোলা কথা’ শুনতে চেয়েছেন। তাঁর ভাষায়, ‘ওঁর আমাদের উদ্দেশ্য করে আজকালকার লেখাগুলোর সুর শুনে মনে হয় আমাদের অভিশপ্ত জীবনের দারিদ্র্য নিয়েও যেন বিদ্রূপ করতে শুরু করেছেন।’
রচনাটির উপসংহারে এসে নজরুল শরৎচন্দ্রকেও ছাড় দেন নি। তিনি শুনেছেন শরৎচন্দ্র নাকি পথের কুকুরদের জন্য একটি মঠ তৈরি করবেন বলেছেন, যেটি কুকুরদের আশ্রয়স্থল হবে। “তিনি (শরৎচন্দ্র) নাকি জানতে পেরেছেন ঐ সময় কুকুর পূর্বজন্মে সাহিত্যিক ছিল, পরে কুকুর হয়েছে।” নজরুলের মন্তব্য মর্মস্পর্শী :
সত্যিই আমরা সাহিত্যিকরা কুকুরের জাত। কুকুরের মত আমরা না খেয়ে এবং কামড়কামড়ি করে মরি। […]
‘আজ তুই একটিমাত্র প্রার্থনাÑ যদি পূর্বজন্ম থাকেই, তবে আর যেন এদেশে কবি হয়ে না জন্মাই। যদি আসি, বরং শরৎচন্দ্রের মঠের কুকুর হয়েই আসি যেন। নিশ্চিন্তে দুমুঠো খেয়ে বাঁচব।
২
একালে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলি, কিন্তু তাকে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছি। কত যুগ আগে নজরুল এটি মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন যে কেবল স্বাধীনতায় কুলাবে না, নতুন সমাজ চাই এবং তার জন্য সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করাটা যথেষ্ট নয়, ধর্মনিরপেক্ষতা আবশ্যক, যেটি প্রথম শর্ত গণতান্ত্রিক সম্মুখযাত্যার। কবিতায় ভাষা ব্যবহারের বেলায় অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর অসাম্প্রদায়িকতা ধর্মনিরপেক্ষতার স্তরে পৌঁছে গেছে। তাঁর লেখা এ ধরনের অনেক পঙক্তিই আমাদের সুপরিচিত। কয়েকটি স্মরণ করা যাক। একেবারেই ইসলামী বিষয় নিয়ে লেখা ‘খেয়াপারের তরণী’তে
অবহেলি জলধির ভৈরব গর্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জন
অন্যদিকে, সম্পূর্ণ আপাত-বিপরীত বিষয়ে লেখা ‘রক্তাম্বরধারিণী মা’তে
জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝ’রে
লালে লাল হোক শ্বেত হরিৎ।
ব্রিটিশের রাষ্ট্র তাঁর শত্রু ছিল, তাঁরা তার বই নিষিদ্ধ করেছে এবং তাঁকে কারারুদ্ধ করেছে; দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী পাকিস্তানি রাষ্ট্রও তাঁর মিত্র ছিল না। পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রীয় কর্তাদের ব্যস্ততা ছিল গোয়েন্দা লাগিয়ে গন্ধ শুঁখে শুঁখে নজরুল কাব্যের অবাঞ্ছিত অংশ খুঁজে বের করা। তাঁরা শ্মশান কেটে গোরস্থান, ভগবান বাদ দিয়ে রহমান বসিয়ে নজরুলকে শুদ্ধ করতে চেয়েছে, কিন্তু নজরুল তাঁর লেখায় কাটাকাটির কোনো অবকাশই রাখেন নি, তিনি অবলীলায় লিখেছেন,
জাগেন সত্য ভগবান যে রে
আমাদেরি এই বক্ষ মাঝে,
আল্লার গলে কে দিবে শিকল, দেখে নেবো মোরা
তাহাই আজি
(‘বন্দনা গান’)
ভগবান আল্লাহ দু’জনেই রয়েছেন, এবং উভয়েই অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছেন, কেবল মিলনের নয়, মুক্তি সংগ্রামের।
অন্যত্র
দিকে দিকে পুন জ্বলিয়া উঠেছে
দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল।
ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ জেগে
তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল।
(‘জুলফিকার’)
নবজাগরণের উৎসবে মশাল এবং মঙ্গল-প্রদীপ এক হয়ে গেছে।
‘ভাঙার গান’-এ আছে
ভগবান পরবে ফাঁসি
সর্বনাশী
শিখায় এ হীন তথ্য কে রে
এবং তারপরেই এসেছে,
মার হাঁক হৈদরী হাঁক
কাঁধে নে দু-ভি চাক
১৯২৬-এর দাঙ্গা নজরুলকে ভীষণভাবে বিচলিত করেছিল। কিন্তু তিনি হতাশ হন নি। উল্টো ‘কান্ডারী হুশিয়ারে’র মতো কবিতা লিখেছেন, যা শুধু নজরুলের পক্ষেই লেখা সম্ভব ছিল। বলেছেন,
হিন্দু না ওরা মুসলিম এই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কান্ডারী, বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার!
এই দাঙ্গা নিয়ে পরিহাস-বিদ্রূপ ও কম করেন নি তিনি। ব্যক্তিগত চিঠিতে বন্ধু শৈলজানন্দকে জানাচ্ছেন, ‘আমি এবার কলকাতা গিয়েছিলুম। আল্লা… আর ভাগবান… এর মারামারির দরুন তোমার কাছে যেতে পারি নি।’
বাঙালী বাঙালীকে খুন করছিল। নজরুল জানেন সে-কালের রাজনীতিতে প্রধান দ্বন্দ্বটা ছিল ভারতবর্ষের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের। সেটা অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল দাঙ্গার কারণে, যে-দাঙ্গার পেছনে প্ররোচণা ছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের। এমন স্পষ্ট উপলব্ধি তাঁর কালের রাজনৈতিক মহলে তো অবশ্যই, বুদ্ধিজীবী মহলেও বিরল ছিল। ‘কান্ডারী হুঁশিয়ার’ কবিতায় আছে, ‘কান্ডারী! তব সম্মুখে ওই পলাশীর প্রান্তর/বাঙালীর খুনে লাল হলো যেথা ক্লাইভের খঞ্জর।’ রাজনৈতিক লড়াইটা ছিল ভারতবর্ষব্যাপী, নজরুল সমগ্র ভারতবর্ষের মুক্তি চেয়েছেন, তাঁর ভারতবর্ষ মানচিত্রের নয়, মানুষের; মানচিত্রের ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদীদের তৈরি, মানুষের ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে নজরুলের অবস্থান বাঙালী হিসাবেই। তাঁর জাতীয়তার ভিত্তি ধর্ম নয়, ভাষা। যে-স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন তিনি দেখেন সেটি সমাজতান্ত্রিক, সেখানে শোষণ থাকবে না। সেই ভারতবর্ষের প্রস্তুতির জন্য তাঁর নিজের লেখায় যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস তাদের ‘সর্বনাশ’ লিখিত হবে। এই শোষকেরা তখন ছিল বিদেশি, কিন্তু আগামীকাল যদি তাদের গদীতে স্বদেশীরা বসে যায় তবে অবস্থার যে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটবে না সে-উপলব্ধি তাঁর দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টিরই অংশ।
যে-সমাজতান্ত্রিক ভারতের কথা তিনি ভাবছেন সেটি প্রতিষ্ঠার দাবি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিরও ছিল, কিন্তু সে-পার্টি তখন সবেমাত্র গঠিত হয়েছে, গঠনের পরে তাত্ত্বিক বিভ্রান্তির কারণে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে তারা পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন করেছিল, এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশের পাততাড়ি গোটানো যখন আসন্ন তখন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কর্মসূচীকে ভুলে গিয়ে লীগ- কংগ্রেসের ঐক্য চেয়েছে। ওদিকে পাকিস্তানকে নজরুল ‘ফাঁকিস্তান’ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। ‘ধূমকেতু’ তার আবির্ভাবের মুহূর্তেই ঘোষণা দিয়েছিল যে, সে লীগ ও কংগ্রেস কোনো রাজনীতিতেই বিশ্বাস করে না, যে অবিশ্বাসের কারণে নজরুল নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।
৩
সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রধান দুর্বলতার আকর ছিল হিন্দু-মুসলিম বিরোধ। নজরুলের মতো পরিষ্কারভাবে সেটা কম লোকেই বুঝেছেন এবং বলেছেন। বিশেষভাবে তিনি বলেছেন ব্রাহ্মণ্যবাদী ছুৎমার্গের বিষয়ে। এ নবযুগে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি একটি কাল্পনিক নয়, সত্য ঘটনার উল্লেখ করেছেন। রেলগাড়ির কামরায় কয়েকজন ব্রাহ্মণ ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করছেন, এমন সময়ে সেখানে কয়েকজন মুসলমানের প্রবেশ; সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রস্ত হয়ে ধর্মপ্রাণ ভদ্রলোকেরা উঠে এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালেন, পাছে স্পর্শ দোষ ঘটে যায়। নজরুলের বক্তব্য, হিন্দু হিন্দু থাকুক, মুসলমান মুসলমান থাকুক, কিন্তু তারা পরস্পরের অস্পৃশ্য হয়ে থাকলে তো সুবিধা হবে শাসন ব্রিটিশের। নবযুগের ওই প্রবন্ধটিতে নজরুল লিখছেন, ‘যে স্থানে মুসলমান গিয়া পা দিবে সে স্থান গোবর দিয়া (!) পবিত্র করিতে হইবে।’ লিখে, ‘গোবর দিয়া’র পরে একটি বিস্ময়বোধক চিহ্ন এমনভাবে বসিয়ে দিয়েছেন যার অপ্রত্যাশিততা ঘটনাকে অত্যন্ত হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু নজরুল যে তাঁর বন্ধু আবুল মনসুর আহমদের ‘আয়না’র ভূমিকাতে লিখেছেন যে এই বইয়ের হাসির পেছনে বেদনার অশ্রু আছে সেটা নজরুলের নিজের সকল ব্যঙ্গ রচনার সম্বন্ধেই সত্য।
সাম্প্রদায়িক ব্যবধান যে প্যাক্টে দূর হবার নয়, সেটা অন্যরা বোঝার আগেই নজরুলের বোঝা হয়ে গিয়েছিল। চিত্তরঞ্জনের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা, কিন্তু তাঁর প্যাক্টের ওপরে নজরুল ভরসা করেন নি। ‘চন্দ্রবিন্দু’ (১৯৩১) বইতে আছে :
আঁট সাঁট করে গাট-ছড়া বাঁধা
হ’ল টিকি আর দাঁড়িতে,
“বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো?” তা
হয় হোক তাড়াতাড়িতে,
একজন যেতে চাহিবে সমুখে,
অন্যে টানিবে পিছনে-
ফসকা সে গাঁট হয়ে যাবে আঁট
সেই ভীষণ টানা টানিতে’
আর যা ঘটবে তা হচ্ছে,
বদনা গাড়ুতে পুন ঠোকাঠুকি
বোল উঠিল হাঁ হন্ত!
উর্দ্ধে থাকিয়া সিঙ্গী-মাতুল
হাসে চিরকুটি দন্ত।
মসজিদ পানে ছুটিলেন মিঞা
মন্দির পানে হিন্দু
আকাশে উঠিল চির জিজ্ঞাসা
করুণ চন্দ্রবিন্দু
এই ঠোকাঠুকি রক্তারক্তিতে যত সুবিধা শিঙ্গী মাতুলের, অর্থাৎ ব্রিটিশের। এমন কথা অন্য কারো পক্ষেই লেখা সম্ভব ছিল না, ঈশ্বর গুপ্ত বা শনিবারের চিঠিওয়ালাদের পক্ষে তো নয়ই।
ঐক্যটা ওপর কাঠামোতে রাজনৈতিকভাবে হতে পারে, কিন্তু ভেতরে যদি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলন না হয় তবে তা টিকবে তো না-ই, বরঞ্চ বিপত্তির কারণ হবে, যেমনটা ঘটেছে। সে-বিপদ নজরুল দেখেছেন, অন্যরা দেখেন নি।
ওই ঐক্য ঘটবার পথে অন্তরায় হচ্ছে উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত, যাদের ভেতর আছে সংস্কার, এবং তার চেয়ে বেশী করে আছে স্বার্থবুদ্ধি, তারা জানে জনগণের ঐক্য ঘটলে তাদের মহাবিপদ ঘটবে, যে বিপদের কথা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অকপটে স্বীকার করেছেন, যেজন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষকের চরম দুর্দশা ঘটছে জেনেও তিনি বলেছেন ব্যবস্থাটাকে ভাঙা চলবে না, কারণ তাতে ‘আধুনিক’ অর্থাৎ বৈষয়িক সুযোগপ্রাপ্ত শ্রেণীর বিপদ ঘটবে।
১৯২৬-এর দাঙ্গার সময়ে লেখা ‘হিন্দু মুসলমান’ প্রবন্ধে নজরুল বলেছেন যে, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের ব্যাপার নিয়ে আলোচনার সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একদা বলেছিলেন, ‘দেখ, যে ল্যাজ বাইরের তাকে কাটা যায়, ভেতরের ল্যাজকে কাটবে কে?’ ওই ল্যাজ নিয়ে দুশ্চিন্তা নজরুলেরও। তিনি বলছেন মারামারিটা হিন্দু-মুসলমানের নয়, এটি হচ্ছে পন্ডিত ও মোল্লার, অর্থাৎ ধর্মব্যবসায়ীদের। আরো লিখেছেন যে এই ব্যবসার প্রকোপে ভ্রষ্ট হয়েছে উচ্চশিক্ষিতরা। রাস্তায় যেতে যেতে তিনি দেখেন একটা বলদ যাচ্ছে, তার ল্যাজটা গেছে খসে। কিন্তু পাশেই দেখেন ‘আমার অতিবড় উদার বিলেতফেরত বন্ধুর মাথায় য্যাবড় ল্যাজ গজিয়েছে।’ নজরুল জানেন, এবং আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে, ‘অন্তরালে যে কাজ করছে সেটি ভিন্ন এক শক্তি, যাদের নেতার নাম শয়তান।’
সে নাম ভাঙিয়ে হিন্দু, মুসলমানকে খেপায়, সে-ই আবার গুর্খা সিপাই হইয়া হিন্দু-মুসলমানকে গুলি করিতেছে। উহার ল্যাজ সমুদ্র পারে গিয়ে ঠেকিয়াছে, উহার মুখ সমুদ্রপারের বাঁদরের মত লাল।
সমুদ্রপারের লালমুখো বাঁদরটা, যার অপর নাম সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ, সে আবার সিংহ সেজে বসে আছে; আসল কারসাজিটা তারই। এ সত্য বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকেরা দেখেও দেখতে চায় না, কারণ জনগণের ঐক্যে তাদের সমূহবিপদ। সিংহ মামার সঙ্গে তাদের যতটা খাতির দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রায় ততটাই দূরত্ব।
ব্রিটিশ, কংগ্রেস ও লীগের সম্মিলিত প্ররোচনায় হিন্দু মুসলমান যখন নিজ নিজ কায়দায় ‘মারো শালা যবনদের’ ‘মারো শালা কাফেরদের’ বলে আল্লাহর এবং মা কালীর প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য চীৎকার করতে থাকে তখন তার ফলটি দাঁড়ায় কী? তারা মাটিতে পড়তে শুরু করে, এবং দেখা যায় যে, তখন তারা
আল্লা মিয়া বা মা কালী ঠাকুরানীর নাম লইতেছে না। হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে-‘বাবা গো, মা গো’। মাতৃপরিত্যক্ত দু’টি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মা’কে ডাকে।
কবি দেখেছেন এবং শুনেছেন। তাঁর দেখবার চোখ ছিল, শুনবার কান ছিল, অন্যরা দেখেও দেখে নি, শুনেও শোনে নি, কেননা তারা ছিল অন্ধ ও বধির। স্বার্থের কারণে।
নিজের ধর্মনিরপেক্ষ এবং বিদ্রোহাতিরিক্ত সমাজবিপ্লবী অবস্থান থেকে যখন নজরুল দেখেন, দুর্দশায় প্রতি বছর বাংলায় দশ লক্ষ মানুষ মারা যায়। দেখে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, ‘রোগ-শীর্ণ অনাহারক্লিষ্ট বিবস্ত্র বুভুক্ষু সর্বহারা ভূখারিদের লাশ’ ‘দিনের পর দিন ধরিয়া মন্দির-মসজিদের পাশ দিয়ে চলিয়া যায়’ তবুও ‘ঐ নিরর্থক’ ভজনালয়গুলো কেন ‘ধ্বসিয়া পড়ে না’?
তাঁর প্রবন্ধের বইগুলো ছোট ছোট, চটি আকারের। দুর্দিনের যাত্রী মাত্র ৫৪ পৃষ্ঠার, ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত প্রকাশক না-পেয়ে যেটি তিনি নিজেই প্রকাশ করেছেন; রুদ্রমঙ্গল ৭৮ পৃষ্ঠার, যুগবাণী ৯২ পৃষ্ঠার। কিন্তু এদের প্রত্যেকটিই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। চন্দ্রবিন্দু মূলত কমিক গানের বই, নিষেধাজ্ঞার প্রকোপ থেকে সেটিও বাদ পড়েনি, কারণ ওই বইতে হিন্দু-মুসলমানের যে ঐক্যের পক্ষে তিনি লিখছিলেন তাতে বিপদ ছিল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র তাঁর কবিতার বই বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা’র ওপর যেমন প্রবন্ধের বইগুলোর ওপরও তেমনি সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সমাজের সঙ্গে নজরুলের দ্বন্দ্ব ছিল, সেটি অবৈরী দ্বন্দ্ব, তার পেছনে আছে ভালোবাসা, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব পরিপূর্ণ বৈরিতার, সে জন্য সমাজের বড় অংশ তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করেছে, কিন্তু রাষ্ট্র তাঁকে কখনোই ক্ষমা করেনি।
কথাটা এইখানে বলে নেওয়া যায়, নজরুল পরিপূর্ণরূপে বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, যে জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষ ও ভাষাভিত্তিক। কিন্তু ওই সীমায় তিনি আবদ্ধ না থেকে এগিয়ে গেছেন; এটা বুঝতে তাঁর কোনো বিলম্ব ঘটেনি যে সামাজিক বিপ্লব ছাড়া শ্রেণীবিভক্ত বাংলায় মানুষের মুক্তি নেই।
সাহিত্যজীবনের শুরু থেকেই তিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কথা ভেবেছেন। ১৯২০ সালে লিখিত বাঁধনহারা উপন্যাসে একটি প্রাণবন্ত চরিত্রের নাম সাহসিকা বোস, যিনি মেয়েদের স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। এই মহিলা অনায়াসে মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, এবং সেই সামাজিক ঐক্যের পূর্বাভাস দেন যার ওপর নজরুল জোর দিয়েছেন। উপন্যাসে রাবেয়া তার ননদকে বলছে, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের জন্য প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন। ‘ভিতরে এত অসামঞ্জস্য ঘৃণা-বিরক্তি চেপে রেখে বাইরের মুখের মিলন কি কখনো স্থায়ী হয়?’
স্থায়ী হয় না। প্যাক্ট হতে পারে, ঐক্য হয় না। ঐক্যের প্রশস্ত পথ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন। দাঙ্গার সময়ে লেখা ‘হিন্দুমুসলিম যুদ্ধ’ কবিতায় নজরুল আশা রাখছেন,
যে-লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ পড়ে মন্দির চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া।
এই সময়েই অন্য একটি কবিতায় তিনি জানাচ্ছেন সাম্রাজ্যবাদের বিপদ দেখা দিয়েছে, ‘সিংহ’ শঙ্কায় লীন হয়েছে, এবং ‘ঘরে ঘরে তার লেগেছে কাজিয়া’। এই পরিস্থিতিতে ‘বদনা-গাড়–তে কেন ঠোকাঠুকি, কাছা-কোঁচা টেনে শক্তিহীন?’ এ টানছে ওর কাছা, ও টান দিচ্ছে এর কোঁচায়, এমনটাই ঘটছিল। অথচ যা করা দরকার ছিল তা হলো,
রথ টেনে আন্ আন্রে তাজিয়া
পূজা দেরে তোরা দে কোরবান
রথ ও তাজিয়া, পূজা ও কোরবানের এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের একটি ছবি আছে কুহেলিকা উপন্যাসে। ১৯৩১ সালে লিখিত এই রচনাটিতে নজরুল পেছনের দিকে তাকাচ্ছেন না, তাঁর দৃষ্টি সম্মুখবর্তী। নজরুল তাঁর প্রথম কবিতার বই অগ্নিবীণা উৎসর্গ করেছেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে, যাঁকে তিনি অভিহিত করেছেন ‘ভাঙা-বাংলার রাঙা-যুগের আদি পুরোহিত’ বলে। কিন্তু ওই যুদ্ধের সেনাধ্যক্ষরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। বিপ্লব তো ভুলেছেনই, বিদ্রোহও ভুলে তাঁরা চলে গেছেন আশ্রমে। স্মরণীয় যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের এই সংগ্রামীরা, সরকার যাঁদের বলতো টেররিস্ট, তাঁরা সাম্প্রদায়িক বলয়ের বাইরে যেতে পারেন নি। মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর আত্মজীবনীতে জানাচ্ছেন যে, কৈশোরে তিনি এঁদের দলে যোগ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেখেছেন যে, সবগুলো দলই মুসলিমবিদ্বেষী। নজরুল কিন্তু হতাশ হন নি। কুহেলিকা উপন্যাসের জন্য তিনি নতুন নায়ক খুঁজে পেয়েছেন প্রমত্তের মধ্যে। প্রমত্ত সম্ভ্রান্তবংশীয় এবং উচ্চশিক্ষিত, হিন্দু-মুসলিম বিভাজনে সে মোটেই বিশ্বাস করে না। বন্ধনীর ভেতর উল্লেখ করা যায় যে, প্রমত্তের নামটি লক্ষ্য করবার মতো, নেপালের গোপন কমিউনিস্ট পার্টির নেতার ছদ্মনাম ছিল প্রচ-; সাদৃশ্যটা কাকতালীয়ই, তবে একেবারে যে তাৎপর্যহীন তা বোধ হয় নয়। নজরুল প্রমত্তদেরকে সন্ত্রাসবাদী বলে মনে করেন না, তাঁর কাছে এঁরা হচ্ছেন বিপ্লববাদী। প্রমত্ত তার বিপ্লবী দলে অনায়াসে টেনে নিয়েছে মুসলমান জমিদার বংশের সন্তান জাহাঙ্গীরকে, যে কোনো ধর্মমন্ত্রে নয়, দীক্ষিত হয়েছে ‘মাতৃমন্ত্রে’। প্রমত্ত মানুষের মুক্তির জন্য লড়ছে। ধর্মকে সে গুরুত্ব দেয় না। সে জানে ফরাসি বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল অন্ধ বিশ্বাসের পরিসমাপ্তিতেই। সহযোদ্ধাদেরকে সে বলে, ইংরেজের ভারতশাসনের বড় যন্ত্র কি জানিস? ধর্মের ভিত্তিতে ভেক দাঁড় করানো। ১৯৩৭-এ আন্দামানের নির্বাসন থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন; ছয় ওই ঘটনার বছর আগেই নজরুল যেন সেই সম্ভাবনাটাই দেখতে পেয়েছেন, তাঁর উপন্যাসে।
প্রমত্ত সাম্যবাদী বিপ্লবী হবে, এটি ছিল সম্ভাবনা। কিন্তু মৃত্যুক্ষুধা’র আনসার যে ইতিমধ্যেই ওই পথের পথিক হয়ে গেছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ রাখার অবকাশ সে দেয় নি, দেয় নি রাষ্ট্রপক্ষও। শুরুতে সে ছিল ঘোরতর গান্ধীবাদী, চরকার বিরুদ্ধে বললে ক্ষেপে যেতো। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে যে, সূতোয় কাপড় হয়, দেশ স্বাধীন হয় না; এবং অন্যসব দেশ যেখানে মাথা কেটে স্বাধীন হতে পারছে না সেখানে তার দেশ সূতো কেটে স্বাধীন হবে এটা আকাশকুসুম কল্পনা। সে বুঝেছে যে দেশের মুক্তি কংগ্রেস বা লীগ আনবে না, আনবে জনগণ, তাই কৃষ্ণনগরে এসে আনসার কাজে নেমে গেছে শ্রমিক সংঘ গড়ে তুলতে। মফস্বল শহরে কারখানার শ্রমিক আর পাবে কোথায়, গায়োয়ান, কোচোয়ান, রাজমিস্ত্রী, কুলি, মজুর মেথর, এদেরকে অধিকার সচেতন করছে। অনতিবিলম্বে খবর রটে গেছে শহরে এক বলশোভিকের বিপ্লবী নেতা এসেছে যে ছেলেদের মধ্যে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করছে ও বিপ্লবী তৎপরতা চালাচ্ছে। ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, এমন কি কংগ্রেসওয়ালারা পর্যন্ত তার দিকে বাঁকা চোখে তাকানো শুরু করেছে। ফলে যা হবার তাই হলো, আনসার গ্রেফতার হয়ে গেল। বিভিন্ন বাড়িতে খানাতল্লাশি চললো, বহু ছাত্র ও তরুণকে হাজতে পোড়া হলো।
পুলিশ কিন্তু গ্রেফতার করতে পারেনি মেহনতি মানুষদেরকে। আনসারকে পুলিশ আটক করেছে শুনে দলে দলে তারা ছুটে এসেছে তাকে মুক্ত করার জন্য। পুলিশের মার-গুতো-চাবুক-লাথিতে তাদের ভ্রক্ষেপ নেই। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবার জন্য ফাঁকা গুলি পর্যন্ত করা হয়েছে। কিন্তু জনতা পিছু হটতে নারাজ। ঔপন্যাসিক লিখছেন,
এরি মধ্যে এক বৃদ্ধ মেথর চিৎকার করে বলে উঠল, ‘বাবাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ওর চেয়ে মার আর কি আছে? আমার বুকে বরং গুলি মার, আমাদের বাবাকে ছেড়ে দাও।’
মুচি মেথরকে ভাই বলে ডাকার রাজনীতি বিষয়ে আমরা অবহিত, মহাত্মা গান্ধী তাদেরকে হরিজন বলেছেন, কিন্তু ওই মানুষদেরই একজন এক মুসলমান যুবককে বাবা বলছে, এবং তার মুক্তির জন্য পুলিশের বন্দুকের মুখে নিজের বুক পেতে দিচ্ছে, এ ঘটনা নতুন রাজনীতির সূচক বটে।
শুধু ওই বৃদ্ধ নয়, সবাই বিক্ষুব্ধ। তারা কাঁদছে। কাতর কণ্ঠে আকাশ-ফাটা জয়ধ্বনি দিচ্ছে। সেই ধ্বনি যেন ‘বিক্ষুব্ধ গণদেবতার মানবাত্মার হুঙ্কার।’ আনসারের চোখ ভিজে ওঠে জলে। সে তার শৃঙ্খলবদ্ধ হাত ‘ললাটে ঠেকিয়ে জনসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে নমস্কার’ করে, বলে ‘তোমরা তোমাদের অধিকার আদায় কর…সেই হবে আমারও উদ্ধার। তোমাদের মুক্তির সঙ্গে আমিও মুক্ত হবো।’
নেতার নয়, মুক্তি আসবে জনতার। আনসার যাচ্ছে জেলেÑ দলের বা তার নিজের জন্য নয়, মেহনতি মানুষের জন্য। যাবার সময় সে বলে যায়, ‘তোমরা তোমাদের অধিকারের দাবী কিছুতেই ছেড়ো না।’ জনতা মুহুর্মূহু জয়ধ্বনি দেয়।
যে-বছর মৃত্যুক্ষুধা পত্রিকায় প্রকাশ শুরু হয় সে-বছরই, ১৯২৬ সালেই শরৎচন্দ্রের পথের দাবী প্রকাশিত হয়েছে। সব্যসাচীও বিপ্লবী, বন্দী অবস্থায় বিপ্লবী আনসারকে পাঠানো হয় বার্মাতে, সব্যসাচীর বিপ্লবী কর্মক্ষেত্রও বার্মা পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু আনসারের সঙ্গে সব্যসাচীর সমুদ্রসম ব্যবধান। সব্যসাচী কবি শশীকে বলেছে যে তার বিপ্লব ভদ্রলোকের, কৃষকের নয়। শশীর সঙ্গে নজরুলের মিল আছে, অনেকে সেটা লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু সব্যসাচীর জগতে তো নজরুলের ঠাঁই নেই। একে সে বলশভিকপন্থী, তার ওপর মুসলমান। সব্যসাচী ব্রিটিশকে তাড়াবে, কিন্তু সমাজে কোনো বিপ্লব ঘটাবে না; তার লক্ষ্য স্বাধীনতা, আপত্তি সাম্যে; আনসার স্বাধীনতা ও সাম্য দুটোই চায়, সে জানে যে সাম্য না এলে স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়াবে শুধু ক্ষমতার হস্তান্তর মাত্র।
মনে হতে পারে যে-আনসারের আবির্ভাব এক ধরনের অকালবোধন। কারণ বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে ওই রকমের চরিত্রের সন্ধান পাওয়া সে সময়ে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তা-ই বা বলি কী করে, যখন নজরুল নিজে ছিলেন, ছিলেন কমরেড মুজফ্ফর আহমদ। এই দু’জনের সমন্বয়েই যেন আনসার তৈরি। নজরুলের ছিল অসাধারণ আকর্ষণ ক্ষমতা ও প্রাণচাঞ্চল্য, মুজফ্ফরের ছিল স্বচ্ছ দৃষ্টি ও অঙ্গীকার, তারা দু’জন একত্র হয়েছিলেন, যেমন কর্মক্ষেত্রে তেমনি আনসারের সৃষ্টিতে। কারাবন্দী অবস্থায় আনসারের যক্ষা হয়েছে, একই অবস্থায় একই রোগে মুজফ্ফরও আক্রান্ত হয়েছিলেন। মুজফ্ফর সম্বন্ধে একটি চিঠি’তে নজরুল লিখেছেন, ‘ও যেন পোকায় কাটা ফুল, পোকায় কাটছে তবু সুগন্ধ দিচ্ছে। আজ তাকে যক্ষা খেয়ে ফেলছে, আর ক’টা দিন বাঁচবে জানি না।’ তাঁর দৃষ্টিতে এই বন্ধুটি ছিলেন সর্বত্যাগী, আত্মভোলা ও মৌন কর্মী, ওঁর ছিল ধ্যানীর দূরদৃষ্টি, উজ্জ্বল প্রতিভা।
নজরুল ওই চিঠিটি লিখেছিলেন ১৯২৬-এ, আত্মশক্তি পত্রিকার সম্পাদককে। আত্মশক্তি চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ দলের মুখপত্র। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এটি যে, নজরুল ছিলেন চিত্তরঞ্জনের অত্যন্ত গভীর অনুরাগী, কিন্তু সেই পত্রিকায় গণবাণী’র সমালোচনা করা হয়েছিল, এই মর্মে যে, গণবাণী’র বক্তব্য সাধারণ মানুষ বুঝবে না। নজরুল বলেছেন কার্ল মার্কসের মতবাদও সাধারণ শ্রমিক বুঝতে পাড়বে না, কিন্তু সে-বাণী তারা বুঝবে যারা ‘জগৎটাকে উল্টে দিয়ে নতুন করে গড়তে চাচ্ছেন না গড়ছেন’। ‘ইঞ্জিন চালাবে ড্রাইভার কিন্তু তাতে চড়বে জনসাধারণ।’ সন্দেহ নেই নজরুল চিত্তরঞ্জনের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকেও অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছিলেন।
৪
নজরুল ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। ১৯৪২-এ, কর্মজীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে, নবযুগে তিনি লিখেছিলেন, ‘বাংলা বাঙালীর হোক। বাঙালীর জয় হোক। বাঙালীর জয় হোক।’ কিন্তু তাঁর সেই বাংলা এক থাকে নি, পাঁচ বছর যেতে না যেতেই দু’টুকরো হয়ে গেছে। দেশভাগের ঠিক পরে অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছিলেন, ‘ভুল হয়ে গেছে ভুল/সবকিছুই ভাগ হয়ে গেছে/ভাগ হয় নিকো নজরুল/ওই ভুলটুকু বেঁচে থাক/বাঙালী বলতে একজনই আছে/ দুর্গতি তার ঘুচে যাক।’ এই উপলব্ধি আমাদের সকলেরই।
বাঙালী বলতে নজরুল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর বাইরে সকল বাঙালীকে বুঝেছেন, যেটা তাঁর আগের কালে তো বটেই, তাঁর নিজের কালেও সকল বাঙালী বোঝেন নি। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখ অনিবার্য হয়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র মনেপ্রাণে বাঙালী ছিলেন, নজরুলের সঙ্গে এখানে তাঁর পুরোপুরি মিল। কিন্তু পার্থক্যও রয়েছে, সেটি যে কেবল সময়ের তা নয়, মূলত দৃষ্টিভঙ্গির। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হয়েছিল আমরা পরাধীন জাতি, অনেককাল পরাধীন থাকবো। নজরুল তাঁর পরে এসেছেন, এবং কারাবন্দী হবার প্রাক্কালে রাজবন্দীর জবানবন্দীতে পরিষ্কারভাবে, অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন অন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ শাসন কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র নজরুলের মনোজগতে উপস্থিত ছিলেন; ‘পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ’ এবং ‘তোমার পণ কি’ নামের ছোট লেখা দু’টিতে এ-উপস্থিতি খুবই স্পষ্ট। নজরুল জানিয়েছেন, না, তিনি পথ হারাননি। আনন্দমঠে’র উপক্রমণিকাতে ‘আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?’ এ প্রশ্নের উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন এসেছিল ‘তোমার পণ কি?’ জিজ্ঞাসু মনুষ্যকণ্ঠ জবাব দিয়েছে, ‘পণ জীবনসর্বস্ব’। তখন বাণী শোনা গেছে, ‘প্রাণ তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।’ বলা হয়েছে, প্রাণের চেয়ে ভক্তি বড়। নজরুল তা কখনোই মনে করেন নি। তাঁর কাছে জীবনের চেয়ে বড় কিছু নেই। ভক্তির বন্ধন নজরুল ছিন্ন করেছেন; রাজভক্তি তো ছিলই না, মুক্তির প্রয়োজনে সমাজভক্তি, গুরুভক্তি, সব ভক্তির বন্ধনই তিনি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন।
বঙ্কিমের সঙ্গে নজরুলের পার্থক্যের মূল জায়গাটা হলো এখানে যে, স্বাধীনতার ব্যাপারে সুতীব্র আকঙ্খা থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমের ভয় ছিল সাম্যে এবং নজরুল সাম্যভিন্ন স্বাধীনতার কথা ভাবতেই পারতেন না। ‘সাম্য’ নিয়ে বঙ্কিম ছোট কিন্তু অসাধারণ একটি বই লিখেছিলেন, কিন্তু পরে সেটি প্রত্যাহার করে নেন; বলেছিলেন যে তাঁর আগের ধারণা ছিল ভ্রান্ত। সাম্যে’র ভয়ের কারণেই বঙ্কিম ঘোষণা করেছিলেন, ‘আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি’; অন্যদিকে নজরুল সদর্পে বলেছেন, ‘গাহি সাম্যের গান’; বইয়ের নাম দিয়েছেন ‘সাম্যবাদী’, ‘সর্বাহারা’, পুত্রদের একজনের ডাক নাম রেখেছেন সান ইয়াৎ সেন, অপরজনের লেনিন। তাঁর ‘ধূমকেতু’ বলেছে স্বরাজ টরাজ বুঝি না, ওর অর্থ একেকজন একেক রকম করেন, চাই পূর্ব স্বাধীনতা। এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর নৈকট্য আছে; সুভাষও বিদ্রোহী ছিলেন, এবং নজরুলের নাগরিক সম্বর্ধনায় সুভাষ যে বলেছিলেন নজরুলের গান তাঁদেরকে গাইতে হবে যেমন কারাগারে তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে, সে-ধারণাও সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সুভাষচন্দ্রও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু সে-সমাজতন্ত্রকে তিনি বলেছেন ভারতীয় এবং তা ছিল অনেকটা স্বপ্নকল্পনার; কিন্তু নজরুলের সমাজতন্ত্র জাতীয় নয়, তা মার্কস ও লেনিনের। হতদরিদ্র এবং সব ধরনের সুযোগবঞ্চিত এক তরুণ কবি কী করে অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত, নানাভাবে সমৃদ্ধ এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অতিপ্রত্যক্ষরূপে অভিজ্ঞ সুভাষ বসুকে মতাদর্শিক ভাবে অতিক্রম করে গেলেন সেটি একটি বিস্ময়ের ব্যাপার বৈকি।
নজরুল সমাজ বিপ্লবের পক্ষে নিজের অবস্থান সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ধূমকেতু ঘোষণা করেছে যুগে যুগে এসে সে পুনরায় এসেছে, ‘মহাবিপ্লব হেতু’। ‘সাবধান ঘণ্টা’ বাজিয়ে শনিবারের চিঠিওয়ালাদেরকে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন,
রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনামের নেশা
রুধির-নদীর পার হতে ঐ ডাকে বিপ্লব-হ্রেষা।
প্রেমও আছে সখা, যুদ্ধও আছে, বিশ্ব এমন ঠাঁই
কারুর পা চেটে মরিব না,
[…] মরিব যেদিন মরিব বীরের বেশে
আমার মৃত্যু লিখিবে আমার
জীবনের ইতিহাস।

নজরুলের এই সমাজবিপ্লবী সত্তাটিকে স্মরণে রাখা প্রয়োজন। দুই কারণে। প্রথমত এটি তাঁর অস্তিত্বের মধ্যে রক্তপ্রবাহের মতো বহমান, যা তাকে প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল করে রেখেছে। দ্বিতীয়ত এই পরিচয় জানা থাকলে তাঁর কর্মজীবনের পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রবলভাবে তিনি প্রেমের কবি, কেননা তিনি ঘৃণারও কবি। ও দুই অনুভব এক সঙ্গে যায়, ঘৃণা না থাকলে ভালোবাসা গভীর হয় না। তাঁর শত্রু ও বন্ধু উভয়েই সুস্পষ্ট রূপে চিহ্নিত, শত্রু পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ, মিত্র নিপীড়িত মানুষ।
নজরুলের বিপ্লবী সত্তা তাঁকে আন্তর্জাতিকতার বোধে দৃপ্ত করেছে। সেখানে তিনি সমসাময়িক আধুনিক কবিদের অনেককেই ছাড়িয়ে গেছেন, যাঁরা আধুনিকতার ওপর কাঠামোটা দেখে অভিভূত হয়েছেন ভেতরের দ্বন্দ্বটাকে অবজ্ঞা করে। আজ থেকে আশি-নব্বই বছর আগে নজরুল পুঁজিবাদকে দানব হিসেবে চিনে নিয়েছিলেন, লিখেছেন,
দশমুখো ঐ ধনিক রাবণ,
দশদিকে আছে মেলিয়া মুখ
বিশ হাতে করে লুণ্ঠন,
ভরে-না ক’ ওর ক্ষুধিত বুক।
পুঁজিবাদকে চিনবার এই ক্ষমতা তাঁকে আন্তর্জাতিকতার বোধে দৃপ্ত করেছে। তাঁর আন্তর্জাতিকতা ওপরের ব্যাপার নয়, ব্যাপার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বোধের। যে জন্য বাবু সাব যখন রেলে কাউকে কুলি বলে নীচে ঠেলে ফেলে দেয় তাঁর কাছে তখন সে ঘটনা বিচ্ছিন্ন একটি দুর্ঘটনা থাকে না, সেখানে তিনি জগৎজুড়িয়া দুর্বলের মা’র খাওয়ার বাস্তবতাটাকে দেখতে পান, এবং জানান যে এই নিপীড়ন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী অভ্যুত্থান অবশ্যাম্ভাবী, এবং তা ঘটছেও। কমিউনিস্ট আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের সুর তাল লয় কিছুই তাঁর জানা ছিল না, কিন্তু গানটি ইংরেজী অনুবাদ পেয়েই যে স্বতঃস্ফূর্ত বাংলা অনুবাদ তিনি করেছেন সেটি অতুলনীয়, যেমন যথার্থতায় তেমনি উদ্দীপনায়। স্মরণীয় যে নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতার প্রকাশটি স্থানীয়, কিন্তু অন্তর্গত বিষয়টি আন্তর্জাতিক।
ইতিহাসের ধারায় তাঁর লাঙল পত্রিকা দেখতে পাচ্ছে, এবার এসেছে শূদ্রের পালা। ‘এবার সমাজের প্রয়োজনে শূদ্র নয়-শূদ্রের প্রয়োজনে সমাজ চলবে।’ রথের রশি’তে রবীন্দ্রনাথও দেখেছিলেন যে, সভ্যতার অগ্রগতি নির্ভর করছে রশিতে শূদ্রের হাত-লাগানোর ওপর। তবু এই তফাৎটুক থাকে যে, রবীন্দ্রনাথ ভাবছেন সভ্যতার অগ্রগতির কথা, নজরুলের চোখে আছে সামাজিক মুক্তির চিন্তা। এবং শূদ্রের শাসনে যে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে তেমনটাও তিনি দেখতে পান নি, তাঁর বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে যে শ্রমজীবী মানুষ পুরাতন সমাজ ভেঙে যে নতুন সমাজ গড়বে তাতে পশ্চাৎগামিতা থাকবে না, থাকবে অগ্রগামিতা। নজরুল ভাঙার কথা বলেছেন, ভাঙার জন্য ঝড় ও শাবল চেয়েছেন, কিন্তু সে ভাঙা নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য নয়, নতুন সমাজ গড়বার প্রয়োজনেই। মেহনতি মানুষের জন্য পিছু হটবার কোনো জায়গা নেই, নেই হতাশ হবার কোনো সুযোগ, এ সত্য তিনি পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।
পুঁজিবাদের দুঃসহ দৌরত্ম্যে আজকের বিজ্ঞানীরা ধরিত্রীর মহাবিপদের কথা বলেছেন সেই কতকাল আগে, যখন খনিজ তেল পোড়ানো মাত্র শুরু হয়েছে, গ্যাস এসে পৌঁছায় নি, শুধু কয়লারই ব্যাপক ব্যবহার চলছে তখনই তিনি নবযুগের সম্পাদকীয়তে লিখেছেন, যেভাবে বরফ গলছে এবং অম্লজলের অভাবে আবহাওয়াতে পরিবর্তন ঘটছে তাতে রোজকেয়ামত বা প্রলয় দিন মনে হয় এগিয়ে আসবে।
সঙ্কটের আন্তর্জাতিকতা দেখছেন, কিন্তু সংগ্রামের আন্তর্জাতিকতাকেও ভুলছেন না মোটেই। পুঁজিবাদীদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন,
বাক্সের পানে রেখে চোখ ফ্যাকাশে হয়েছে বুঝি?
বাক্স ও চাবি নেবে না উহারা, কেড়ে নেবে শুধু পুঁজি।
[‘শোধ কর ঋণ’]

এই নতুন যুগের বার্তাবহ হচ্ছে রুশ বিপ্লবীরা, বিশেষ করে তাদের লাল ফৌজ। বয়স যখন বিশ তখন নজরুল করাচী সেনানিবাসে কর্মরত অবস্থায় ‘ব্যথার দান’ গল্পটি লেখেন। ওই গল্পে বেলুচিস্তানের দারা ও সায়েফুল মূলক দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর উভয়েই ‘লাল ফৌজে’ যোগ দিয়েছে। এই বাহিনীর সেনারা ভাড়াটে নয়, তারা সমাজবিপ্লবী। অক্লান্ত পরিশ্রমে, ‘প্রাণের প্রতি ভ্রক্ষেপও না-করে বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য’ তারা বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছে, তাদের বীরত্ব ও ত্যাগের অন্য কোনো পুরস্কার নেই, ‘বিশ্ববাসীর কল্যাণ’ প্রতিষ্ঠা করা ভিন্ন।
গল্পে নজরুল লাল ফৌজের কথাই লিখেছিলেন, কিন্তু পত্রিকায় ছাপার সময় মুজফ্ফর আহমদ বিচক্ষণতার সঙ্গে লাল ফৌজ কেটে সেখানে ‘মুক্তিসেবক সৈন্যদল’ বসিয়ে দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি ছিল ১৯১৯ সালে ‘লাল ফৌজ’ কথাটা উচ্চারণ করাও দোষের ছিল, সেখানে গল্পে হলেও ব্রিটিশ ভারতের তরুণেরা ওই বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে এমন খবর পেলে পুলিশের টিকটিকি নিশ্চয়ই পিছু নিতো। ওই গল্পে আরো একটি ব্যাপার ছিল; শুরুতে নজরুল তাঁর নায়কের নাম রেখেছিলেন নূরুন্নবী, যেমন বাঁধনহারা’র নায়কের নাম নূরু; নূরু নামেই তিনি বন্ধুমহলে পরিচিত ছিলেন। পরে গল্পের পটভূমিতে উপযুক্ত হবে না বিবেচনা করেই সম্ভবত নূরুন্নবীকে বদলে করেন দারা। বোঝা যায় লাল ফৌজে যোগদানকারী দারার মধ্যে নজরুল নিজেকে দেখতে পেয়েছিলেন।
কামাল পাশার তুরস্ক যে সমাজ বিপ্লব ঘটেছে সে নিয়েই তো তাঁর প্রারম্ভিক পর্যায়ের কবিতা লেখা। পরবর্তীতে আয়ারল্যান্ডের কথা এসেছে, এসেছে গ্রীসের খবর। চীনেও তখন বিপ্লবী তৎপরতা চলছে, সে-খবরও আমরা পেয়ে যাই তাঁর কবিতাপাঠে। ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারীতে লেখা ‘সাম্যের জয় হোক’ কবিতায় আছে, ‘চীন ও ভারতে মিলেছি আমরা শত কোটি লোক’ ‘সহিব না আর এই অবিচার, খুলিয়াছে আজ চোখ।’ এর আগে এক কবিতার লিখেছেন,
ক্ষুদ্র অস্ত্র লয়ে কি করিয়া যুদ্ধ করে চীন
অস্ত্র ধরিতে পারে না, যাহারা অন্তরে বলহীন
[…]
সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকা ভাই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ভবে,
এই অস্ত্রেই সর্ব অসুর দানব বিনাশ হবে
(‘বোমার ভয়’)
সমাজবিপ্লবী অবস্থানে ছিলেন বলেই কংগ্রেসের রাজনীতি তাঁর কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য হয় নি। কংগ্রেস স্বরাজের কথা বলছে, নজরুল লিখছেন,
ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নূন
বেলা বয়ে যায়, খায়নিক বাছা, পেটে তার জ্বলে আগুন।
[…]
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান তুমি আজিও আছ কি? কালি ও চুন
কেন ওঠে নাক’ তাহাদের গালে, যারা খায় ওই শিশুর খুন?
(‘আমার কৈফিয়ত’)
১৯২৭-এ কানপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছে, নজরুল তাঁর লাংগল-এ এর নাম দিয়েছেন বড়দিনের ছুটিতে All India Political Tubri Competition.,’ বলেছেন তুবড়িবাজিতে কাজ হবে না, ভূমি-স্বত্বে পরিবর্তন আনতে হবে। জানাচ্ছেন,
ভূমি-স্বত্বের সঙ্গে ভারতীয় স্বরাজের প্রতিষ্ঠার এত নিকট সম্বন্ধ যে সে সমস্যার সমাধান না হলে স্বরাজ আসতেই পারে না। তাই প্রজাস্বত্ব আইনের আলোচনার সময় সমস্ত নেতারা কি করেন, আমরা দেখার জন্য উৎসুক আছি। যাঁরা বলেন স্বরাজ হলে ওসব ঠিক হবে- তাঁরা গোঁড়াতেই ভুল করেন। (‘পোলিটিক্যাল তুবড়ি বাজি’)
ভূমির মালিকানা বিত্তবানদের হাতে থাকবে অথচ সাধারণ মানুষ, যাদের অধিকাংশই কৃষক, তারা মুক্ত হয়ে যাবে এমন অলীক কল্পনাকে কবি নজরুল কখনোই প্রশ্রয় দেন নি। কংগ্রেসের রাজনীতিকে যেভাবে তিনি হাস্যকর করে দিয়েছেন তা অসামান্য। যেমন, ‘ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসে’র মধুর আশ্বাসবাণী সম্বন্ধে লিখেছেন :
কোরাস :
বগল বাজা দুলিয়ে মাজা
বসে কেন অমনি রে!
ছেঁড়া ঢোলে লাগাও চাটি
মা হবেন আজ ডোমনী রে।
রাজা শুধু রাজাই রবেন
পগার-পারে নির্বাসন
রাজ্য নেবে দু’ভাই মিলে
দুর্যোধন আর দুঃশাসন
[…] মাভৈ ! এবার স্বাধীন হব
যাই বলেছি, পৃষ্ঠে ঠাস!
পড়ল মনে, পীঠ-স্থানএ,
ডোমিনিয়ান স্টাটাস।
তাঁর দূরদৃষ্টিতে নজরুল যা দেখতে পেয়েছিলেন সাতচল্লিশে তো অবিকল তাই ঘটেছে, পৃষ্ঠে ঠাস করে যা পড়েছে তার নাম ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস; ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে গেছে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে এবং শাসন ক্ষমতা চলে গেছে দুষ্ট দু’ভাই, দুর্যোধন আর দুঃশাসনের হাতে।
১৯৩১-এ বিলেতে যখন রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স চলছে সেই সময়েই কলকাতায় বসে নজরুল লিখছেন,
ডিম্-গোলাকার গোল-টেবিল
করবে সার্ভ অশ্ব-ডিম,
[…]
আনবে স্বরাজ ব্রিটিশ-বর্ন
অস্ট্রেলিয়ার ভাইপোকে।
[…]
বাধাসনে আর লট্ঘাটি
দোহাই বাবা চ্যাংড়া থাম্!
এমন ফলার কাঁচকলার
তোরাও পাবি ল্যাংড়া আম।
তরুণ বিদ্রোহীদেরকে কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কাঁচকলা ও ল্যাংড়া আমের, বলেছে সাগর মন্থন করে দুধ না আনতে পারলেও টক দই ঠিকই নিয়ে আসবে। অন্যত্র, নজরুল দেখতে পাচ্ছেন কংগ্রেসের ‘রাজী’ ‘না-রাজী’ দু’ভাগের দ্বন্দ্ব নিয়ে ‘জোর জমিয়াছে খেলা/ ক্যালকাটা মাঠে সহসা বিকাল বেলা।’
খেলা দেখ, দেখ খেলা
রাজী কি না-রাজী জয়ী হলো,
বলো তোমরাই সাঝ-বেলা।
কবুতরগুলি ফেরে নাই ঘরে,
ঘুরিছে মাথার ’পর,
কাহারা জিতিল, দেশে গিয়া
শুনাবে খোশখবর।
মজাদার এই খেলায় দুর্গতি যা ঘটবার সেটা ঘটছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার, সেই ফুটবলটি দু’পক্ষের পায়ে সমানে ঘা খেয়েই চলেছে। সাইমন কমিশন এসেছে, তারা দেখতে পেয়েছে যে এদেশে,
ত্যক্তের চেয়ে ভক্তই বেশি
আহা হা ভক্ত বেঁচে থাক
বলছে,
বৃহত্তম জু’ দেখিনু জীবনে
প্রথম দু’পেয়ে জন্তু
তবে আশঙ্কার ব্যাপার একটাই, সেটা হলো,
কালো চামড়ার ভিতরে ওদের
আমাদেরি রক্ত
এ যদি না হতো- শ্বাশ্বত হত
ও দেশে মোদের তক্ত।
সেই ১৯২০ সালে নজরুলের বয়স যখন একুশ তখনই সান্ধ্য দৈনিক নবযুগের সম্পাদকীয়তে নজরুল তাঁর এই উপলব্ধি জানিয়ে দিয়েছেন যে খোসামদি বা গুপ্ত হত্যা কোনোটাতেই কাজ হবে না। লিখেছেন,
উদমো ষাঁড়ের মত দেওয়ালের সঙ্গে গা ঘেঁসড়াইয়া নিজের চামড়া তুলিয়া ফেলা হয় মাত্র। দেওয়াল প্রভু কিন্তু দিব্যি দাঁড়াইয়া থাকেন। তোমার বন্ধন, ওই সামনের দেওয়ালকে ভাঙ্গিতে হইলে একেবারে তাহার ভিত্তিমূলে শাবল মারিতে হইবে। হুজুগে ফল মিলবে না, প্রয়োজন ধারবাহিক আন্দোলনের সাপ লইয়া খেলা করিতে গেলে তাহাকে দস্তুর মত সাপুড়ে হওয়া চাই, শুধু একটু বাঁশি বাজাইতে পারিলেই চলিবে না। (‘ভাব ও কাজ’)
১৯৪১-এ ‘আমার লীগ কংগ্রেস’ প্রবন্ধে দু’দলের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সম্বন্ধে নজরুলের বক্তব্য,
এক খুঁটিতে বাঁধা রামস্থাগল, এক খুঁটিতে বাঁধা খোদার খাসি, কারুর গলার বাঁধন টুটল না, অথচ তারা তাল ঠুকে এ ওঁকে ঘুঁস মারে। দেখে হাসি পায়।
এদের রাজনীতিতে যে মুক্তি আসবে না সেটা পরিষ্কার বুঝতে পেরে ১৯২৫ সালেই নজরুল উদ্যোগ নিয়েছিলেন একটি বিকল্প রাজনৈতিক দল গঠনের। নাম দিয়েছিলেন, ‘শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়’। সাধারণ স¤পাদকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি নিজে। দলের উদ্দেশ্য ছিল, ‘সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ লাভ।’ দল গঠনের আবশ্যকতার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, খোসামুদি এবং গুপ্তহত্যা কোনোটাই যেহেতু কাজে লাগে নাই তাই বোমা এবং পিস্তলের শক্তি অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী গণআন্দোলনের চলমান শক্তিকে প্রয়োগ করা। সেই সঙ্গে দরকার এবং ‘শ্রেণীগত স্বার্থত্যাগী ভদ্র যুবকদের সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষকের সংযোগ’ সাধন।
ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ‘এই দল শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থের জন্য বুঝিবেন’। যারা নিজের হাত পা মাথা খাটিয়ে নিজের জীবিকা অর্জন করে সেই ভদ্রলোকদেরকেও শ্রমিক হিসাবে গণ্য করা হবে, বলা হয়েছিল।
কর্মসূচীর মধ্যে ছিল আধুনিক কলকারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামওয়ে প্রভৃতির মুনাফার জন্য ব্যবহার না করে দেশের উপকারের জন্য ব্যবহার করা এবং তৎসংক্রান্ত কর্মীদের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিচালিত করা। ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছিল, ভূমির চরম স্বত্ব থাকবে ‘স্বায়ত্তশাসন- বিশিষ্ট পল্লীতন্ত্রের হাতে’- যে-পল্লীতেও থাকবে সকল শ্রেণীর শ্রমজীবীর নিয়ন্ত্রণে। (নজরুল রচনাবলী, ৪, ৭৬)
বুঝতে অসুবিধা নেই যে মডেলটি ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার। সমাজবিপ্লবী আন্দোলনের জন্য শিক্ষিত মানুষকে জনগণের কাছে যেতে হবে। তবে যেতে হবে শ্রেণীচ্যুত হয়ে, তাদেরই একজন হিসাবে। নজরুলের ভাষায়,
তাদের কাছে টর্চ লাইট হাতে নিয়ে গেলে তারা সরে দাঁড়াবে, কেরোসিনের ডিবে হাতে করে গেলে তার থেকে যত ধোঁয়াই বের হোক না কেন তাদেরকে আকর্ষণ করবে।
এবং
যা বলার তা বলতে হবে। কিন্তু যেন মাস্টারী ভাব ধরা না পড়ে। (ঐ, ৪, ১১০)
মেহনতি মানুষের কাছে যারা যাবে তাদের ‘অন্তরে’ বিপ্লবের আগুন থাকা চাই, থাকা চাই বেদনার বোধ, নইলে,
অগণন জনগণ নাহি আসে তাহাদের আহ্বানে
কানে বাজে শুধু জয়ধ্বনি সে ধ্বনি বাজে না ক’ প্রাণে।
এবং পরিণতি দাঁড়ায়
সবাই মোড়ল, সবাই শুনিবে আপন জয়ধ্বনি;
সৈনিক নাই, শত শত দলে শত শত সেনাপতি;
তখ্তে চড়িতে পারিল না কেউ, তক্তায় চড়ে নাচে;
তক্তায় ঠাঁই নাই দেখে নেতা হতে উঠে বসে গাছে।
৫
‘অগ্নিগিরি’ নামে নজরুলের একটি ছোটগল্প আছে। তার নায়ক সবুর মাতাপিতাহীন এক কিশোর। এককালে বিত্তবেসাত ছিল, এখন নেই। এখন সে আশ্রিত হিসাবে থাকে একটি পরিবারে, যারা তার খুবই আদর-যত্ন করে। কিন্তু পাড়ার বখাটে ছেলেরা সুযোগ পেলেই পথেঘাটে সবুরকে উত্যক্ত করে। বেচারা সবুর মুখ বুজে সব সহ্য করে। কিন্তু হঠাৎ টের পাওয়া গেল যে তার ভেতরে অগ্নিগিরি আছে। সেদিন জ্বালাতনের মাত্রাটা একটু বেশিই হয়েছিল, এবং তা নিয়ে বাড়ির যে-মেয়েটির সে গৃহশিক্ষকতা করতো সেই নূরজাহান তাকে ধিক্কার দেয়ায় সবুর ওই ছেলেদের মুখোমুখি হয়। সে একা, কিন্তু তার হাতে উত্ত্যক্তকারীরা একের পর এক ধরাশায়ী হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাদের একজন, নাম তার আমীর, ছুরি উঁচিয়ে সবুরকে আঘাত করতে যায়। সবুর সেটি প্রতিহত করে, তাতে উল্টো আমীরের বুকেই ছুরি বসে যায়, এবং তার মৃত্যু ঘটে। সবুরের জেল হয়ে যায় সাত বছরের। সবুরের শাস্তি লাঘব হতো, হয়তো-বা সে মুক্তিই পেয়ে যেতো যদি উকিল লাগাতো, কিংবা উচ্চ আদালতে আপীল করতো। গৃহস্বামী পরিবারটি টাকা খরচে উদগ্রীব ছিলেন, সবুরকে তাঁরা আপন সন্তানের মত ভালবাসতেন। কিন্তু সবুর রাজি হয় না। নূরজাহানকে সে জানায়, ইতিমধ্যেই তাদের অনেক ক্ষতি সে করেছে, ঋণের বোঝা আর বাড়াবে না। জেলখানায় দরজাটি বন্ধ হবার আগে নূরজাহানকে সবুর বলে, ‘আমায় ক্ষমা করো নূরজাহান। আমি তোমাদেরকে আমার কথা ভুলতে দিতে চাইনে বলেই এই দয়াটুকু চাই।’
সবুরের ভেতর নজরুল আছেন। ওই কিশোর অনেক দুঃখ ও অপমান সহ্য করেছে, কিন্তু তার ভেতরকার অগ্নিগিরি জেগে উঠেছে অন্যকিছুতে নয়, নূরজাহানের ধিক্কারে। নজরুলও বিদ্রোহ করেছেন, এবং সমাজ বিপ্লবী হয়ে উঠেছেন, শুধু দুঃখ ও অপমানের জ্বালায় নয়, নীরব ধিক্কারের কারণেও। ওই ধিক্কার শুনেছেন তিনি নিপীড়িত মানুষের কাছ থেকে। তাঁর পক্ষে জেগে ওঠা ভিন্ন উপায় ছিল না।
আনসার পারে নি, আনসার যক্ষায় আক্রান্ত হয়েছে, তার মৃত্যু আসন্ন; নজরুল নিজেও পারেন নি, তিনি শেষ পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর অপারগতার দায়িত্ব অনেকটাই যে-আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে তিনি যুক্ত রেখেছিলেন সেই আন্দোলনের। তরুণ সবুর সাত বছর জেল খাটবে, সে ভরসা করে ওই সময়ের মধ্যে তার হাতে যে রক্ত লেগেছিল সেটা মুছে যাবে; জেল থেকে বের হয়ে নূরজাহানদেরকে সে খুঁজে নেবে, এবং নতুন সমাজে নতুনভাবে জীবন শুরু করবে। যেন নজরুলের প্রত্যাশিত সমাজেরই স্বপ্নছবি।
এমন একটি সমাজ তিনি চেয়েছিলেন যেখানে মানুষের জীবন হবে সুন্দর ও স্বাভাবিক। তিনি ভাঙতে চেয়েছেন, নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য নয়, নতুন করে গড়বার জন্যই, যেকথা তিনি বারবার বলেছেন। সুন্দরের সাধক ছিলেন বলেই অসুন্দরের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই। লড়াইটা মুক্তির। তাঁর গানে চরণ আছে, ‘আমারে দেব না ভুলিতে।’ আমরা তাঁকে ভুলতে পারবো না।
তাঁর কাজটা সাংস্কৃতিক। ওই সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সাহিত্যেরও একটি ধারাপ্রবাহ চলছিল, তরুণ কবিরা তৈরি করেছিলেন, তাঁরা আধুনিকতার দাবিদার ছিলেন। প্রকৃত আধুনিকতা কাকে বলে সে-বিষয়ে ‘ন্যাশনালিজম’ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি বক্তৃতায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আছে। তিনি বলেছেন, প্রকৃত স্বাধীনতা হলো মনের মুক্তি, রুচির দাসত্ব নয়। নজরুলের সমসাময়িক ‘আধুনিক’ কবিরা পশ্চিমের সাহিত্যের অবক্ষয়ধর্মী ও প্রতিক্রিয়াশীল রুচির দাসত্বের আবর্তে পড়ে গিয়েছিলেন, নজরুল ছিলেন ব্যতিক্রম, তাঁর আধুনিকতাই ছিল যথার্থ, কেননা মনের দিক থেকে তিনি ছিলেন মুক্ত, এবং রুচির দাসত্বের ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখান নি।
নজরুল থাকবেন। আমাদের জীবনের আনন্দ ও নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য থাকবেন, থাকবেন আমাদের স্বপ্ন ও সংগ্রামের সাথী হিসাবে। ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে চিনে ছিল, পাকিস্তানীদের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র তাঁর কাব্যে অবাঞ্ছিত অংশ খুঁজতে ব্যস্ত হয়েছিল, আমাদের সমাজে যদি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসন্ন হয়ে পড়ে তবে সেদিন রাষ্ট্র এই কবির বাণীকে নিয়ে হয়তো অস্বস্তিতে পড়বে, কিন্তু সমাজ তাঁকে কাছের মানুষ হিসাবে পাবে। ইতিমধ্যে অন্যায় ও অবিচারকে সহ্য করার দরুন নজরুলের রচনা আমাদেরকে ধিক্কার দেবে, যেমন নূরজাহান দিয়েছিল তার আপনজন সবুরকে, যদি আমরা তাঁর রচনা পাঠ করি।