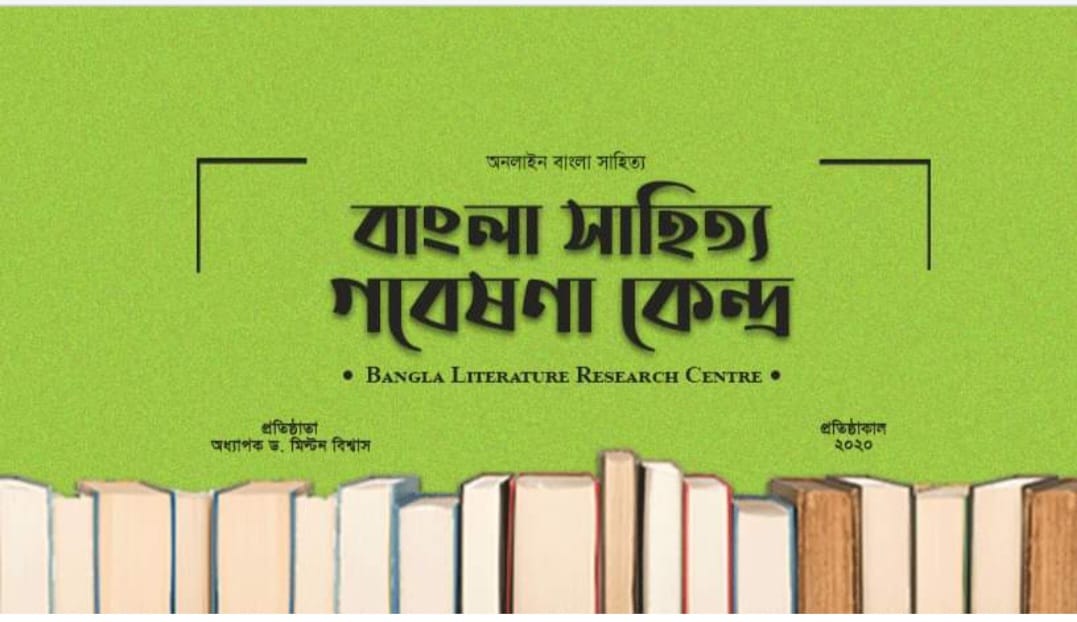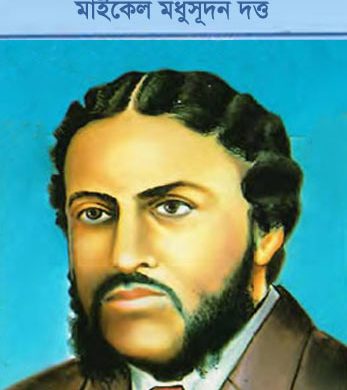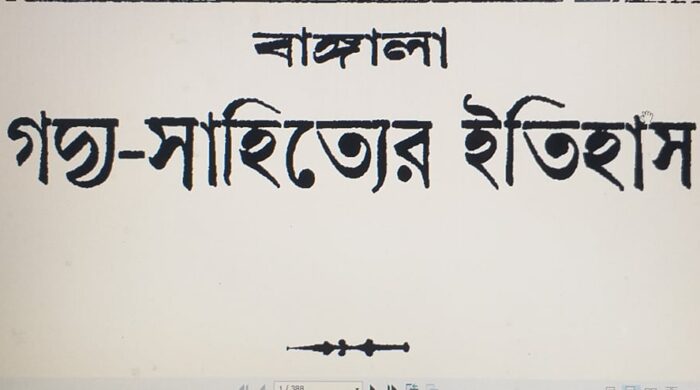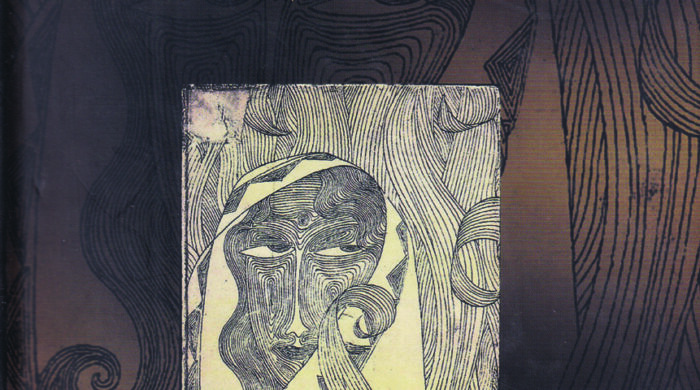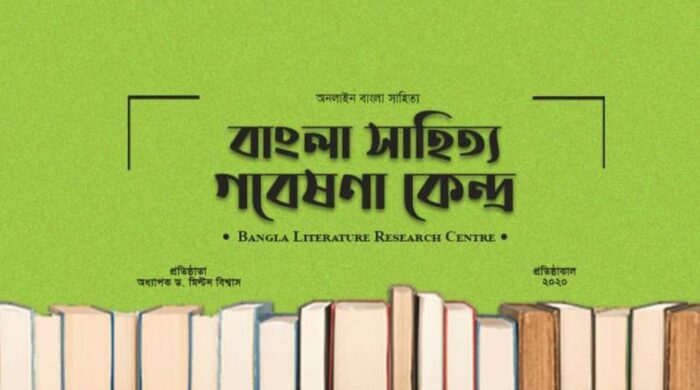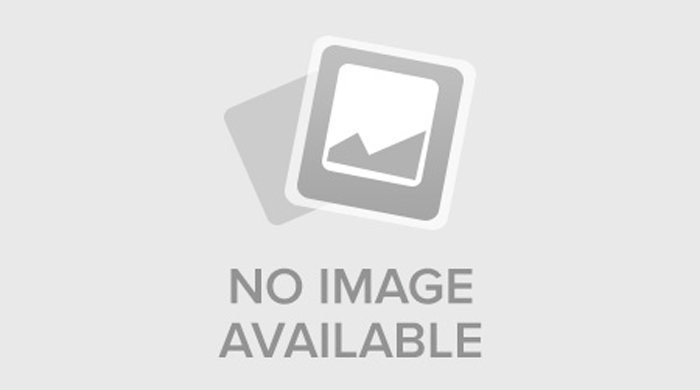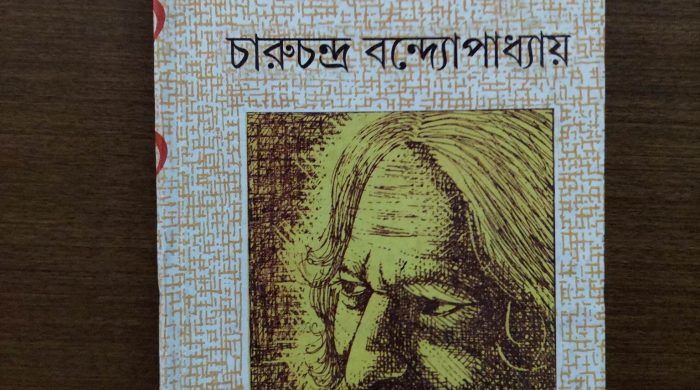চন্দন আনোয়ার।।
জন্মের পর প্রথম পা মধ্যবিত্তের উঠোনে ফেলে, আমৃত্যু মধ্যবিত্তের পীড়নে দুর্দশাগ্রস্ত জীবন অতিবাহিত করেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই সম্ভবত সেই সাহিত্যিক, যে কিনা মধ্যবিত্তের আলগা আভিজাত্যের বাকল চাঁচাছোলা করে একেবারে ন্যাংটো করে ছেড়েছেন। সামান্য সহানুভূতিও পায়নি এই শ্রেণি মানিকের কলমের কাছে। স্বশ্রেণির স্বরূপ সন্ধানে তিনি ছিলেন কাপালিকের মতোই নিষ্ঠুর ও নির্মম। বিশেষত, মানিক নিজেই যখন বলেন, এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাশ্য ও মুখোশ-পরা হীনতা, স্বার্থপরতা তাঁর মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে তখন আর আমাদের বুঝে নিতে বাকি থাকে না যে, বাস্তবতাবর্জিত কল্পনাপ্রসূত ন্যাকা সাহিত্য ও ভ- সমাজকে ভেঙে গুড়িয়ে দেবেন মানিক। বিশশতকের সামাজিক বাস্তবতা এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হিসেবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাকে এ পথে ঠেলেছে।
মূলত, মানিক পরিবারের বিকাশের মধ্যেই নিহিত আছে উনিশ শতকের বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের ইতিহাস। বিক্রমপুরের নিভৃত পল্লির এক পুরোহিত পরিবার কীভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণিতে উঠে আসল এবং কলকাতার অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত জীবনে কী পরিমাণ বাস্তব সংকটের মুখোমুখি হতে হল-এই ইতিহাসের মধ্যেই খোঁজ মিলবে সমগ্র বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের উত্থানের রহস্য। ঢাকার বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালবদিয়া গ্রামের সন্তান মানিক পিতা শ্রী হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭০-১৯৫৮) উত্তরাধিকারসূত্রে কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্য হলেও পুরোহিত পিতা করুণাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসার উদাসিন, ভবঘুরে স্বভাব এবং যজমনদের দান গ্রহণে লজ্জা-ই মূলত পরিবারটিকে ফেলেছিল চরম দুর্দিনে। এরিমধ্যে এ পরিবারে ঘটে গেছে একটি স্মরণীয় ঘটনা। শ্রী হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় দাদা বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় চরম অর্থকষ্ট, বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হতে ত্রি-বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অল্প কিছুদিনের বিরতিতে সরকারি চাকুরিতে ঢুকে ছিলেন আসাম প্রদেশে। শ্রী হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ও অগ্রজের পথ ধরেই হেঁটেছিলেন এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অসীম মনোবলের জোরেই গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি অর্জন করতে পেরেছিলেন। প্রথমে শিক্ষকতা দিয়ে শুরু করলেও পরে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যা প্রদেশের পি ডব্লি¬উ ডি’র ক্লার্ক হিসেবে সরকারি চাকুরি জীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে সেটেলমেন্টের কানুনগো পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন। পদোন্নতির একপর্যায়ে তিনি উপনীত হয়েছিলেন সাবডেপুটি কালেক্টর পদে। সেই সাথে বিক্রমপুরের মধ্যযুগীয় পুরোহিত পরিবারের সন্তান ঐতিহ্য ভেঙে প্রবেশ করেন নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের জীবনে। বিশশতকের কলকাতার বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির খাতায় নাম লিখিয়ে মানিক পিতাও হয়ে গেলেন তাদেরই একজন।
বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ‘মধ্য-বিশ-শতকের বাংলাদেশের সামাজিক বিশৃঙ্খলার ঘনিষ্ঠ রূপকার’। (বসু, ৮৬) এ কৃতী কথাশিল্পীর জন্মও (১৯০৮) হয়েছে জাতির এক সংকটকালে। তখন ছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫) উত্তাল সময়।তাছাড়াও ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের বেশ কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনাসূত্রে বিশশতকের ভারতবর্ষ অতিক্রম করছিল এক অস্থির নৈরাজ্যের সময়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ রদ ছিল বাঙালির স্মরণাতীতকালের আক্ষেপ। আশাভঙ্গের নিদারুণ যন্ত্রণায় যুবকশ্রেণি তখন অস্থির, তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল। অব্যবহিতকাল পরেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসেবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং ক্রমাগত কর্মের বাজার ছোট হয়ে আসায় এই প্রথম সংকটের মুখোমুখি দাঁড়াতে দেখি মধ্যবিত্তের জীবনকে। যুদ্ধোত্তরকালে ব্রিটিশ সরকারের যে স্বরাজ প্রতিশ্রুতি ছিল, পরে যা চাতুরিতে রূপ নিয়েছিল এবং এরিমধ্যে জালিয়ানবাগের হত্যাকাণ্ডে (১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯) বিস্মিত, শংকিত, ক্রোধান্বিত ভারতবাসী অসহযোগ আন্দোলনের পথে নামলে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছিল দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় ছিল যে, যুবসমাজের আশাতীত অংশগ্রহণে আন্দোলন অগ্নিরূপ নেবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই গান্ধীজী পিছু ফিরলেন। ফলে বিশাল প্রত্যাশা রূপ নিয়েছিল সীমাহীন নৈরাশ্যে। যার প্রমাণ, আন্দোলনকারী যুবকদের একটা বিরাট অংশ কংগ্রেসেরই চরমপন্থিদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল। সরকার উৎখাতের জন্য বেছে নিয়েছিল সন্ত্রাসের পথ। গোপীনাথ সাহা, ক্ষুদিরাম বসু, সূর্যসেন, যতীন দাস প্রভৃতি দুঃসাহসী শহীদদের আদর্শ ছিল তাদের সামনে। অবদমিত যৌবনশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে বিকল্প সন্ত্রাসের পথে। নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে তারা যেন এক ভয়ানক ভাঙনের ভয়ঙ্কর নেশায় মেতে উঠেছিল। তাছাড়া প্রচলিত মধ্যবিত্ত জীবনের মূল্যবোধে তারা নির্ভর ও আশ্রয় কোনটাই পাচ্ছিল না। সেই সাথে বিশশতকেই কৃষ্ণের মতো বিজ্ঞান তাঁর সর্বরূপ দেখিয়েছে। মানুষের সকল সম্ভাবনার শক্তিকে কব্জায় নিয়ে গতি ও শক্তি দিয়ে মানুষকে অসাধ্যের অমরাবতীতে নিয়ে গেছে বিজ্ঞান, আবার এই বিজ্ঞান-ই ভয়ানক ধ্বংসের ক্ষমতা নিয়ে অসুরের মতো মানুষ নিধন করে মানুষের সমস্ত অর্জন ও পুরো সভ্যতাকেই উপহাসের মুখে ঠেলেছে। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর বিষময় বিকাশ ঘটেছিল বিশশতকের প্রথম দুই দশকেই। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনোবিকলন ধারণা সভ্য মানুষেরা ঘাড়গুঁজে মেনে নিয়েছে। কার্ল মার্কস প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রের প্রতি অতিশয় প্রাবল্যে ধাবিত হওয়ায় এবং আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ ও ডারউনের বিবর্তনবাদকেও অস্বীকার করতে না পারায় বিশশতকের সামাজিক-রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক জীবনের ঠিকানা হয়ে পড়েছিল অনির্দিষ্ট, মাঝিবিহীন পাল তোলা নৌকোর মতো। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিশশতকের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনোজাগতিক সমস্যা-সংকট, পরিবর্তন-বিবর্তনের সব বাস্তবতা নিয়ে গড়ে উঠেছিল মানিক মানস; তাঁর গল্পের মধ্যবিত্তের প্লাটফর্ম।
নিঃসন্দেহে, বিশশতকের বাংলাসাহিত্যে কল্লোল-কালিকলম-প্রগতিগোষ্ঠীর আবির্ভাব ছিল বিরাট আশীর্বাদের। তারা সকলেই ছিলেন যুগ সত্যের উপাসক, রবীন্দ্র ঘরানার বাইরের বাসিন্দা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন ও মনন পরিপূর্ণভাবেই কল্লোলীয় চেতনার সমর্থক ছিল বললে ভুল বলা হবে না, তবে মানিকের চিন্তা-চেতনা ছিল আরো অগ্রসরমান। জীবন, জগৎ, ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে কল্লোলের লেখকদের মধ্যবিত্তসুলভ রোমান্টিক ভাবাবেগের প্রশ্রয় দেননি মানিক। বিশশতকের ব্যক্তিকেন্দ্রিক জটিলতার যে বিচিত্ররূপ, তা ছিল মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের জীবনপ্রণালির বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না কল্লোলের শিক্ষিত তরুণ লেখকদের। তারা যে জীবনকে দেখেছেন, তা বিদেশি সাহিত্য পাঠ এবং কলকাতার চারপাশের কিছু চালচিত্র। পিতার কর্মসূত্রে বিচিত্র জনপদের বিচিত্র মানুষের জীবনাচরণের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেছিল মানিকের ছেলেবেলাতেই। মানিক শুধু কলকাতার নয়, সারা বাংলার গ্রাম-শহরের নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষদের নিত্যদিনের জীবনের বাস্তবরূপ দেখেছেন আবেগের চশমা খোলা চোখে। এ কাজে সক্রিয় থেকেছে মানিকের আশৈশব বিজ্ঞানকেন্দ্রিক জীবন জিজ্ঞাসার প্রাবল্য। মানব মনের প্রকৃতি ও প্রবণতা বিশ্লে¬¬ষণে এবং ভিতরে লুকায়িত অমিত সম্ভাবনার আবিষ্কারে মানিকের বিস্ময়কর সহজাত ক্ষমতা ছিল। তাঁর চোখ ছিল মানব সভ্যতার উৎসের দিকে। আদিম ও শক্তিশালী মানুষের প্রতি ছিল মানিকের পক্ষপাতিত্ব। প্রাগৈতিহাসিক জীবন তাঁর প্রার্থিত। পরাজয় নয়, অনন্ত সম্ভাবনায় মানুষের বিজয়-ই তাঁর কাম্য। এজন্যে আদিম হিংস্রতাকেও মেনে নিতে তাঁর আপত্তি নেই। তাঁর গল্পের অধিবাসীরা পরাজয় মেনে নেয় না। জীবন বাজি রেখে লড়ে। প্রয়োজনে মৃত্যু বা আত্মহত্যার পথে হাঁটে, তবু শেষ পর্যন্ত লড়ে। তাঁর গল্পের অসুস্থ, বিকারগ্রস্ত, উদ্ভ্রান্ত প্রকৃতির চরিত্রগুলো বস্তুত আমাদেরই রুগ্নতার প্রতিবিম্ব। আর তাতে সন্দেহ নেই যে, ‘তাঁর-চোখে দেখা জীবনের আতঙ্কজনক আর্তি ঐ পথে ঠেলেছে।’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক মানুষ কিন্তু চোখে পরেছিলেন আদিম চশমা। ফলে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের এপিঠ-ওপিঠ দেখেছিলেন, এবং তাঁর চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি কৃত্রিম আভিজাত্যের নেপথ্যের স্বার্থপরতা, শঠতা, লোভ, লুটপাট তথা কুটকামনার সর্পিল প্রবাহ।
ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে মানিক সাহিত্যে। মানব মনের চেতন-অবচেতন-নির্জ্ঞানস্তরের এমন নির্মোহ-নিরপেক্ষ প্রতিফলন মানিকের লেখা ছাড়া আর কোথাও চোখে পড়ে না। যা দেখা যায় তাতে নারী-পুরুষের আদিম দৈহিক যৌনতার-নগ্নতার উচ্ছ্বাসই বেশি। তবে মানিক এ সত্যও উপলব্ধি করেছিলেন, যৌন সমস্যার মতোই মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যাও গুরুত্বপূর্ণ। বরং তা যৌনপ্রবৃত্তির চাইতেও মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণের বেশি মৌলিক শক্তি। মানিক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, ফ্রয়েডের মনোবিকলন চিন্তাতে জীবনের সামগ্রিক পরিচয় নেই, এক বিশেষ অংশ মাত্র। বাস্তববাদী মানিক বেশিদিন মনোবিকলন ধারণাকে আঁকড়ে থাকতে পারেননি। মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তিই তাঁর চূড়ান্ত কাম্য ছিল। কেননা ‘ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা না জানলে কিছুই ভালো করে জানা যায় না।’ সম্ভবত এই কারণেই যোগ দিয়েছিলেন কিংবা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন কম্যুনিস্ট পার্টিতে (১৯৪৩)। মার্কসবাদ পড়তেন প্রচুর এবং নিজেকে মার্কসবাদী লেখক হিসেবে সোচ্চার কন্ঠে ঘোষণা করতে কুণ্ঠাবোধ ছিল না। মানিকের রাজনৈতিক আদর্শ ও জীবনর্শন প্রসঙ্গে তাঁর ভিতরে বিশ্বাস ও কর্মের কোনপ্রকার ফাঁক-ফাঁকি-চালাকি ছিল না। এবং নিজস্ব চিন্তায় ছিলেন অনমনীয় ও অবিচল। ফলে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির সোপান মার্কসবাদ-এই পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই তিনি ঢুকে পড়েছিলেন মার্কসীয় ঘরানায়।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় তাঁর ১৬টি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই সাথে দুটি গল্পসংকলনও প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর জীবদ্দশাতেই গ্রন্থভুক্ত গল্পের সংখ্যা শ-দুয়েক। এছাড়াও প্রচুর অগ্রন্থিত গল্পও রয়েছে। মানিকের সমগ্র গল্পকে দুটি পর্যায়ে বিভাজন করা যায়। ১৯২৮ হতে ১৯৪৩ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পূর্বে লেখা গল্পগুলো প্রথম পর্যায়ভুক্ত, আর ১৯৪৪ হতে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পরে লেখা গল্পগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ, প্রকাশকাল, গল্পের সংখ্যা এবং গল্পের নামের একটি তালিকা এখানে উপস্থিত করা যায় :
১. অতসীমামী (১৯৩৫)- ১০টি : অতসীমামী, নেকী, বৃহত্তর-মহত্তর, শিপ্রার অপমৃত্যু, সর্পিল, পোড়া কপালী, আগন্তুক, মাটির সাকী, মহাসঙ্গম, আত্মহত্যার অধিকার।
২. প্রাগৈতিহাসিক(১৯৩৭)- ১০টি : প্রাগৈতিহাসিক, চোর, মাটির সাকী, যাত্রা, প্রকৃতি, ফাঁসি, ভূমিকম্প, অন্ধ, চাকরী, মাথার রহস্য।
৩. মিহি ও মোটাকাহিনী (১৯৩৮)- ১২টি : টিকটিকি, বিপত্নীক, ছায়া, হাত, বিড়ম্বনা, রকমারী, কবি ও ভাস্করের লড়াই, আশ্রয়, শৈলজ শীলা, খুকী, অবগুণ্ঠিত, সিঁড়ি।
৪. সরীসৃপ(১৯৩৯)- ১২টি : মহাজন, মমতাদি, মহাকালের জটারজট, গুপ্তধন, প্যাঁক, বন্যা, বিষাক্ত প্রেম, দিক পরিবর্তন, নদীর বিদ্রোহ, মহাবীর ও অচলার ইতিকথা, দুটি ছোট গল্প, সরীসৃপ।
৫. বৌ (১৯৪৩)- ১৩টি : দোকানীর বৌ, কেরানীর বৌ,
সাহিত্যিকের বৌ, বিপত্নীকের বৌ, তেজী বৌ, কুষ্ঠরোগীর বৌ, পূঁজারীর বৌ, রাজার বৌ, উদারচরিতানামের বৌ, প্রৌঢ়ের বৌ, সর্ববিদ্যাবিশারদের বৌ, অন্ধের বৌ, জুয়ারীর বৌ।
৬. সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩)- ১৩টি : সমুদ্রের স্বাদ, ভিক্ষুক, পূজা কমিটি, আপিম, গুণ্ডা, কাজল, আততায়ী, বিবেক, ট্রাজেডীর পর, মালী, সাধু, একটি খোয়া, মানুষ হাসে কেন।
৭. ভেজাল (১৯৪৪)- ১১টি : ভয়ঙ্কর, রোমান্স, ধনজন গৌরব, মুখে-ভাত, মেয়ে, দিশেহারা হরিণী, মৃতজনে দেহ প্রাণ, যে বাঁচায়, বিলামসন, বাস্, স্বামী-স্ত্রী।
৮. হলুদ পোড়া (১৯৪৫)- ১১টি : হলুদ পোড়া, বোমা, তোমরা সকলেই ভাল, চুরি চুরি খেলা, ধাক্কা, ওমিলনাইন, জন্মের ইতিহাস, অন্ধ, ধাঁধা, ফাঁদ, ভাঙ্গা-ঘর।
৯. আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬)-১৬টি : আজ কাল পরশুর গল্প, দুঃশাসনীয়, নমুনা, বুড়ী, গোপাল শাসমল, মঙ্গলা, বেড়া, নেশা, তারপর, স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই, শক্রমিত্র, রাঘব মালাকর, যাকে ঘুষ দিতে হয়, কৃপাময় সামন্ত, নেড়ী, সামঞ্জস্য।
১০. পরিস্থিতি (১৯৪৬)- ১২টি : প্যানিক, সাড়ে সাত সের চাল, প্রাণ, রাসের মেলা, মাসিপিসি, অমানুষিক, পেট ব্যাথা, শিল্পী, কংক্রীট, রিক্সাওয়ালা, প্রাণের গুদাম, ছেঁড়া।
১১. খতিয়ান (১৯৪৭)- ১০টি : খতিয়ান, ছাঁটাই রহস্য, চক্রান্ত, কানাই তাঁতি, ভণ্ডামি, চোরাই, চালক, টিচার, ছিনিয়ে খায়নি কেন, একান্নবর্তী।
১২. মাটির মাশুল(১৯৪৮)- ১৫টি : মাটির মাশুল, বক্তা, ঘর ও ঘরামি, পারিবারিক, ট্রামে, ধর্ম, দেবতা, নব আলপনা, ব্রীজ, ভয়ঙ্কর, আপদ, পক্ষান্তর, সিদ্ধপুরুষ, হ্যাংলা, বাগদী পাড়া দিয়ে।
১৩. ছোটবড় (১৯৪৮)- ১৪টি : ভালবাসা, তথাকথিত, চালক, ছেলে-মানুষি, স্থানে ও স্তানে, স্টেশন রোড, পেরানটা, দীঘি, হারানের নাত জামাই, ধান, সাথী, গায়েন, নব আলপনা, ব্রীজ।
১৪. ছোট বকুলপুরের যাত্রী(১৯৪৯)- ৮টি : ছোট বকুলপুরের যাত্রী, বাগদী পাড়া দিয়ে, মেজাজ, প্রাণধিক, ঘর করলাম বাহির, সখী, নিচু চোখে দু আনা দু পয়সা, নিচু চোখে মেয়েলী সমস্যা।
১৫. ফেরিওয়ালা (১৯৫৩)- ১৩টি : ফেরিওয়ালা, সখি, সংঘাত, সতী, লেভেল ক্রসিং, ধাত, ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই, চুরি-চামারি, দায়িক, মহাকর্কট বটিকা, আর না কান্না, মরব না সস্তায়, একবাড়িতে।
১৬. লাজুকলতা(১৯৫৪)- ১৬টি : লাজুকলতা, উপদলীয়, এদিক ওদিক, এপিঠ ওপিঠ, পাশ ফেল, কলহান্তরিত, গুণ্ডা, বাহিরে ঘরে, চিকিৎসা, মীমাংসা, নিরুদ্দেশ, সুবালা, স্বাধীনতা, আপদ,
পাষ-, অসহযোগী।
ছকে প্রদত্ত ১৬টি গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো ছাড়াও বেশ কিছু গল্পের সন্ধান মেলে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫০), স্বনির্বাচিত গল্প (১৯৫৬), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহ (১৯৫৭), উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ (১৯৬৩)- এই চারটি গল্প সংকলনে বিভিন্ন গল্পগ্রন্থের গল্প ছাড়াও কিছু নতুন সংযোজন ঘটেছে। গল্পগুলো হল- বিচার, কে বাঁচায় কে বাঁচে, প্রাকশারদীয়া কাহিনী, বড়দিন, শান্তিলতার কথা, সশস্ত্র প্রহরী, মাছের ল্যাজ ও মাংসের ঝাঁজ, সবার আগে চাই, জল মাটি দুধ ভাত, খাটাল, গলায় দড়ি কেন, কালো বাজারে প্রেমের দর, ঢেউ, হাসপাতালে, দুর্ঘটনা, মানুষ কেন হতবাক, একটি বখাটে ছেলের কাহিনী, উপায়, কোনদিকে। তাছাড়াও যুগান্তর চক্রবর্তী তাঁর সম্পাদিত অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (২য় সং ১৯৯০) গ্রন্থে মানিকের অগ্রন্থিত গল্পের যে তালিকা দিয়েছেন তা হল-স্নায়ু, মানুষ কেন কাঁদে, চোখ, কলহের জের, সঞ্চয়াভিলাষীর অভিযান, অকর্মণ্য, প্রতিক্রিয়া, গৃহিনী, পুত্রার্থ, অপর্ণার ভুল, ঘটক, সন্ধ্যা ও তারা, খুনী, জোতদার, ব্যথার পূজা, সাধারণ প্রেম, জয়দ্রথ, শীত, চৈতালী আশা, প্রেমিক, সমানুভূতি, বাজার, রাস্তায়, দলপতি, পশুর বিদ্রোহ, বাঘের বংশরক্ষা, দুটি যাত্রী, বন্ধু, অন্ন, ভীরু, শারদীয়া, ভোঁতা হৃদয়, গেঁয়ো, রূপান্তর, গেঁয়ো (২নং), বিয়ে, শিল্পী, মায়া নয়-দায়, স্টুডিও, বিচিত্র, ছোট একটি গল্প, রত্নাকর, অগ্নিশুদ্ধি, বিষ, গল্প, রোমাঞ্চকর, ঘাসে কত পুষ্টি, মতিগতি, চিন্তাজ্বর, তারপর, বিদ্রোহী, চাওয়ার শেষ নেই, মেজাজের গল্প, পালাই! পালাই!, সংক্রান্তি, ডুবুরী, জীবনের সমারোহ, রফা ও দফার কাহিনী, চাপা আগুন। এছাড়াও কিছু গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে, যা সংগ্রহ হয়নি এখনও। এখন-পর্যন্ত-প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মোটামুটি হিসাবে বলা যায়, কম-বেশি শ-তিনেক ছোটগল্পের স্রষ্টা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ( সৈয়দ, পৃ ১৬)
বন্ধুদের আড্ডায় স্রেফ বাজি জেতার জন্যে খেপা মন নিয়ে লেখা গল্প ‘অতসীমামী’ই হয়ে গেল বাংলা কথাসাহিত্যের প্রাঙ্গণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যয়ের প্রবেশের ছাড়পত্র। এরপরের ইতিহাস বাংলা কথাশিল্পের জগতের এক রাজপুরুষের ভাঙাÑগড়া-উত্থান-পতন-বিকাশ-বিবর্তনের ইতিহাস। প্রচলিত গল্পের ঘরানার বাইরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ আবিষ্কার করে সেই পথে নিরন্তর হেঁটে গেছেন প্রান্তের স্বর্ণপ্রান্তরে, যেখানে মানিককে ছুঁতে পারে এমন কোন উদ্যমী পথিকের খোঁজ মেলে না শত বছরেও। ‘অতসীমামী’র ভাষার বুনন ও চিন্তার ঋজুতা দেখে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না যে, স্রেফ বাজি জেতার জন্যই মানিকের এই পথে আসা, বরং ভিতরে তার প্রস্তুতি ছিল ষোল আনাই। রোমান্টিক মেজাজের প্রথম গল্পটির আইডিয়া যদিও উত্তরকালে মানিকের কী গল্প কী উপন্যাস কোন কিছুতেই আমরা পাই না, তারপরেও গল্পটির সম্মোহন আজও অনস্বীকার্য। অনেকের ভাষ্য মতে, গল্পটিতে শরৎচন্দ্রের প্রভাব আছে। এই ভাষ্য অবশ্য খুব বেশি সমর্থন করা যায় না। বংশীবাদক যতীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব খুঁড়ে বিশশতকের জীবনযন্ত্রণার যে রক্ত বেরিয়েছে, সেই রকম রক্ত শরৎচন্দ্রের কোথায় আছে? বিস্ময়কর নাটকীয়তা গল্পটির পাঠক মনোযোগের অন্যতম কারণ।
যদিও গল্পটি মানিক সাহিত্যের মূল স্রোতে পড়ে না, তারপরও গল্পটির প্রতি মানিকের আলাদা শ্রদ্ধার বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। যতীনমামা ও অতসীমামী মানিকের বাস্তব অভিজ্ঞতায় ছিল। বিশেষত মানিক নিজেই বলেছেন, ‘অতি জানা অতি চেনা মানুষকেই তাই করেছিলাম ‘অতসীমামী’র নায়ক-নায়িকা। সত্যই চমৎকার বাঁশী বাজাতেন চেনা মানুষটি, বেশী বাজালে মঝে মাঝে সত্যই তাঁর গলা দিয়ে রক্ত পড়তো এবং সত্যই তিনি ছিলেন আত্মভোলা খেয়ালী প্রকৃতির মানুষ। ভদ্রলোকের বাঁশী বাজানো সত্যই অপছন্দ করতেন তাঁর স্ত্রী। (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ২/৪০২)
বিশশতকের মধ্যবিত্তের জীবন বাস্তবতার করুণ জীবনালেখ্য মানিকের ‘অতসীমামী’ গল্পটি। লেখকের ধারণা ভুল ছিল, বংশীবাদক যতীন্দ্রনাথ কেষ্টুবিষ্টু গোছের লোক ছিলেন না এবং থাকারও কথা ছিল না। পুঁজিবাদের তুমুল উত্থানের সময়ে ঠুনকো বংশীবাদক নিতান্তই উপযোগিতাহীন পুরাতন শার্ট-প্যান্টের মতোই। লেখক বাড়িতে ঢুকে যা দেখলেন, তাঁর ধারণার পুরো বিপরীত। ঘরে তক্তপোষ, টেবিল-চেয়ার কিছুই নেই। একটি রংচটা ট্রাংক, কাঠের বাক্স, দড়িতে টাঙানো একটি মাত্র ধুতি এবং পেরেকে লটকানো একটা আধময়লা পাঞ্জাবিই যতীনমামার মোটের উপর সম্পদ। বার্ষিক পাঁচশো টাকা আয়ের জমির মালিক যতীন্দ্রনাথের সীমাহীন দরিদ্রতার মাঝেও মধ্যবিত্তসুলভ আত্মসম্মানবোধ ছিল সজীব ও সক্রিয়। তাই অন্যের দান গ্রহণে তাঁর এত কুণ্ঠা। ভাগ্নেকে জলখাবার দিয়ে যতীনমামা যে নির্মম অভিনয় করেছে, মধ্যবিত্তের টানাপোড়নের সংসারে এমন অভিনয় চলে হরহামেশাই।
প্রথম রসগোল্লাটা গিলেই মামা বললেন, ওয়াক্! রইল পড়ে খেয়ো তুমি, নয়তো ফেলে দিও। দেখি সন্দেশটা কেমন!
সন্দেশ মুখে দিয়ে বললেন, এ জিনিষটা ভালো, এটা খাব। বলে সন্দেশ দুটো তুলে নিয়ে রেকাবিটা ঠেলে দিয়ে বললেন, যাও তোমার সুজির ঢিপি ফেলে দিও খন নর্দমায়।
অতসীমামীর চোখ ছলছল করে এল! মামার ছলটুকু আমাদের কারুর কাছেই গোপন রইল না। (অতসীমামী)
যতীন্দ্রনাথ বাঁশি বাজাতেন মনে-প্রাণে, জীবন উৎসর্গ করে। সুরের ইন্দ্রজাল বিস্তার করতেন বুকের তাজা রক্ত দিয়ে। তাতেই পেতেন আনন্দ। অতসীমামী টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হলে, বেঁচে থাকার আশ্রয় বাঁশি ও বাড়ি দুটিই বিক্রি করে যতীন্দ্রনাথকে পড়তে হয় কঠিন অস্তিত্বের সংকটে। ফিরে আসেন গ্রামে। কিন্তু আর বেশি দিন বাঁচেননি। শেষ তিনবছর বাঁশিটার জন্য ছটফট করে কাটিয়ে গেছেন।যতীন্দ্রনাথ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে বিশশতকের শেকড়বিচ্ছিন্ন যন্ত্রণাকাতর মধ্যবিত্ত মানুষদের মনোবেদনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন মানিক। তিরিশের দশকের লেখা এই গল্পের নায়কের যন্ত্রণাকাতর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে মানিক মধ্যবিত্তের মর্মান্তিক জীবনবেদ নির্মাণের ইঙ্গিত দিলেন।
প্রাগৈতিহাসিক জীবন সংগ্রামের নিষ্ঠুর সত্যই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘প্রাগৈতিহাসিক’ গল্পের ভিত্তি। পরিশীলিত, পরিমার্জিত, সভ্য মানুষদের ভেতরে আদিম জীবনাচরণের প্রধানতম দিক-হিংস্রতা, শক্তিমত্ততা, নীতিবিবর্জিত যৌনতা আজও স্বরূপে সক্রিয়। গল্পের নায়ক বলিষ্ঠ প্রত্যয়ী ভিখু-ই সত্য জীবনধর্মী। তার উদ্ধত ঘোষণা মরিবে না। সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশুরা যে অবস্থায় বাঁচে না সে অবস্থায় মানুষ সে বাঁচিবেই। সংগ্রামী জীবনের সামনে বিরাট মহিমা নিয়ে উপস্থিত হয়। তাই পাঁচীকে পাবার জন্য ভিখুর হিংস্র-অনৈতিক প্রতিযোগিতায় নিরঙ্কুশ সমর্থন আধুনিক মানুষদের। ভাগ্যবিড়ম্বিত বিদ্রোহি ভিখুর বিন্নু মাঝির সুখের ঘর পোড়ানোর মতো হিংসাত্মক ভাবনা, বিশশতকের মধ্যবিত্ত সমাজকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। পৃথিবীর যত খাদ্য ও নারীর একা দখলদারিত্ব চায় ভিখু! সে আত্মপ্রতিষ্ঠা চায়। বশিরকে নির্মমভাবে হত্যা করে পাঁচীকে অধিকারে তাই এত অনন্দ। ভিখুর এ বিজয়ের আনন্দ ভিখুর একার না। বিশশতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশকের অধিকারবঞ্চিত, বিবেকধর্ষিত যন্ত্রণাকাতর মানুষদেরও আনন্দ। সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যপীড়িত, ফ্রয়েডীয় লিবিডো চেতনার বিজ্ঞান সত্যের ভিখু বিশশতকের বাস্তবতার প্রতিভূ।
মধ্যবিত্ত জীবনের দেউলিয়াত্ব, অন্তঃসারশূন্যতা, লোভাতুর দৃষ্টিভঙ্গি ‘প্রকৃতি’ গল্পের অমৃতের চোখে ধরা পড়ে তখনই যখন দশ বছর পর মধ্যবিত্তের খাতায় নাম লেখাতে আসে। অমৃতের বরাবরই অভিজাত সমাজের প্রতি ছিল তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ। সে আশ্রয় নেয় এক সময়ের সাহায্যকারী উকিল প্রমথনাথ বাবুর বাড়িতেই। পূর্বধারণা মতো এই মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে জীবনের সৌন্দর্য খুঁজে পায় না আর। এক সময়ের আশ্রয়দানকারীর বাড়ির কর্তার এমন কুণ্ঠিতভাবে বিমূঢ় অনুগ্রহ প্রার্থনা, বাড়ির কর্ত্রীর দারিদ্র্য প্রকাশের প্রচেষ্টা, বিবাহিত মেয়ের এমন বেহায়াপনা অমৃতের মনকে মধ্যবিত্তের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। কিন্তু অমৃতের জন্য সবচেয়ে বেদনাদায়ক সত্য হচ্ছে, তার আর নিম্নবিত্তের জীবনে ফিরে যাবার পথ নেই। মানুষের এই রকম প্রকৃতি-এই যুক্তিতে মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিনিধি রাখাল হালদারের হাতে হাত মিলিয়ে সীমাহীন অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটায় অমৃত। সেই সাথে মধ্যবিত্তের চৌহদ্দিতে নিজের প্রবেশাধিকারও নিশ্চিত করে।
বিশশতকের মধ্যবিত্ত জীবনের স্বার্থের সংঘাত, কৃত্রিমতা ও সংকীর্ণতা দেখা যায় ‘অন্ধ’ গল্পটিতেও। অলংকারের শোকে স্ত্রীর সংসার ত্যাগ এবং মৃত্যজনিত শোককাতর সনাতনের আত্মপীড়ন, সেই সাথে কন্যার স্বার্থতাড়িত ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে মধ্যবিত্তের প্রকৃত বাস্তবতা। বাস্তবিকপক্ষে, সংসারের প্রত্যেকেই যে যার স্বার্থের জন্য অন্ধ এবং অন্ধেরই আধিপত্য চলছে। ফলে, সনাতনের মতো একজন বিবেকশাসিত মানুষকে অন্ধ হিসেবেই বেঁচে থাকতে হয়েছে। আর ‘চাকরী’ গল্পের দুই বন্ধু মহেন্দ্রজীৎ ও জয়গোপালের অসুস্থ প্রতিযোগিতাই প্রমাণ করে যে, মধ্যবিত্তের স্বার্থের দ্বন্দ্ব কতটা ভয়ানক, অমানবিক। মিথ্যা খুনের আসামি ‘ফাঁসি’ গল্পের গণপতির ফাঁসি-ই যখন কাম্য হয়ে ওঠে নিজের পরিবারের, এমন কি স্ত্রী রমার কাছেও, তখনই আমাদের ভাবতে হয়, মধ্যবিত্তের জীবন আলেখ্যকে আর কতটা সর্বনাশের প্রান্তে নামাবেন মানিক? গণপতির বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ এবং নিম্নআদালতে ফাঁসির আদেশ স্ত্রী রমা মেনে নিলেও, উচ্চআদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে গণপতির প্রত্যাবর্তনকে মেনে নিতে পারে না। বাধা আসে ভেতর-বাহির উভয় দিক হতেই। একজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক হঠাৎ খুনের মতো ঘৃণ্য অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে, সমাজ কি খুব সহজে ছাড়বে? প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ প্রতি মুহূর্তে বিষাক্ত নিন্দার, কলঙ্কের ছোবল মারবে গণপতি ও তার পরিবারকে, যার প্রমাণ শুনানিকালে আদালতে উৎসাহী জনতার হিড়িক, পাঠক খাবে তাই পত্রিকায় মামলার বিস্তৃত বর্ণনা। এরিমধ্যে নির্যাতনের শিকার হয় সদ্যবিবাহিতা ছোটবোন। মূলত উচ্চতর আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে গণপতি বাড়ি ফিরলেই সৃষ্টি হয় নতুন এক সংকট। যে সংকটের আঁচ প্রথমেই পেয়েছে গণপতি।
গণপতিকে পুলিশে ধরিবার কিছুদিন আগে মহাসমারোহে তার ছোটবোন রেণুর বিবাহ হইয়াছিল। গণপতি এক সময় রেণুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে সকলের এমনি চকিতভাব দেখা গেল। এ ওর মুখের দিকে চাহিল-কিন্তু বয়স্ক কেহ জবাব দিল না। শুধু পশুপতির সাত বছরের মেয়ে মায়া বলিল, পিসিমাকে শ্বশুরবাড়িতে রোজ মারে, কাকা।
গণপতি অবাক হইয়া বলিল, মারে?
মায়া বলিল, তুমি মানুষ মেরেছ কিনা তাই।
তিন চারজন একসঙ্গে ধমক দিতে মায়া চুপ করিয়া গেল। মনে হইল ধমকটা যেন গণপতিকে দেওয়া হইছে। কারণ মায়ার চেয়েও তার মুখখানা শুকাইয়া গেল বেশী। (ফাঁসি)
বাস্তব হচ্ছে, গণপতির ফাঁসি হলেই বরং পরিবারটি মুখগুঁজে টিকতে পারত, মোটামুটি বৈধব্যের পোশাকে বেঁচে থাকতে পারত রমাও। এ নিষ্ঠুর সত্য বুঝেই রমা গণপতিকে অনুরোধ করেছে পরিচিত লোকালয় ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে। যেখানে কেউ চেনে না, কেউ জানে না। একাধিকবার অনুরোধ করেও গণপতির মত পরিবর্তন করাতে ব্যর্থ হয় রমা। ফলে আত্মসচেতন রমার বেঁচে থাকার আর কোন পথ থাকে না। উত্তরণের একমাত্র পথ খোলা ছিল আত্মহত্যা এবং তাই রমা করেছে। গণপতির যদি ফাঁসি হত কিংবা আমৃত্যু কারাগারে থাকত, তাহলেও শত কলঙ্ক-নিগৃহের দায় নিয়ে রমা বেঁচে থাকতে পারত। কিন্তু মুক্ত গণপতির ঘৃণ্য অপবাদের জীবন, রমার মতো ব্যক্তিত্ববান নারীর পক্ষে, বিশেষত স্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়ে বেঁচে থাকা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। তাই রমার এই আত্মহত্যা।
আবদুল মান্নান সৈয়দের মতে, ‘বৌ’ গল্পগ্রন্থটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র সাহিত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। একশো বছরের বাংলা সাহিত্যেরও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। (সৈয়দ, ১৮ ভূমিকা) দোকানির বৌ, কেরানীর বৌ, সাহিত্যিকের বৌ, পূঁজারীর বৌ, প্রৌঢ়ের বৌ, অন্ধের বৌ, সর্ববিদ্যাবিশারদের বৌ প্রত্যেকেই আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের দেখা-জানা নারীর প্রতিমূর্তি। বিচিত্র এসব নারীর মানসিকতাও আশ্চর্যরকমের স্বতন্ত্র। তাদের সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়ার প্রত্যাশাও বিচিত্র। দোকানি শম্ভুর বৌ সরলা, কেরানি রাসবিহারীর বৌ সরসী স্বামীর সোহাগে গরবিনী নারী। অন্যদিকে অমলা তার সাহিত্যিক স্বামী সূর্যকান্তের মধ্যে তার কাঙ্ক্ষিত চরিত্র খুঁজে পায় না, এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির বিরাট ফারাক ধরতে পেরে সে আশাহত। সূর্যকান্ত একটু বেশি বাস্তববাদী। অমলার বিশাল প্রত্যাশা রূপান্তর ঘটে নৈরাশ্যে। স্বামীর অবহেলায় নির্মম আত্মপীড়নে হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত অমলার করুণ পরিণতি মধ্যবিত্ত সংসারে পুরুষের আচরণের নগ্নরূপ। বিপত্নীক রমেশের বৌ প্রতিমাও অমলার মতোই স্বামীর সংসারে পূর্বপরিকল্পিত আবেগ-অনুভূতির মিল না পেয়ে এক ধরনের মানসিক অস্বস্তিতে ভোগে। কুষ্ঠরোগীর বৌ মহাশ্বেতা সর্বাধিক বেদনাদায়ক বাস্তবতার শিকার। পিতা অবৈধ অর্থ উপার্জন করেছে, তারই পাপে সন্তান যতীন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। কত ভয়াবহ সেই প্রায়শ্চিত্ত তা কল্পনারও অতীত। সমাজ-পরিবার-পরিজন সর্বত্র যতীন অশুচি, অস্পৃশ্য। লোভ-লুটপাট-শোষণ-নিপীড়ন ও অন্যায় পথে উপার্জিত অর্থের বিনিময়ে একশ্রেণির নষ্টচিন্তার মানুষ সুখ ক্রয় করে, বিপরীতে চলে রিক্ত ও বঞ্চিতদের তুমুল আর্তচিৎকার। কিন্তু পাপের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে এক সময়, নিজের পাপ পুরুষানুক্রমে নিজের উত্তরসূরীর রক্তে প্রবাহিত হয়ে সৃষ্টি হয় দূরারোগ্য ব্যাধি-ইতিহাসের এই এক নিষ্ঠুর প্রতিশোধ!
মানুষের লোভ, লালসা এবং অর্থগূধ্লুতা সমাজ বিবর্তনে যে অসম অবস্থার সৃষ্টি করে তারই ফলে একদিকে পূঞ্জীভূত পাপ ও ব্যভিচার। অন্যদিকে রিক্ত ও বঞ্চিতের আর্তনাদ। এদের নিষ্পাপ অভিশাপ অন্যদের পাপের ফলে পুরুষানুক্রমে বংশের রক্তধারার সঙ্গে মিশে দেখা দেয় দূরারোগ্যব্যাধি। যতীনের বাবা বহুমানুষের সর্বনাশ করেই প্রচুর বিত্ত অর্জন করেছিলেন। অবশ্য ধন লাভের এটাই বিধি। ( মিত্র, ১৭২)
বাস্তবে যতীনের কোন অপরাধ নেই, লুটপাট ও মানুষের সর্বনাশ করে বিরাট প্রাচুর্যের পাহাড় জমিয়েছে তার বাবা। ক্রমাগত শরীরের সর্বত্র পচন ছড়িয়ে পড়লে যতীন মানসিকভাবেও বিকল হয়ে পড়ে। এর সাথে রহস্যজনকভাবে স্ত্রী মহাশ্বেতার একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলার প্রবণতায় যতীনের সুস্থচিন্তার সব পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। মূলত, মানুষের স্তরে আর নেই যতীন। মানুষের ভালবাসা পাবার প্রত্যাশাও তার ফুরিয়েছে। মহাশ্বেতাকে সন্দেহ, নিজের রোগ মহাশ্বেতার শরীরে ছড়িয়ে দেবার হিংসাত্মক প্রচেষ্টা, যতীনের বিকারগ্রস্ত মানসিকতারই চূড়ান্ত প্রতিফলন ফলন ।
হাসি তো পাবেই। হাসি নিয়েই যে মেতে আছ। একদিকে স্বামী মরছে, ওদিকে আর একজনের সঙ্গে হাসির র্হরা চলছে। আমি কিছু বুঝি না ভেবেছ!
মহাশ্বেতা বলে-কার সঙ্গে র্হরা চলছে?
তাই যদি জানব তুমি এখনো এ বাড়িতে আছ কি করে? যতীন পচন ধরা নাক দিয়া সশব্দে নিশ্বাস গ্রহণ করে, গলিত আঙ্গুলগুলি মহাশ্বেতার চোখের সামনে মেলিয়া আর্তনাদের মত বলতে থাকে, ভেবো না, ভেবো না, তোমারও হবে। আমার চেয়ে আরো ভয়ানক হবে! এত পাপ কারো সয় না!
হিংস্র ক্রোধের বশে যতীন আঙ্গুলের ক্ষতগুলি মহাশ্বেতার হাতে জোরেজোরে ঘষিয়া দেয়। আগুন দিয়া আগুন ধরানোর মত সংক্রামক ব্যধিটাকে সে যেন মহাশ্বেতার দেহে চালান করিয়া দিয়াছে এমনি এক উগ্র আনন্দে অভিভূত হইয়া বলিল: ধরল বলে, তোমাকেও ধরল বলে! আমাকে ঘৃণা করার শাস্তি তোমার জুটল বলে, আর দেরি নাই। (কুষ্ঠরোগীর বৌ)
বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে, মহাশ্বেতা কুষ্ঠরোগীদের আশ্রম খুলেছে বাড়িতে! তাদের সেবা করেই বাকি জীবন অতিক্রমের ব্রতও তার। কিন্তু যতীন যখন কেঁদে উঠে বলে, মহাশ্বেতা শুধু ওদের সেবা করছে, তার দিকে তাকিয়েও দেখছে না। তখন মহাশ্বেতা নিশ্চুপ থাকে। প্রকৃতপক্ষে, যতীনের স্ত্রী হিসেবে মহাশ্বেতা নিজের মধ্যে কোন জায়গা অবশিষ্ট রাখেনি।কুষ্ঠরোগীর বৌ হিসেবে কুষ্ঠরোগীকে সেবার ব্রত নিয়ে জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করার জন্য বাড়িতে কুষ্ঠরোগীদের আশ্রম খুলেছে।
‘বৌ’ গল্পগ্রন্থের প্রত্যেক বৌ-ই আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছে নিজ নিজ অবস্থান হতে। ভেতরে-বাইরে নানাবিধ জটিল সংঘাতের মুখোমুখি বৌরা নিজের আত্মমর্যাদা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ম্লান হতে দেয়নি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রীতিনীতি দ্বারা। প্রতিটি নারী নিজেকে বিজয়ী দেখতে চেয়েছে। নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনের বিচিত্র বেদনা-মধুর অনুভূতির চমৎকার মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লে¬ষণ করেছেন মানিক।
দারিদ্র্যপীড়িত ছিন্নমূল মানুষের টিকে থাকার স্বার্থ এবং মধ্যবিত্তের জৈবিক স্বার্থযোগে একটি বীভৎস নাগরিক জীবনচিত্র ‘সিঁড়ি’ গল্পে। ভাড়াটিয়ার আর্থিক দুর্বলতার পরিপূরক হিসেবে থাকে যুবতী কন্যা বা যুবতী স্ত্রী। বাড়িওয়ালা মানব তার ভাড়াটিয়ার কন্যা পঙ্গু ইতির দেহভোগের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে নেয়। অন্যদিকে বিনা ভাড়ায় বসবাসের সুযোগ, ভদ্রতার আবরণে কাঁচা পয়সা পাবার লোভ, এসব কারণে ইতি স্বেচ্ছাপ্রণোধিত হয়েই দেহদানে এগিয়ে যায়। এর মাধ্যমে ইতির পরিবারের কষ্টও লাঘব হয় কিছু পরিমাণে।
মা বাবা ভাইবোনদের কথা ভেবে ও কথা বলেছি, কি কষ্টে আছে সবাই বলো তো? নইলে, আমি তো রাজরাণী। অবশ্যি, দেখতে শুনতে রাজরাণী নই। তোমার জন্যে রাজরাণী।
তেতলায় মানুষ আছে , দুতলায় মানুষ আছে, সিঁড়িতে আর কেউ নেই। তবু ইতি জোর করে গলা একেবারে খাদে নামিয়ে দিয়ে বলে, তুমি আমার রাজা। (সিঁড়ি)
ইতির নারীরতের সর্বশেষ পূঁজি বিনিয়োগের মধ্যমে টিকে থাকার সংগ্রাম বিশশতকের নাগরিক জীবনের কদর্য সত্য। ইতির মধ্যে অপরাধজনিত অন্তর্দাহের চিহ্ন দেখা গেলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি মানব অতি স্বাভাবিক। যেন ইতির দেহ তারই প্রাপ্য। মানবিক মূল্যবোধের চর্চা অল্পবিস্তর নিচুতলার মানুষদের মধ্যে থাকলেও মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত মানুষের মধ্যে তার লেশমাত্র ছিল না। আদিম জৈবচেতনার মতো অর্থনীতিও অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ অনুষঙ্গ আধুনিক মানুষের জীবনে। চূড়ান্ত বিচারে অর্থনীতি-ই মানুষের প্রেম, বিশ্বাস, বন্ধন, মূল্যবোধ ইত্যাদির চালিকাশক্তি। ‘সরীসৃপ’ গল্পে ‘প্রাগৈতিহাসিক’ গল্পের ভিখুর মতোই চারু, পরী, বনমালীর জীবনযাপনে বিকারগ্রস্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। একই পুরুষকে ঘিরে দুই সহোদর বোনের সরীসৃপলীলা এ গল্পের মূল বিষয়। ধনীর এক পাগল ছেলের সাথে বিয়ে হয় সতের বছরের সুন্দরী তরুণী চারুর। বনমালীর বয়স তখন পনের। চারু বাগানে পায়চারিকালে পাহারাদারের দায়িত্ব পড়ে মোসাহেব পুত্র বনমালীর উপর। ছলে-কৌশলে রূপের খেলায় চারু বনমালীকে প্রলুব্ধ করে, ভগবান সুবুদ্ধি দিয়েছিলেন তাই বাগানবাড়ি তোমার কাছে বাঁধা রাখার কথা মনে হয়েছিল, আমার সর্বস্ব গেছে যাক কি আর করব;-সবই মানুষের কপাল। মাথাগুঁজবার ঠাঁইটুকু যে রইল, এই আমার ঢের। স্বামী পাগল, প্রেমিক বনমালী-ই চারুর আশ্রয়। আশ্রয় পেল বটে, কিন্তু তখন সে এক সন্তানসহ বিধবা। কিশোর বনমালী একদিন ছিল চারুর খেলার পাত্র। প্রতি মুহূর্তে জব্দ করে চারু উপভোগ করেছে নারীত্বের স্বাদ ও আনন্দ। নিয়তির কী খেলা! সেই চারু আজ বনমালীর অনুগ্রহ প্রার্থী। চারুকে নিয়ে রীতিমত কৃষ্ণলীলায় মেতে উঠেছে বনমালী। ভাগ্যের ফেরে চারু বনমালীর জালে বন্দি, যে কোন মুহূর্তে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে পারে। তাই বনমালীর মন দখলে চারু অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নামে নিজের সদ্যবিধবা বোন পরীর সাথে। মূলত পরীর এ বাড়িতে আগমন-ই চারুর জীবনের নতুন সংকট। চারুকে ডিঙ্গিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই পরী বনমালীকে দখলে নিয়ে নিল। ঝড়ের রাতে চারু আবিষ্কার করে, পরী-বনমালী এক ঘরে, এক বিছানায়। বনমালীর বুকে পরীর পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে চারুর ভেতরে তীব্র জ্বালা অনুভব করলেও ঘর হতে বের হয় নিঃশব্দেই।
পা হইতে মাথা অবধি চারুও একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করিল। এক চিৎকার করিয়া বিছানায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরীকে আঁচড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেওয়ার জন্য গলাটিপিয়া তাহাকে একেবারে মারিবার জন্য, সে এক অদম্য অস্থির প্রেরণা অনুভব করিতেছিল।
কিন্তু সংসারে সব কাজ করা যায় না। কাকে সে কি বলিবে ? এটা তার বোনের শয়ন ঘর কিন্তু ঘরে মালিক বনমালী। (সরীসৃপ)
শেষে নিজের বোনের হত্যার ষড়যন্ত্রের জালে নিজেরই প্রাণ হারাতে হল চারুকে। চারুর মৃত্যু বনমালীর মনোলোকে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়Ñ পরীর প্রতি উদাসীন, চারুর ছেলে ভুবনই তার সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্রে চলে আসে। পরীর রূপ আছে কিন্তু চারুর মতো বনমালীকে আটকানোর মন্ত্র জানা ছিল না। নির্বিকারচিত্তে বনমালী পরীকে নামিয়ে দিল ঝি-চাকরের পদমর্যাদায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী কত অসহায়! স্বার্থপর, মতলববাজ, কূটিল, আত্মসর্বস্ব, বিকৃতরুচির বনমালীকে ঘিরে চারু ও পরীর অসুস্থ প্রতিযোগিতাই তার প্রমাণ। জৈবিক তাড়নায় নয়, মূলত অর্থনৈতিক কারণেই চারু ও পরী বনমালীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। মানুষ কতটা নিচে নামতে পারে, সংসারের কূটিলতা, কদর্যতা ও পাষণ্ডতা কতটা ভয়ংকর হতে পারে এই তিনজন নর-নারী সেই প্রতিযোগিতা-ই করেছে।
মধ্যবিত্তের জীবনের বাহিরে ফিটফাট হলেও, ভেতরে থাকে নির্মম টানাপোড়ন। অর্থ-বিত্তের প্রাচুর্য নেই, আবার কৃত্রিম ভদ্রতারও অন্ত নেই। মিথ্যা আভিজাত্যবোধ, আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন জীবনের উচ্চ আকাক্সক্ষা, গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলে মধ্যবিত্তের দিনকাল। ক্ষেত্রবিশেষে শ্রমিকশ্রেণি তথা নিম্নবিত্তরা থাকে সুবিধাজনক অবস্থানে। ‘প্যাঁক’ গল্পে মানিক এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন দুই শ্রেণির দুইজন প্রতিনিধিকে পাশাপাশি রেখে। কেরানি অনাথবন্ধু এবং ট্যাক্সিড্রাইভার শিবচরণ একই বিল্ডিং এর উপরতলা-নিচতলার বাসিন্দা। অনাথবন্ধুর সংসার অভাব, অভিযোগ ও টানাপোড়নের। অন্যদিকে শিবচরণের পরিবারে সদস্য বেশি হলেও প্রাত্যহিক অর্থের সমাগম ঘটায় স্বচ্ছলভাবেই দিন চলে। মানিক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মধ্যবিত্তের বাস্তবতা-ই তুলে ধরেছেন। অনাথবন্ধুর টানাটানির সংসার কিন্তু আত্মসম্মানবোধ টন্টনে। ছেলে সুকান্তের মোটরড্রাইভিং শেখার আগ্রহে তার ইগোতে বাঁধে।Ñভদ্রলোকের ছেলে অর্থোপার্জন করিয়া মোটর হাকায়; মোটর হাকাইয়া অর্থোপার্জন করে না। কষ্ট করিয়া মোটর ড্রাইভিং শেখার কি দরকার, রিক্সা টানুক না সুকান্ত? একই কথা, তাতেও পয়সা আসিবে। অমন পয়সা রোজগারের মুখে আগুন।
চরম অর্থ সংকটেও অনাথবন্ধু তার ছেলের মোটর ড্রাইভিং শেখাকে যে সহজভাবে মেনে নিতে পারছেন না, এর নেপথ্যের কারণ হিসেবে বলা যায়, অনাথবন্ধুর ভিতরে জ্যান্ত হয়ে আছে বিশশতকের শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রবল ও সক্রিয় আত্মসম্মানবোধ। জীবনের কোন স্বাদই পূরণ হয় না এ শ্রেণির মানুষদের। এমনি ভাগ্যাহত এক চরিত্র ‘সমুদ্রের স্বাদ’ গল্পের নায়িকা নীলা। আপাতদৃষ্টিতে সমুদ্র দেখার মতো সামান্য বিষয় নিয়ে গল্পটি লেখা হলেও ভেতরের ব্যঞ্জনা তুচ্ছ নয়। নীলা জেনেছে, পৃথিবীর তিনভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। সেই অবধি সমুদ্র দেখার তীব্র আকাক্সক্ষা তার। পরিণত বয়স্কা হওয়ায় তীর্থযাত্রী পিতার সাথে যেতে পারেনি। তারপর জীবনযুদ্ধে এতটাই সক্রিয় থাকতে হয়েছে যে, আর সমুদ্র দেখা হয়নি। জসীম উদ্দীনের ‘কবর’ কবিতার বৃদ্ধ দাদুর মতো নীলাকে একে একে বাবা, মা, ভাই-এসব নিকটজনদের হারাতে হয়েছে। মামার বাড়িতে পীড়িত জীবন এবং শেষে আধ-পাগলের সাথে বিয়ে নীলার জীবননাট্যে ট্রাজিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নীলার সমুদ্র দর্শনের স্বপ্ন স্বামী-শাশুড়ির কাছে পরিহাসের বিষয়। সুযোগ পেলেই নীলা চুপিচুপি নিঃশব্দে কাঁদে। এ অধিকারও পায় না স্বাচ্ছন্দ্যে। নীলা ছিঁচকাঁদুনে, শাশুড়ির সাথে স্বামীও একমত। তাছাড়া লক্ষণ ভাল নয়, মাদুলি-তাবিজ পরিয়ে সমুদ্র দর্শনের ভূত তাড়ানোর পরামর্শ আসে প্রতিবেশির নিকট হতেও। মধ্যবিত্তের সাধ ও সাধ্যের সংঘাতে স্বপ্নাতুর নীলার রক্তাক্ত আবেগ-অনুভূতির সমাপ্তি ঘটে অশ্রুজলেই। স্বামী-সংসারের সব অসঙ্গতি, অন্যায়কে নীলার মেনে নিতে হয় নীরবে, নিঃশব্দে। কিছু বলিবার নাই, কিছু করিবার নাই, মুখ বুজিয়া সব মানিয়া লইতে হইল নীলার। গল্পের শেষে বর্ণিত নীলার পরিণতি মধ্যবিত্ত সংসারের নারীর চিরন্তন নিয়তি।
বাহিরে গিয়া অনাদি দেখতে পায়, দরজার কাছে বারান্দায় দেয়াল ঘেঁষিয়া বসিয়া নীলা বাটিতে তরকারি কুটিতেছে। একটা আঙুল কাটিয়া গিয়া টপ্ টপ্ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতেছে আর চোখ দিয়া গাল বাহিয়া পড়িতেছে জল। মাঝে মাঝে জিভ দিয়া নীলা জিভের আয়ত্তের মধ্যে যেটুকু চোখের জল আসিয়া পড়িতেছে সেটুকু চাটিয়া ফেলিতেছে। (সমুদ্রের স্বাদ)
অভাবের তাড়নায় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত একজন যুবক কী পরিমাণ মানসিক বিকারগ্রস্ত হতে পারে ‘ভিক্ষুক’ গল্পের যাদব-ই প্রমাণ করে দিয়েছে। বহু কষ্টার্জিত চাকরি ছেড়ে অবলীলায় ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছে। এ পেশায় অল্প পরিশ্রমে অধিক আয়। হাড়ভাঙা খাটুনির পরও যখন সংসারে স্বচ্ছলতা এল না, তখন শিক্ষিত যুবক আত্মসম্মানবোধ এবং শ্রেণিমর্যাদা দূরে ঠেলে বেঁচে থাকার লড়াই হিসেবে গ্রহণ করে এ হীন পেশা। ‘বিবেক’ গল্পের শিক্ষিত ঘনশ্যাম শয্যাশায়ী স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ধনী বন্ধুর টেকিল থেকে স্বর্ণের ঘড়ি ও তারই মতো পরিস্থিতির ফাঁদে পড়া উপকারী বন্ধু শ্রীনিবাসের মরণাপন্ন সন্তানের চিকিৎসার জন্যে স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রির টাকা চুরির মতো বিবেকবর্জিত কাজ করেছে। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস, স্ত্রী চিৎকার জন্যে চুরি নিরর্থক হয়ে যায়, কারণ ডাক্তার জবাব দিয়েছে, স্ত্রী মণিমালাকে বাঁচানো ক্ষমতা তার হাতে নেই, ভগবানে হাতে চলে গিয়েছে। ধনী বন্ধুর ঘড়ি কৌশলে পূর্ববৎ স্থানে ফেরৎ দিয়ে আসলেও বন্ধু শ্রীনিবাসের টাকা ফেরত দেয়নি।
‘আপিম’ গল্পে আছে মধ্যবিত্ত পরিবারের মোহগ্রস্ত মানুষদের আসল রূপ। সহানুভূতির অভাবে নয়, অভাব শুধু সামর্থ্যের। আপিমখোর হরেন নেশাগ্রস্ত হয়ে একা স্বপ্ন দেখে না, সংসারের সবাই বিকারগ্রস্ত মানসিকতার। বিপত্নীক হরেন, ছোটভাই নরেন, স্ত্রী মায়া, ছেলে বিমল, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে অচেনা। এমন কি সংসারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হরেনের পনের বছরের মেয়ে অমলাকে মায়া বুঝতে পারে না। পরিবারের একমাত্র আপিমখোর হরেন। স্ত্রীমৃত্যুজনিত আত্মপীড়নের হাত হতে বাঁচতে সে আপিম খায়। সংসারের অন্য সদস্যদের তুলনায় হরেন বেশি সংবেদনশীল, অনেকাংশে মানবিকও। বস্তুতপক্ষে, পুরো মধ্যবিত্ত সমাজটাই আকুণ্ঠ নেশায় মজে আছে, সমাজের বাসিন্দারা সকলেই বিকারগ্রস্ত, যে কারণে হরেনের মতো মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন এক মানুষকেও দাঁড়াতে হয় সর্বনাশের চূড়ায়।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষে চলেছিল ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা। এরই প্রত্যক্ষ প্রভাবে সৃষ্টি হয় ১৯৪৩ (১৩৫০বং) খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর। এ দুর্ভিক্ষ নগদ কেড়ে নিয়েছিল প্রায় ত্রিশ লাখ মানুষের জ্যান্ত প্রাণ। অধ্যাপক ক্ষিতিশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত বেসরকারি কমিশনের মতে, মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩৫ লাখের উপরে। মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের সময় একশ্রেণির মুনাফাখোর, মজুতদার, চোরাকারবারি রাতারাতি আঙুল ফুলে কলা গাছ বনে যায়। গরিব আরো গরিব এবং বিপরীতে বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পদশালী হতে থাকে আরো সম্পদের মালিক। দুর্নীতি, ঘুষ, বলাৎকার ইত্যাদি অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জনের নোংরা প্রতিযোগিতা চলেছে হরদম। খাদ্যের অভাবের পাশাপাশি ছিল কৃত্রিম বস্ত্রসংকটও। সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তি ভেঙে পড়ায়, প্রচুর অর্থ জমিয়ে নিজের নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য মানুষগুলো বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল সেই সময়ে। ফলে দ্রব্যমূল্য চলে যায় মধ্যবিত্তের ক্রয়সীমার বাইরে। খাদ্যসংকট ভয়াবহ রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়। অনাহারি কঙ্কাল সর্বস্ব কৃষক-শ্রমিকের জ্যান্ত শরীর রাস্তা থেকে টেনে নিতে শেয়ালÑকুকুরের তেমন সমস্যা হচ্ছিল না। একদিকে নিরন্ন মানুষের মৃত্যুর সমারোহ, অন্যদিকে খাদ্যের প্রাচুর্যে উন্মাদ শেয়াল-কুকুরের উল্লাস-আনন্দ চিৎকারে বীভৎস এক জনপদে পরিণত হয়েছিল গ্রামবাংলা। বেঁচে থাকার উৎকট তাড়নায় নিম্নবিত্ত মানুষের সাথে মধ্যবিত্তরাও গেল শহরে। কিন্তু ভূমি শ্রমিকের শ্রমের মর্যাদা যান্ত্রিক শহরে নেই। ফলে মধ্যবিত্ত মানুষদের আশ্রয় জুটেছিল খোলা আকাশের নিচে ফুটপাতে কিংবা বস্তিতে, আর তাদের খাদ্য সংগ্রামের প্রতিপক্ষরা ছিল শহরের হিংস্র কুকুর। এবং খাদ্যস্থল ছিল ডাস্টবিন। খাদ্যের প্রয়োজনে শেষে মধ্যবিত্ত নারীরা সামাজিক-ধর্মীয় সম্ভ্রমবোধ ভুলে জীর্ণ-শীর্ণ দেহটাই বিকানোর প্রতিযোগিতায় নাম লেখায়। এদের প্রধান খরিদ্দার যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের বাজারে রাতারাতি পুঁজিপতি হয়ে উঠা একশ্রেণির লোলুপ পুরুষ। কন্যা বিক্রি ও দেহ ব্যবসার জমজমাট বাজার গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল কলকাতা শহরে।
যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীমনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। নিজে ঘুরে বেড়িয়েছেন গ্রামে গ্রামে। প্রত্যক্ষ করেছেন দুর্ভিক্ষের আসল রূপ। উৎসাহ দিয়েছেন পীড়িত মানুষদের উঠে দাঁড়াতে। প্রয়োজনে সরকারের তালাবদ্ধ খাদ্য গুদামগুলো লুট করে একদিনের জন্য হলেও খেয়ে বাঁচতে। দুর্ভিক্ষকালীন সময় ও উত্তরকালের গল্পগুলোতে মানিক মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যরে প্রতি চরম আস্থাশীল। দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের শিকার ছিন্নমূল বুভুক্ষু মানুষদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে লেখা হয়েছে প্রচুর, কিন্তু মানিকের চিন্তা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। বিশেষত, নিজে দুর্ভিক্ষের বাস্তব ছবি দেখে অনুধাবন করেছেন যে, নিরন্ন মানুষদের নিজেদেরই জেগে উঠতে হবে, প্রয়োজনে লুট করে হলেও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে। দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে সৃষ্ট চরিত্ররা মানিকের সক্রিয় ভালবাসা পেয়েছে। এইজন্য দেখা যায়, লুট করে নায়ক জেল খাটছে।
দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল ছোবলে ‘আজ কাল পরশুর গল্পে’র রামপদ ও স্ত্রী মুক্তার সাজানো গোছানো সুখের সংসার টেকে না। দুর্ভিক্ষের সময় সাত বছরের ছেলে এবং বউ মুক্তাকে রেখে রামপদ বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে জীবিকার সন্ধানে। স্বামীর অনুপস্থিতি এবং খাদ্যের অভাবে ছেলের মৃত্যুতে মুক্তার জীবনে নেমে আসে ভয়ানক অমানিশা। আর এই অসহায়ত্বের সুযোগে গ্রামের প্রতাপশালী ঘনশ্যাম মুক্তার দেহভোগের নেশায় প্রমত্ত হয়ে ওঠে। আত্মসম্ভ্রম বাঁচাতে মুক্তাকে গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি জমাতে হয়। কিন্তু সেখানেও মুক্তা তার অনিবার্য পরিণতিকে এড়াতে পারল না। যুদ্ধের বাজারে দেহ বিক্রি ছাড়া মুক্তার মতো গৃহস্থঘরের নারীদের আর কোন পুঁজি ছিল না। আরো করুণ বিষয়, গ্রামে ফেরার পথ বন্ধ করে দিল স্বার্থান্বেষী সমাজপতিরা। পতিতশ্রেণিদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেবার ব্রত গ্রহণকারী একদল মানবদরদি কর্মী মুক্তাকে গ্রামে ফিরিয়ে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সমাজগর্হিত জীবনাচারের মধ্যদিয়ে মুক্তা তার কুলমর্যাদা হারিয়েছে, ফলে সমাজ তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যেকারণে মুক্তার গৃহে প্রত্যাবর্তনের সংবাদে সমাজ জেগে ওঠে এবং সামাজিক শান্তির প্রশ্নে সোচ্চার কণ্ঠ সমাজপতি ঘনশ্যামের, যার দেহভোগের লালসা হতে বাঁচতেই মুক্তাকে গ্রাম ছাড়তে হয়েছিল।
দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত মানুষের বেঁচে থাকার পরিবর্তে মৃত্যুর সমারোহ চলেছিল সাড়ম্বরে। জীবনের প্রতি মায়া, বেঁচে থাকার ব্যাকুল প্রত্যাশা সব মানুষেরই ধর্ম। সামান্য খড়কুটো ধরে হলেও শেষ পর্যন্ত মানুষ বাঁচতে চায়। যেখানে জীবন-মৃত্যুর দরকষাকষি চলে প্রতি মুহূর্তে কিংবা শেয়াল-কুকুরের মতো জীবন, সেখানে নারীত্বের অহংকার, সম্ভ্রমের কী মর্যাদা? সমাজ-ধর্মের রীতিনীতি রক্ষার চাইতে পেটের দায়-ই যে বড় দায়। মানিক তাঁর গল্পে মুক্তা ও রামপদের সংসার গড়েছেন আবার। বনমালীর সোচ্চারকণ্ঠ, কিসের বিচার? কার বিচার? রামপদের বউ কোন দোষ করেনি, প্রমাণ করে, দুর্ভিক্ষের চক্রে পড়ে যাদের নৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে, তারা মূলত পরিস্থিতির শিকার। সমাজ-ধর্মের চোখ রাঙানিকে এড়িয়ে, মুক্তার অনিচ্ছাকৃত পাপকে বিচারের ঊর্ধেŸ এনে, স্বামীর সংসারে ফিরিয়ে দিয়ে, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত মানুষদের নতুনভাবে বাঁচার প্রত্যয় জাগিয়েছেন মানিক।
বিশশতকের চল্লিশের দশকের নব্যপুঁজিপতিরা পুঁজি সংগ্রহে এতটাই মরিয়া ছিল যে, নিজের বউকে বা প্রেমিকাকেও পণ্য হিসেবে বাজারে তুলতে দ্বিধাবোধ করত না। ‘যাকে ঘুষ দিতে হয়’ গল্পের নায়ক মাখন একশো টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে নাম লেখায় ঠিকাদারিতে। উদ্দেশ্য অবৈধ পথে বিপুল অর্থোপার্জন। পুঁজিপতি দাস সাহেবের সহযোগিতায় মাখন তিনবছরেই নব্যপুঁজিপতি। এর পিছনে রয়েছে স্ত্রী সুশীলার উচ্চাভিলাসী আকাঙ্ক্ষাও। পুঁজির নেশায় মাখন এতটাই বিবেকশূন্য, লাখ টাকার কনট্রাক্ট পাবার লোভে স্ত্রী সুশীলাকে দাস সাহেবের নির্জন ঘরে ব্যবহারের জন্য রেখে আসে। চাল, নুন তেল, কেরোসিনের মতোই ভোগ্যপণ্যের তালিকায় ছিল নারীও, হোক সে একজনের স্ত্রী বা প্রেমিকা। ‘কালোবাজারে প্রেমের দর’ গল্পের প্রেমিক ধনঞ্জয় ও তার প্রেমিকা লীলা নিজেদের প্রেম একপ্রকার বিকিয়ে দিয়েছে নিজেদের ওপরে উঠার সিঁড়ি খুঁজে পেতে। নব্যপুঁজিপতি কালোবাজারি নিরঞ্জনের সাহায্যে ধনঞ্জয় ওপরে ওঠার স্বপ্ন দেখে। প্রেমিকের স্বপ্ন বাস্তবায়নে লীলাও প্রেমের ঐন্দ্রিকজাল পাতে। গা বাঁচিয়ে প্রেমের অভিনয় করতে গিয়ে নিজেই আটকে পড়ে নিরঞ্জনের নজরে। যথারীতি আসে বিয়ের প্রস্তাব। পুঁজিপতি নিরঞ্জনের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের মতো শক্তি বা ইচ্ছা কোনটাই দেখি না লীলার মধ্যে। দুজনেরই বিনিদ্র রাত কাটে। একদিকে ধনঞ্জয়ের সামনে বিরাট অঙ্কের অর্থের হাতছানি, অন্যদিকে লীলার সামনে বিশাল সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভন। প্রেমের আবেগ-অনুভূতি, মহত্ব সবই মূল্যহীন, অন্তত বিশশতকের পুঁজিবাদী সমাজে। বিশেষ করে, যে সমাজের পুঁজিপতি হবার প্রধান ভিত্তিই হচ্ছে শোষণ, লুটপাট, কপটতা, শঠতা, ছলচাতুরি, সেই সমাজে সুশীলা-লীলারা এভাবেই বিক্রি হবে পণ্যের মতো। এমনটাই ছিল বাস্তবতা।
বিশশতকের মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনপ্রবাহের অবর্ণনীয় দৈন্যের চিত্র ‘টিচার’ গল্পটিতে। টিচাররাও যে মানুষ, এবং তাদের পরিবার-পরিজন আছে, আছে জীবন-জীবিকার প্রশ্ন, এসব কথা ভুলে থাকেন উঁচুতলার মানুষেরা। টিচার বললেই অভিজাত মানুষের সামনে ভেসে ওঠে অনাহারি, অর্ধ-আহারি, শীর্ণ পোশাক পরিহিত এক মহৎ মানুষের ছবি। শত অভাব-অভিযোগের মধ্যেও তিনি আদর্শের বুলি আওড়াবেন। চেঁচিয়ে ছাত্রদের পড়াবেন, সকল ধনের সেরা বিদ্যা মহাধন, আর এদিকে অভাবের চোটে অনাহারে পেটে আলসার হবে। বিশশতকের টিচাররা প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধের বেড়া ভেঙে অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। বেতন বৃদ্ধি, নিয়মিত বেতন পাবার দাবিতে জোটবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে নামে। রাজমাতা হাইস্কুলের সেক্রেটারি রায়বাহাদুর অবিনাশ তরফদার এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তব্য, স্কুলের শিক্ষকরা কি শ্রমিক, যে আন্দোলনে নামবে। তাই শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে নীতিমূলক বক্তৃতা করে বলেন, দারিদ্র্যকে হাসিমুখে বরণ করে দেশের ভবিষৎ মেরুদণ্ড গড়ে তোলার মহান দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষকরা, তুচ্ছ দুটো পয়সার জন্য, সামান্য দুটো অসুবিধার জন্য, তারা নিজেদের নামিয়ে আনবে, আদর্শ চুলোয় দিবে, শিক্ষা-দীক্ষাহীন অসভ্য মজুর ধাঙরের মতো হাঙ্গামা করবে, তা কখনো হতে পারে না। রায়বাহাদুর তা বিশ্বাস করে না। রায়বাহাদুরের এই নীতিমূলক বক্তৃতার প্রতিবাদ হিসেবে এক অভিনব কৌশল আঁটে স্কুলের যুবকশিক্ষক গিরিন। তাঁর ছেলের অন্নপ্রাশনে রায়বাহাদুরকে নেমন্তন্ন করা হয়। তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য স্কুলশিক্ষক গিরিনের যে আয়োজন, তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী:
যথাসাধ্য আয়োজন? বৈঠকখানার ভাঙ্গা তক্তপোষ, বিছানো ছেঁড়া-ময়লা শতরঞ্চির একপ্রান্তে কুণ্ডলী পাকনো ঘেয়োকুকুরের মতো দলা পাকিয়ে বসে আছে খালি গায়ে জবুথবু একটা মানুষ (গিরিনের পিতা), মেঝেতে লোম ওঠা বিড়ালটা ছাড়া আর কোন জীবন্ত প্রাণী নেই ঘরে। তক্তপোষ ছাড়া বসবার আসন আছে আর একটি, কেরোসিনের কাঠের একটা টেবিলের সামনে কালিমাখা একটি কাঠের চেয়ার। দিনে বৈঠকখানা হলেও ঘরটি যে রাত্রে শোবার ঘরে পরিণত, তার প্রমাণ গুটানো কাঁথা মশারীর বাণ্ডিলটা জানালায় তোলা রয়েছে, তক্তপোশের নিচে ঢুকিয়ে আড়াল করে গোপন করে ফেলবার বুদ্ধিটা বোধ হয় কারো মাথায় আসেনি। (টিচার)
রায়বাহাদুর গিরিনের বাড়িতে ঢুকে অন্নপ্রাশনের কোন চিহ্ন দেখতে পেলেন না। ভেতর হতে শুধু একটা শিশুর কান্নার শব্দ কানে এসে ধাক্কা লাগল। যার মুখে ভাত, সেই ছেলে জ্বরে ভুগছে। জ্বর আসার সময় বিশ্রীভাবে কাঁদে। অবচেতন হয়ে পড়লে আর কাঁদে না। গিরিনের স্ত্রীর বিয়ের শাড়ি ছাড়া আর কোন কাপড় নেই রায়বাহাদুরের সামনে আসার মতো। ছোট একটি কঙ্কাল বুকের কাছে ধরে পাংশুটে রঙের ছিন্নবস্ত্র পরিহিতা রোগা গিরিনের বউ সামনে আসতেই রায়বাহাদুরের মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। ভয়ে-আতংকে তাঁর ভেতরটা কেঁপে ওঠে। রায়বাহাদুরকে ফাঁদে ফেলে গিরিন আপোষহীন মুচকি হাসে। চতুর বাহাদুর নিজেকে সামলে নেয়। দীনহীন চেহারার বাড়িঘর, রুগ্ন সন্তান, জীর্ণ-শীর্ণ দেহের স্ত্রী, চিকিৎসার অভাবে পুষ্টিহীন বোন, এসব দেখিয়ে তাঁর স্কুলের শিক্ষক গিরিন কী চাইছে? করুণা না প্রতিবাদ, রায়বাহাদুর দ্বিধায় পড়ে। এভাবে তার কাছ হতে অনুগ্রহ আদায় করা যায় না, বরং সমূহ বিপদ, একথা তার স্কুলের একজন শিক্ষকের না জানার কথা ছিল না। বাস্তব অর্থে একজন শিক্ষকের জীবন কী পরিমাণ দূর্দশাগ্রস্ত এবং তাঁর গতকালের বক্তৃতা কতটা অন্তঃসারশূন্য ও বাস্তবতাবর্জিত, রায়বাহাদুর বুঝলেন ঠিকই, তাই বলে, ঘাড় ধরে বাড়ি টেনে এনে এমন নিষ্ঠুর প্রতিবাদ! ফাঁদে পড়ে গিরিনের বেতন বৃদ্ধিব আশ্বাস দিলেন বটে, তা ছিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কৌশল। বস্তুত তীব্র আত্মঅবমাননায় ভোগেন রায়বাহাদুর। বিনয়ের সাথে গিরিন বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে রায়বাহাদুর আরো অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি পড়েন। এরপরেই গিরিনের ঘর-সংসারের দৈন্য যেন তাকে শাসনের সুরে প্রতিবাদ করেছে। রুগ্ন শিশু মরে গিয়ে কান্না থামিয়ে তাকে দায়ী করতে চায়। উঠানে উলঙ্গ তিন ছেলে খেলার ছলে যেন তাকেই উপহাস করেছে। আর এসবেরই সমুচিত পুরস্কার গিরিনের বরখাস্তের নোটিশ। অবশ্য ক্ষমতা থাকলে রায়বাহাদুর ফাঁসির হুকুম দিত।
গিরিনের মতো শিক্ষকদের নিয়তির খুব একটা হেরফের দেখি না বর্তমান বাস্তবতায়। রায়বাহাদুরের ভূমিকায় অবতীর্ণ এ সময়ের প্রশাসনযন্ত্র। তারা শিক্ষকের মহত্ত্ব স্বীকার করলেও জীবন-জীবিকার প্রশ্নে নির্বিকার! বরং শিক্ষকের আদর্শের সুযোগে ন্যায্য পাওনা হতেও বঞ্চিত করে। অভাব-অনটনে অসুস্থ জীবন, ভেতরে চরম দারিদ্রের ঘা, তবু মধ্যবিত্তীয় ভদ্রতার আবরণে তাদের মুখে থাকে হাসি। মানিক শিক্ষক জীবনের অন্তর্নিহিত বাস্তবতার নিষ্ঠুর সত্যই বিশ্লেষণ করেছেন। যুগ বদলেছে, কোন অজুহাতেই ব্যক্তিমানুষ তার অধিকার ছাড়তে রাজি না। এতকাল শিক্ষকের আদর্শ নিয়ে গল্প লেখা হত। মানিকই প্রথম শিক্ষকের অধিকারের প্রশ্ন তুলে গল্প লিখলেন।
বিশশতকের সংকটের শিকার শিশুরাও। তারাও অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। মানিকের ‘আর না কান্না’ গল্পে সাত বছরের শিশু কন্যা পেট ভরে ভাত খাওয়ার আন্দোলনে নামে। প্রতিপক্ষ এ শিশুর মা। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরও যতীনের সংসারে চরম অসন্তোষ। পেট ভরে ভাত খাওয়ার দাবিতে তারই আত্মজারা বিদ্রোহ করেছে। বিশেষত, মেজ মেয়েটা দারুণ আক্রোশে মর্মান্তিক সব কথা বলেছে মাকে।মেজ মেয়েটা ছ্যাঁচড়। সভ্যতা ভব্যতা কিছু শেখেনি সাত বছর বয়সে। সে ফ্যাঁস করে ওঠে, ইস্! তোমরা খাবে না খাবে আমাদের কি? আরো ভাত রাঁধনি কেন? তোমরা খাও-না যত খুশি, আমরা না করেছি? আমাদের খালি মারবে, আমাদের খালি পেট ভরে খেতে দেবে না! মায়ের অক্ষমতার বিপরীতে মেয়ের আক্রমণাত্মক ভূমিকা সত্যিই আমাদের প্রচলিত মূল্যবোধের জন্য ভয়ানক অশুভ সংবাদ। মেয়ের চোখে মা-ই অপরাধী, জন্ম দেবার অপরাধে অপরাধী। তাদের পেটভরে ভাত খেতে দিতে অক্ষম সে। প্রতিবার খাদ্য গ্রহণের সময় বুভুক্ষু সন্তানদের মায়াভরা আর্তি, মা অবলার নির্মম অভিনয়, গল্পের শরীরজুড়ে বিশশতকের মধ্যবিত্ত সমাজ বাস্তবতার নির্মোহ উপস্থাপন।
চারজন একসঙ্গে খেতে বসে। তার মানে চারজনকেই
একসঙ্গে বসানো হয়, একসঙ্গে চুকিয়ে দিলেই হাঙ্গামা চুকে যায়।
অবলারও সহ্যের সীমা আছে তো।
আমি আলু পাইনি মা।
আমায় ডাঁটা দিলে না যে ?
একটুখানি ডাল দাও মা, শুধু একটু খানি।
পেট ভরেনি।
আমারও ভরেনি।
খা খা আমার হাড়মাংস চিবিয়ে খা তোরা। (আর না কান্না)
ক্ষুধার অসহ্য যন্ত্রণার কাতরানি সহ্য করতে না পেরে যতীনের মেজ মেয়ে শেষে মাঝরাতে ঢুকে পড়ে রান্নাঘরে। অন্ধকারেই জল-আটা মিশিয়ে খাবার আয়োজন করে, কিছু আটা ছড়িয়েÑছিটিয়ে পড়ে মেঝেতে। বলা চলে, বিশশতকের অনাহারক্লিষ্ট সব শিশুরই প্রতিনিধিত্ব করেছে যতীনের মেজ মেয়ে। কোন যুক্তি নয়, বাড়ন্ত শিশুরা চায় পেটভরে ভাত খেতে, মন খুলে হাসতে, খেলতে, বেড়ে উঠতে। আর এ দায়িত্ব তাদেরই, যারা পৃথিবীতে এনেছে। অবলা পরাজিত, প্রতিপক্ষ তারই সন্তনের যৌক্তিক আন্দোলনের কাছে। বিধ্বস্ত অবলা যখন আর্তনাদ করে ওঠে, আর সয় না, এবার আমি মরব। তখনও সে মেয়ের নিষ্ঠুর আক্রমণের শিকার, মরো তো নিজে মরো না? আমাদের মারছ কেন?
বিশশতকের রূঢ় বাস্তবতার আঘাতে দীর্ঘকালের প্রচলিত একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। রক্তের সম্পর্ক নয়, শ্রেণিগত অবস্থানই প্রধান। মধ্যবিত্ত জীবনের মাপকাঠি অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা। একান্নবর্তী পরিবারে যার আয় বেশি, তারই দাপট। পরিবারে তুলনামূলকভাবে কম উপার্জনশীল মানুষটি অবহেলা, অবজ্ঞা, অনাদরের শিকার হয়। ক্ষেত্রবিশেষে, বহুধা বিভক্তি আসে অখণ্ড পরিবার ব্যবস্থায়। এমনি মর্মান্তিক বাস্তবতা ‘একান্নবর্তী’ ও ‘চালক’ গল্প দুটিতে। মানিকের ব্যক্তি জীবন, এ দুটি গল্পের মতো, এত স্পষ্টভাবে তাঁর সাহিত্যে আর কোথাও প্রতিফলিত হয়নি। (সৈয়দ আজিজুল হক, পৃ.৩৭৮) এজন্য মানিক সাহিত্যে গল্প দুটির ভিন্ন মাত্রা আছে। ‘চালক’ গল্পে একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য অভিজিত শিক্ষিত চাকরিজীবী ভাইদের কাছে অপাংক্তেয়, অবহেলার পাত্র। তার অপরাধ সে বাসচালক। কিন্তু সংসারে অভিজিতই সর্বাধিক অর্থের যোগানদাতা। স্ট্যাটাস বজায় রাখার অজুহাতে শিক্ষিত ভাইরা যৎসামান্য ব্যয় করে সংসারে। তারপরেও অভিজাত হালদার পরিবারের লজ্জা; এবং কলঙ্ক। স্বয়ং পিতা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন। কখন এ ছেলে পরিবারের আভিজাত্য নষ্ট করে। এড়িয়ে চলে স্ত্রী পর্যন্ত। অভিজিতের সাথে এক টেবিলে খেতে, কথা বলতে ভদ্রতায় বাঁধে শিক্ষিত ভাইদের। অথচ বিপদে আবার অভিজিতের কাছে হাত পাতে নির্দ্বিধায়। শেষে পিতা রসিক হালদারের সত্য উপলব্ধি ঘটে। পরিবর্তন ঘটে তার দৃষ্টিভঙ্গির। সে ধরতে পারে, তার শিক্ষিত ছেলেদের কৃত্রিমতা, ফাঁকি ও ভণ্ডামি। অবশেষে অশিক্ষিত বাসচালক অভিজিত-ই তার নির্ভরতা, আশ্রয়। জীবনের বাকি সময় অভিজিতকে নিয়েই আলাদা থাকার আগ্রহ তার। রসিক হালদার চরিত্রটির মধ্যে স্পষ্টতই মানিকের পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াপাত ঘটেছে। বড় ছেলের কৃত্রিম, স্বার্থতাড়িত ব্যবহারে মানিকের পিতা-মাতা কী পরিমাণ মনঃযাতনায় ভুগেছেন, তা মানিকের বড় ভাইকে লেখা দীর্ঘ পত্র হতে (২৩.১১.১৯৪০) জানা যায়। পিতার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন, আপনি যেরূপ কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে বাবা যদি বা আর ২/৪ বৎসর বাঁচিতেন তাহা আর বাঁচিতে পারিবেন না। আপনার এক একখানি পত্র আসিতেছে আর বাবার কয়েকরাত্রি ঘুম হইতেছে না এবং সবসময় উত্তেজিত হইয়া থাকিতেছেন।
‘একান্নবর্তী’ গল্পে চার ভাই বীরেন, ধীরেন, হীরেন ও নীরেন এর একান্নবর্তী সংসার। সে সাথে বেঁচে আছেন বৃদ্ধ মা। পরিবারের লজ্জা ও কলঙ্ক সেজ ভাই হীরেন। বীরেন ডাক্তার, ধীরেন উকিল, নীরেন দুশ টাকায় শুরুর গ্রেডে সরকারি চাকরি পেয়েছে আর বছর। হীরেন সাতাশ টাকার কেরানী, যুদ্ধের দরুণ পাঁচ দশ টাকা বোনাস এলাওন্স বুঝি পায়। হীরেনকে ভাই বলে পরিচয় দিতে একটু শরম লাগে ভাইদের।
উপার্জনের তারতম্যের জন্য মানিক তাঁর পরিবারে চরম অবহেলার, কতকাংশে ঘৃণার পাত্রও হয়েছিলেন। মানিকের অক্ষমতা, আর্থিক দৈন্য বড় ভাই এর মনে ক্রোধের সঞ্চার করেছে বরং। গল্পের হীরেনের মতোই মানিক তাঁর ভাইদের কতটা বিরাগভাজন ছিলেন বড় ভাইকে লেখা পত্রে তার প্রমাণ মেলে।
আপনি কোনদিন আমাদের ভাই বলিয়া কাছে টানেন নাই, স্নেহ করেন নাই, বরং ঘৃণা, অবজ্ঞা ও অবহেলা করিয়াছেন। ইহা সত্য কথা, আমার কল্পনা নহে। চারিদিকে আপনার নাম, আপনি অনেক বড় হইয়াছেন, এবং আমরা সকলে আপনার সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলিয়া গর্ববোধ করিতেছি এবং সভয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে প্রায় দেবতার মত মনে করিতেছি কিন্তু সেই সঙ্গে দিনের পর দিন কথায় কাজে ব্যবহারে আপনি আমাদের বুঝাইয়া দিয়া চলিতেছেন যে আমরা অতি নিচু স্তরের জীব। (অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ.২৯১)
মানিকের ভাইদের মতো কেরানি হীরেনের ভাইরাও অধিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পৃথক রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা করে। একমাত্র বৃদ্ধ মা হীরেনের পক্ষে, আশ্রয়ে। যেমনটা মানিকের বৃদ্ধ বাবা করেছিলেন। বড় চাকরিজীবী ছেলে রেখে মানিকের উপর নির্ভর করতেন। ছোট ভাই নীরেন, সংসার ভাগাভাগি হওয়ায় তার বিলেতে পড়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ব্যাঘাত হওয়ায় হীরেনের পক্ষ নিল বটে, দুশো টাকা বেতনের চাকরি হলে কিছু দিনের মধ্যেই পক্ষত্যাগও করে। নীরেনকে বুঝাতে গিয়ে হীরেন যা বলেছে, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের বাস্তবতা আছে তাতে।
হীরেন তাকে বুঝিয়ে বলেছিল, কেন, এত ভালই হল! রোজ বিশ্রী খিটখিটে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। একটু দুধ, একটু করে মাছ, এই নিয়ে কী মন কষাকষি বলতো? দাদার আয় বেশি, তিনি ভালভাবে থাকতে চান। মেজদার ভাল উপার্জন হচ্ছে তিনিও খনিকটা ভালভাবে থাকতে চান। আমি সংসারে মোটে চল্লিশটা টাকা দিয়ে মজা করব। ওরা কষ্ট করবেন সেটা উচিত নয়। ভাই বলে কি কেউ কারো মাথা কিনেছে নাকি যে খাওয়া খাওয়ি কামড়া কামড়ি করেও একসাথে থাকতে হবে ভাই সেজে? তার চেয়ে ভিন্ন হয়ে সদ্ভাবে ভাইয়ের বদলে ভদ্রলোকের মতো থাকাই ভাল।
তোমার চলবে?
চলবে না ? কষ্ট করে চলবে। তবে অন্যদিকে লাভ হবে। মাথাহেঁট করে থাকতে হবে না, যাই খাই খুদকুঁড়ো হজম হবে। (একান্নবর্তী)
একই পরিবারের মানুষদের জীবনযাপনের এমন ভিন্নতা, বিশশতকের সময়ের সংকট। একদিকে ডাক্তার বীরেনের বউ পুলকময়ী, উকিল ধীরেনের বউ কৃষ্ণপ্রিয়ার আরাম-আয়েসের হল্লা চলে, অন্যদিকে সংসারের টানাপোড়নে হীরেনের বউ লক্ষ্মী দিশেহারা। পরিস্থিতি এক সময় আত্মহত্যার কথাও ভাবায়। অবশেষে তারই সমগোত্রীয় আরো তিন-চারজন কেরানির বউকে একজোট করে অভিন্ন শ্রেণিসম্পর্ক স্থাপন করে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার আপাত একটা বন্দোবস্ত করে নেয়। তাদের মধ্যে রক্তের বন্ধন নেই, আছে কেবল সামাজিক-আর্থিক অবস্থানের একতা।
বিশশতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশকের মধ্যবিত্ত মানসের নিষ্ঠুর রূপকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মধ্যবিত্ত জীবনের সর্বগ্রাসী অস্বস্তি দ্বারা আক্রান্ত মানিকের ব্যক্তি জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাই তীব্র ঘৃণা, অশ্রদ্ধার কারণ। প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করেছেন নিজ শ্রেণির ভেতরের ভণ্ডামি, ধূর্তামি, নষ্টামি, ফাঁকি, অসংগতি ও অন্তঃসারশূন্যতার জায়গাতে। জীবনের এই আত্মবঞ্চনা, জটিলতা, কূটিলতা, কৃত্রিমতা, স্বার্থপরতার নোংরামি দেখে মানিকের ভেতরে এতটাই ক্ষোভ-জ্বালার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সামান্যতম সহানুভূতিও পায়নি তাঁর কাছে। নিজ জীবনের পরতে পরতে অনুভব করেছেন এই জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণাকে। তাই অসুস্থ, রুগ্ন, পরাজিত মানিক তাঁর জীবনকে ঠেলে দিয়েছিলেন অন্ধকারের দিকে। প্রচণ্ড অভিমান নিয়ে পৃথিবী ছাড়েন জীবনের মাঝপথেই। অতুলচন্দ্র গুপ্তসহ আরো অনেকেই বলেছেন, মানিক আত্মহত্যা করেছেন। মানিক তাঁর নিজের বাস্তব জীবন দিয়েই উপলব্ধি করেছিলেন, মধ্যবিত্ত জীবন শেকড়বিচ্ছিন্ন, নৈরাশ্যপীড়িত ও মনোরোগাক্রান্ত। জীবনের কুৎসিত ও বীভৎস সত্যকে মিথ্যা ভদ্রতা ও আভিজাত্যের চাদরে ঢেকে দিয়ে ভেতরে পচন ধরিয়েছে নিজেদের এবং নষ্ট করেছে তাদের সমাজকেও; সেই সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে জাতীয় জীবনের মূলস্রোতধারা হতেও। গভীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক সংকটে পতিত মধ্যবিত্ত জীবনের মুক্তিই ছিল মানিকের আজন্ম স্বপ্ন। মানিক তাঁর লেখায় কোথাও উপদেশ দেননি। দক্ষ সার্জনের মতোই কাটা-ছেঁড়া করেছেন মধ্যবিত্তের জীবন, বের করে দেখিয়েছেন ভেতরের ঘা, যেন ঘা শুকিয়ে সুস্থ, সুন্দর, স্বাভাবিক ও সত্য জীবনে ফেরে।
গ্রন্থপঞ্জি
গল্পগ্রন্থ
বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। অতসী মামী, মানিক গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড। কলকাতা:
গ্রন্থালয় প্রা. লি., ১৯৬৩।
প্রাগৈতিহাসিক, মানিক গ্রন্থাবলী, ৩য় খণ্ড। কলকাতা: গ্রন্থালয়
প্রা. লি., ২য় সং ১৯৭৮।
বৌ, মানিক গ্রন্থাবলী, ৪র্থ খণ্ড। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রা.লি.
বিশেষ সং ১৯৮২।
মিহি ও মোটা কাহিনী, মানিক গ্রন্থাবলী, ৪র্থ খণ্ড। পূর্বোক্ত।
সরীসৃপ, মানিক গ্রন্থাবলী, ৩য় খণ্ড। পূর্বোক্ত।
সমুদ্রের স্বাদ, মানিক গ্রন্থাবলী, ৪র্থ খণ্ড। পূর্বোক্ত।
আজ কাল পরশুর গল্প, মানিক গ্রন্থাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা:
গ্রন্থালয় প্রা.লি. ২য় সং ১৯৮০।
খতিয়ান, মানিক গ্রন্থাবলী, ৮ম খণ্ড। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রা.লি.
বিশেষ সং ১৯৭৪।
ফেরিওয়ালা, মানিক গ্রন্থাবলী, ১২শ খণ্ড। কলকাতা: গ্রন্থালয়
প্রা.লি. ১৯৭৫।
অগ্রন্থিত গল্প
বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। যাকে ঘুষ দিতে হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত। ঢাকা: অবসর, ১৯৯৮।
কালোবাজারে প্রেমের দর । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প।
আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত। ঢাকা: অবসর, ১৯৯৮।
সহায়ক গ্রন্থ
রায়, শিবনারায়ণ। বাঙালিত্বের খোঁজে এবং অন্যান্য আলোচনা । কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০০৪।
ম্যাকলেন, জন. আর। “বঙ্গবিভাগ (১৯০৫) : হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক”। বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) । সিরাজুল ইসলাম (সম্পা)। ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯৩।
শামসুদ্দীন, আবু জাফর। “বাঙালীর আত্মপরিচয়”। বাঙালীর আত্মপরিচয়। সফর আলী আকন্দ (সম্পা.)। রাজশাহী: আই বি এস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১।
সরকার, স্বরোচিষ। কথাসাহিত্য ও নাটকে মুসলিম সংস্কারচেতনা ১৮৬৯-১৯৪৭। ঢাকা :বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫।
খান, রফিকউল্লাহ। বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ (১৯৪৭-১৯৮৭)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭, প্র.পু.মু. ২০০৯।
ঘোষ, বিশ্বজিৎ। বাংলাদেশের সাহিত্য । ঢাকা: আজকাল, ২০০৯।
হক, সৈয়দ আজিজুল। মানিক বন্দ্যোপধ্যায়ের ছোটগল্প: সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, প্রপ্র১৯৯৮।
চৌধুরী, গোপিকানাথ রায়। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য। কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, প্রপ্র ১৯৮৬।
ভীষ্মদেব চৌধুরী। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮।
বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বিচিত্রা, বিশ্বনাথ দে সম্পা.। কলকাতা: সাহিত্যম, ১৯৭১।
ইসলাম, আজহার। সাহিত্যে বাস্তবতা । ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।
দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ। বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ। কলকাতা: পুস্তক বিপণী, ৩য় সং২০০০।
মিত্র, ড. সরোজ মোহন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, চতর্থ সংস্করণ-১৯৯৯।
হক, হাসান আজিজুল। কথাসাহিত্যের কথকতা। হাসান আজিজুল হক রচনাসংগ্রহ-৪। ঢাকা: সাহিত্যিকা, ২০০৩।
হক, হাসান আজিজুল। অপ্রকাশের ভার। রচনাসংগ্রহ-৪। পূর্বোক্ত।
হক, হাসান আজিজুল। অতলের আঁধি। রচনাসংগ্রহ-৪। পূর্বোক্ত।
হক, হাসান আজিজুল। কথা লেখা কথা। হাসান আজিজুল হক রচনাসংগ্রহ-৫। ঢাকা:জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭।
ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান। সংস্কৃতির ভাঙা সেতু। রচনাসমগ্র ৩। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৪।
মুরশিদ, গোলাম। মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর: একটি নির্দলীয় ইতিহাস। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১০।
আখতার, সানজিদা। বাংলা ছোটগল্পে দেশভাগ (১৯৪৭-১৯৭০)। ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ২০০২।
মৃধা, প্রশান্ত। গল্পের খোঁজে। ঢাকা:শুদ্ধস্বর, ২০১১।
মামুদ, হায়াৎ, সম্পাদক। উন্মোচিত হাসান:হাসান আজিজুল হকের আলাপচারিতা। ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১১।
ভট্টাচার্য, তপোধীর। ছোটগল্পের বিনির্মাণ। কলকাতা:অঞ্জলি পাবলিশার্স, ২০০২।
জাফর, আবু। হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজবাস্তবতা। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬।
ডিনা, সরিফা সালোয়া। হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জমান ইলিয়াসের ছোটগল্প:বিষয় ও প্রকরণ। ঢাকা: বা/এ, ২০১০।
মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। সাহিত্য: এপার বাংলা ওপার বাংলা। কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০০৯।
ত্রিপাঠী, অমলেশ। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)। কলকাতা: আনন্দ পাবলিসার্স লি:, প্র.স ১৩৯৭ ।
সাত্তার, সরদার অব্দুস। কথাসাহিত্যের আঙিনায় দাঁড়িয়ে । ঢাকা:সুচয়নী পাবলিসার্স, ২০১০।
ম-ল, আলাউদ্দিন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: নির্মাণে বিনির্মাণে। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯।
অলোক রায়, সম্পা.। সাহিত্যকোষ:কথাসাহিত্য, সাহিত্য কোষ: কথাসাহিত্য। কলকাতা: বাগর্থ, ১৯৬৭।
আনোয়ার, চন্দন। হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য : বিষয়বিন্যাস ও নির্মাণকৌশল। ঢাকা : বাংলা একোডেমি, ২০১৫।
উজানের চিন্তক হাসান আজিজুল হক। ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১২।
কথাসাহিত্যের সোজাকথা। ঢাকা : যুক্ত, ২০১৬।
আনোয়ার, চন্দন, সম্পা। হাসান আজিজুল হক : নিবিড় অবলোকন। ঢাকা : কথা প্রকাশ, ২০১৫।
এই সময়ের কথাসাহিত্য ১ম ও ২য় খ-। ঢাকা : অনুপ্রাণন
প্রকাশন, ২০১৫।
গল্পপঞ্চাশৎ : শূন্যদশকের গল্প। ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৩
( চন্দন আনোয়ার, কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক এবং সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)