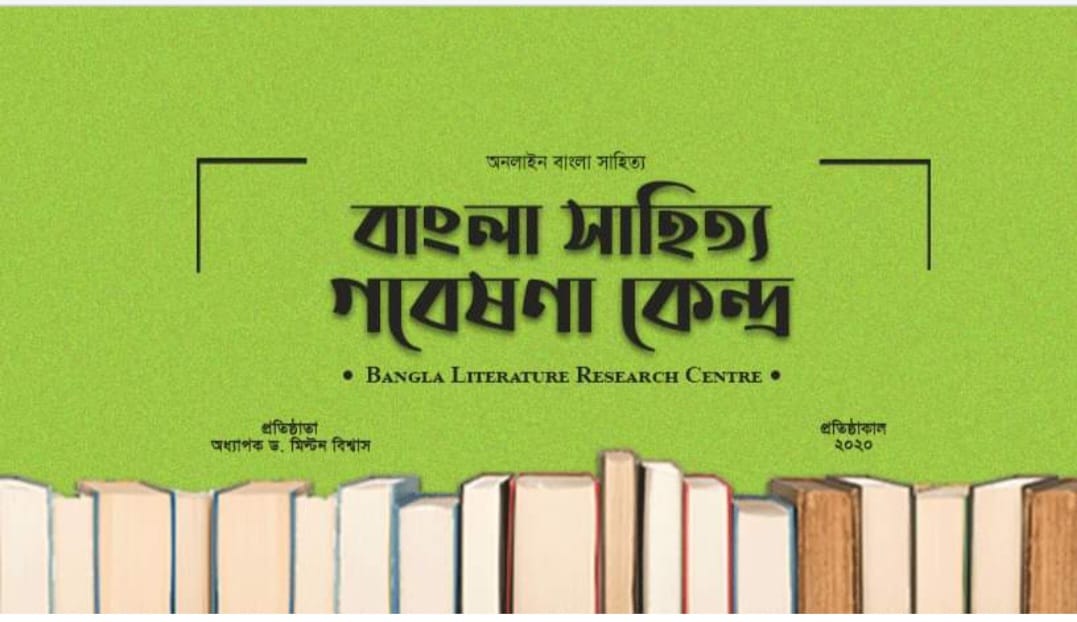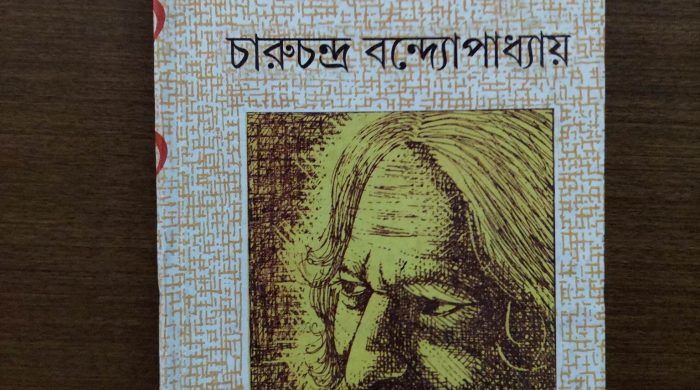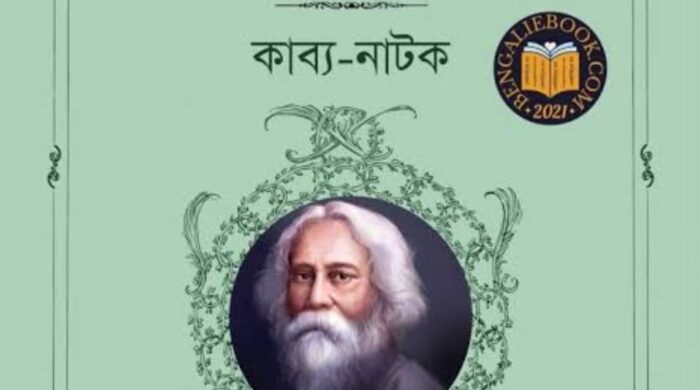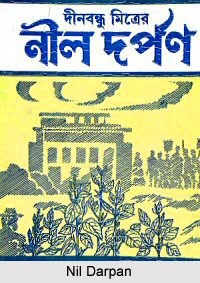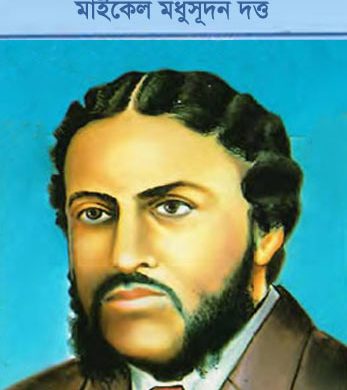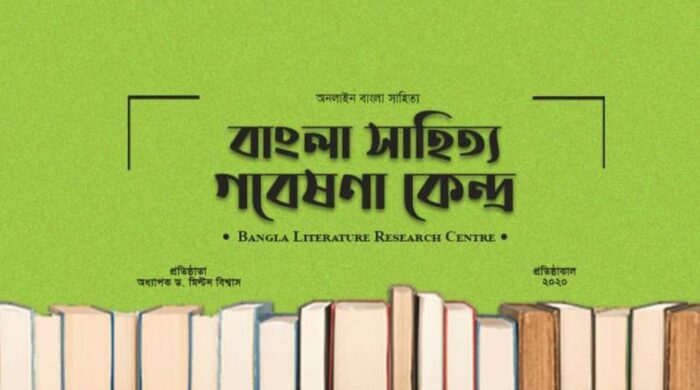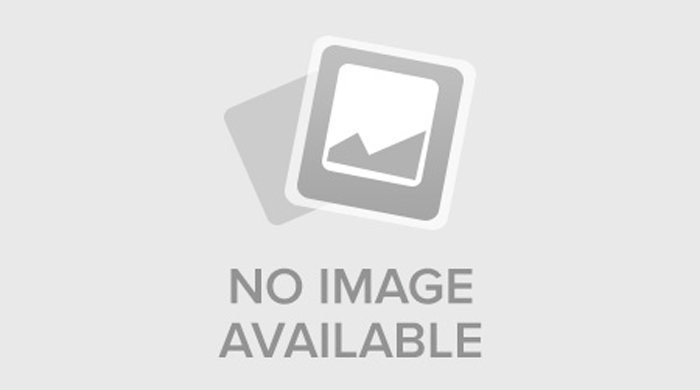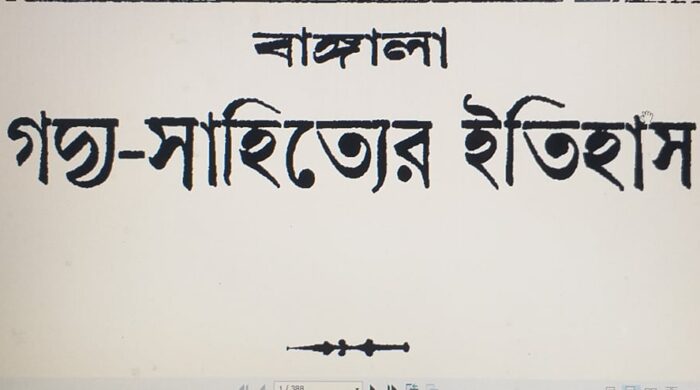মিল্টন বিশ্বাস।।
(প্রাককথন: আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্যের অন্যতম স্রষ্টা বুদ্ধদেব বসুর সৃষ্টিতে মিথ ও পুরাণ অনুষঙ্গ অঙ্গীকৃত হয়েছে জীবন বাস্তবতার সত্য প্রকাশের তাগিদে। জীবনের গভীরতর অনুভূতি জাগ্রত করতে তাঁর কাব্যনাটকগুলো বহুস্তরিক ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত। ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ তাঁর মিথ ও পুরাণভিত্তিক কাব্যনাট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মহাভারতের ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী বুদ্ধদেব বসুর নির্মাণে আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ববেদনা, মানসতা ও মনস্তত্ত্বে সমকালীন হয়ে উঠেছে। মূল পুরাণকাহিনিকে যেমন তিনি নতুন বোধে উত্তীর্ণ করেছেন তেমনি নাট্যকাহিনিতে মাতা–কন্যা, পিতা–পুত্র সম্পর্কের বিরোধগুলোকে উন্মোচিত করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। মানব সম্পর্কের দ্বন্দ্বগুলো উদঘাটিত হয়েছে লোলাপাঙ্গী–তরঙ্গিণী, বিভাণ্ডক–ঋষ্যশৃঙ্গ ও রাজমন্ত্রী–অংশুমান চরিত্রের বিন্যাসে। আমার বর্তমান প্রবন্ধের মৌল প্রতিপাদ্য নাটকে রূপায়িত সম্পর্কের বিরোধগুলোকে চিহিৃত করে বিশ্লেষণ করা।)
বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কাব্যনাট্য সৃষ্টিতে অনন্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যভাবনার সারাৎসার অধিগ্রহণে এই নাট্যকারের শিল্পীচৈতন্যে যে প্রণোদনা জাগ্রত হয়েছিল তারই অনিবার্য পরিণামে চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্যের প্রসারণ ও প্রতিষ্ঠা। তাঁর কাব্যনাট্যের অন্তর্চৈতন্যের উপলব্ধিময় স্তর প্রগাঢ় ব্যক্তিতায় নয়, প্রকাশ মাধ্যমের বিচিত্রতায় সমীকৃত হয়েছে। নতুন সময়-সমাজ-মানসিকতার যোগ্য অভিব্যক্তি প্রদানের জন্য নবতর নাট্য-আঙ্গিক অধিগ্রহণ ছিল অনিবার্য। ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ (১৯৬৬), ‘কালসন্ধ্যা’ (১৯৬৯), ‘প্রথম পার্থ’ (১৯৭০), ‘অনাম্নী অঙ্গনা’ (১৯৭০) এবং ‘সংক্রান্তি’ (১৯৭৩) নাটকে মহাভারতীয় পুরাণের পুনর্মূল্যায়ন করেছেন তিনি। ‘পুরাণের কাহিনীর অন্তরালে প্রসারিত শাশ্বত মানবাভিজ্ঞতার সঙ্গে ব্যক্তিক অনুভব ও স্বকালের জটিলতাকে যুক্ত করে তাকে রহস্য ও অনন্ত ইঙ্গিতে গূঢ় করে তুলেছেন।’(কণিকা, ১৯৯৪ : ১৩৮) ‘পুরাণসূত্রকে সম্প্রসারিত করে’ (সুদক্ষিণা, ১৯৯৭ : ৭৬) নতুন বয়নের (text) অন্তর্বুননে বুদ্ধদেব বসুর দক্ষতা বিশিষ্ট। তবে আলোচ্য নাটকের মিথ-পুরাণের পুনর্মূল্যায়নের সাফল্য-বিশ্লেষণ নয় বরং টেক্সট পর্যালোচনায় মাতা-কন্যা ও পিতা-পুত্র সম্পর্কের দ্বন্দ্ব অভিব্যক্তির তাৎপর্য উদ্ঘাটন আমার লক্ষ্য।
২.
‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’র অন্তর্বুননে মহাভারতীয় ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনিকে বুদ্ধদেব বসু নিম্নোক্তভাবে গ্রহণ করেছেন-
‘অঙ্গদেশে যখন অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, দৈবজ্ঞেরা বললেন, আজন্ম-বনবাসী তরুণ তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজধানীতে নিয়ে আসতে পারলেই দুর্যোগের অবসান হবে। ঋষ্যশৃঙ্গ কখনো কোনো নারীকে চোখেও দেখেননি, তরুণ হয়েও তপোবলে তিনি অগ্রগণ্য; তাই এই অসাধ্যসাধন শুধু তাঁরই পক্ষে সম্ভব, কিন্তু সেজন্য তাঁর কৌমার্যনাশ প্রয়োজন। রাজমন্ত্রীদের আজ্ঞায় এক বৃদ্ধ বেশ্যা এই অপহরণের ভার নিল। তারই রূপসী ও যুবতী কন্যা নিপুণ উপায়ে তপস্বীকে ব্রহ্মচর্য থেকে ভ্রষ্ট করলে; তারপর তাঁকে রাজধানীতে নিয়ে আসা কঠিন হ’লো না। তিনি নগরে প্রবেশ করামাত্র প্রচুর বৃষ্টিপাত হ’লো; রাজা লোমপাদ তাঁর কন্যা শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দিলেন। য়োরোপীয় হোলি গ্রেইল উপাখ্যানের যেটি অখৃষ্টীয় ও প্রাচীনতর অংশ, অনেক পণ্ডিতের মতে তার আদি উৎস এই ঋষ্যশৃঙ্গ-কাহিনী।’(বুদ্ধদেব, ১৩৯১ : ৮৭)
নাটকটি সম্পর্কে তাঁর আরো কিছু মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হল :
‘একটি পুরাণকাহিনীকে আমি নিজের মনোমতো করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা।…আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন।’ (বুদ্ধদেব, ১৩৯৩ : ৬)
প্রযোজনার জন্য পরামর্শ অংশে নাট্যকার আরো বলেছেন :
ক) ‘…এই নাটক বিশেষভাবে ভাষানির্ভর।’(বুদ্ধদেব, ১৯৯০ : ৩২৫)
খ)‘সারা নাটকটিতেই কোনো উচ্চহাসির অবকাশ নেই, অন্তত আমার অভিপ্রায়ের তা সম্পূর্ণ বহির্ভূত।’(ওই, পৃ ৩২৬)
গ) ‘ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী বিষয়ে সব কথা নাটকের মধ্যেই বলা আছে; এখানে শুধু যোগ করতে চাই যে চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গের ভূমিকাটি অভিনেতার বিশেষ কলানৈপুণ্য দাবি করবে। অন্তর্বর্তী এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে ঋষ্যশৃঙ্গ বাইরের দিক থেকে অনেক বদলে গিয়েছেন, রাজপুরুষোচিত বৈদগ্ধ্য ও কপটতা, বেঁকিয়ে ও ব্যঙ্গের সুরে কথা বলতে শিখেছেন- অথচ তাঁর সহজাত শুদ্ধতা এখনো অস্পৃষ্ট। জ্বালা, বিক্ষোভ, চাতুরী, শ্লেষ, এবং এক অপ্রকাশ্য বিশাল কামনা- এই বিভিন্ন ভাবগুলির সন্নিপাতে দ্বিতীয় অঙ্কের সরল তপস্বী এখন জটিল সাংসারিক চরিত্র হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ঐ সাংসারিকতা- রাজবেশের মতোই- তাঁর ছদ্মবেশমাত্র; যে-মুহূর্তে লোলাপাঙ্গীকে দেখে তাঁর চমক লাগলো (মাতাকে দেখে কন্যাকে মনে পড়া স্বাভাবিক), তারপর যখন ‘তরঙ্গিণী’নামটি শুনতে পেলেন, সে-মুহূর্ত থেকেই জেগে উঠতে লাগলো তাঁর মৌলিক ঋজুতা ও নির্মলতা; তরঙ্গিণীকে চোখে দেখার পর থেকে নিজের বা অন্যদের সঙ্গে তার কোনো লুকোচুরি আর রইলো না। তাই, যখন তিনি তপস্বীবেশে ফিরে এলেন, তখন তাঁর মধ্যে দেখা দিলো এমন এক স্বপ্রকাশ মহত্ত্ব, যা অন্যেরা সহজে ও সবিনয়ে মেনে নিলে।
লোকেরা যাকে ‘কাম’ নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে তারই প্রভাবে দু-জন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হলো- নাটকটির মূল বিষয় হলো এই। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে নায়ক-নায়িকার বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটলো; একই মুহূর্তে জেগে উঠলো তরঙ্গিণীর হৃদয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গের ইন্দ্রিয়লালসা; একই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হলো ‘পতন’ আর বারাঙ্গনাকে অকস্মাৎ অভিভূত করল ‘রোমান্টিক প্রেম’-যে ভাবে রবীন্দ্রনাথের ‘‘পতিতা’’য় বর্ণিত আছে, সেই ভাবেই। ‘রোমান্টিক প্রেম’অর্থ হলো কোনো বিশেষ একজন ব্যক্তির প্রতি ধ্রুব, অবিচল, অবস্থানির্বিশেষ, এবং প্রায় উন্মাদ হার্দ্য আসক্তি- যার প্রতীক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে ট্রিস্টান, এবং আমাদের সাহিত্যে রাধা। তরঙ্গিণী সেই আবেশ আর কাটিয়ে উঠতে পারলে না, তাই চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখে প্রথমে নিরাশ হলো সে; এবার যেন দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনাটি উল্টে গেলো- অর্থাৎ, ঋষ্যশৃঙ্গই চাইলেন তরঙ্গিণীকে ‘ভ্রষ্ট’ করতে, আর তরঙ্গিণী খুঁজলো ঋষ্যশৃঙ্গের মুখে সেই স্বর্গ, যা দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গ তার মুখে দেখেছিলেন, এবং যার পুনরুদ্ধারে সে বদ্ধপরিকর। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঋষ্যশৃঙ্গই তরঙ্গিণীকে বুঝিয়ে দিলেন, কোথায় মানুষের সব কামনার চরম সার্থকতা। নায়ক-নায়িকার এই বিবিধ পরিবর্তন-প্রসূত উদ্বর্তন যতটা কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা যাবে, ততটাই এই নাট্যাভিনয়ের সাফল্যের সম্ভাবনা।’ (ওই পৃ ৩২৬-২৭)
নাটকটি সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য : বুদ্ধদেব বসুর ‘‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’’ প্রথাগতভাবে কাব্যনাটক নয়। ‘‘চার অঙ্কের নাটক’’ রূপেই নাট্যকার নাটকটির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু গভীর অর্থে একটি কাব্যনাটক।…আবু সয়ীদ আইয়ুব বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগ্রন্থের মধ্যে ‘‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’’র নাম করেছেন। (কমলেশ, ১৯৯৯ : ১১৯)
৩.
পুরাণ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর আগ্রহ তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরু থেকেই লক্ষ করা যায়। তিনি সাহিত্যে বিশ্বমানবের অন্তঃসারকে উন্মোচন করতে চেয়েছেন। এজন্য তাঁর কাব্য ও নাটকে ভারতপুরাণ ও গ্রীকমিথ অঙ্গীকৃত হয়েছে। তাঁর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ (১৯৬৬), ‘কলকাতার ইলেক্ট্রা’ (১৯৬৮), ‘কালসন্ধ্যা’ (১৯৬৯), ‘অনাম্নী অঙ্গনা’ (১৯৭০), ‘সংক্রান্তি’ (১৯৭৩) নাটকে এবং ‘দময়ন্তী’ (১৯৪৩), ‘দ্রৌপদীর শাড়ি’ (১৯৪৮) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে পুরাণ ও মিথ ব্যবহারে কৃতিত্ব লক্ষণীয়।
বুদ্ধদেব বসুর কাছে ‘পুরাণকথা’একই বীজ থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে ভৌগোলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে-বহু বিভিন্ন ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে। (বুদ্ধদেব, ১৩৮৫ : ৩২)- এই পুরাণকথা জীবনের সত্য উদ্ঘাটনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। কারণ সাহিত্য পুরাণের গতিশীল বৈশিষ্ট্যের ধারক। এজন্যই মহাভারত কোনো সুদূরবর্তী ধূসর স্থবির উপাখ্যান নয়, আবহমান মানবজীবনের মধ্যে প্রবহমান। উপলব্ধির জন্য যে আভ্যন্তরীণ দৃষ্টি ও যুক্তির বিকাশ আবশ্যক তা মহাভারতে পরিদৃষ্ট হয়। এখানে লক্ষ করা যায় ‘চিরকালের সমস্ত মানবজীবনের প্রতিবিম্বন তাতে এমন মন্দেরও সন্ধান পাওয়া যায় যাতে এই ঘোর কলিকে আমরা আঁৎকে উঠি, আবার ভালোও অপরিসীম ও অনির্বচনীয়রূপে ভালো, জীবনের এমন কোনো দিক নেই, মনের এমন কোনো মহল নেই, দৃষ্টির এমন কোন ভঙ্গি নেই, যার সঙ্গে মহাভারত আমাদের পরিচয় করিয়ে না দেয়।’(বুদ্ধদেব, ১৯৮২ : ১১৯) ‘মহাভারত’ইতিহাস নয় ইতিহাসের এক বিশাল ও অস্পষ্ট আকরভাণ্ডার, যাতে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে তথ্য ও উদ্ভাবনা, ধূসর ও ধূসরতর স্মৃতিসমূহ যা কল্পনার দ্বারা রঞ্জিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। এই মহাভারত বুদ্ধদেব বসুর কাছে ‘শিল্প কর্মের অনিঃশেষ উপাদান-ভাণ্ডার’সমগ্র গ্রীক রোমক মিথলজির চেয়েও ঐশ্বর্যবান ও বিশালতর। এজন্য তিনি মহাভারতের মৌষলপর্ব অবলম্বনে লিখেছেন ‘কালসন্ধ্যা’, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারতের বনপর্বের কাহিনি বর্তমান সভ্যতার আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’তে।
মূলত সাহিত্যে মিথ ব্যবহৃত হয় লেখকের নিজস্ব বিশৃঙ্খল এবং রূঢ় বাস্তব জগতের কাহিনিবৃত্তকে একটি পরিপূরক বা নিয়ন্ত্রক শক্তি দান করার জন্য। পুরাণ নির্দিষ্ট করে একটি নতুন উপায় যার দ্বারা কল্পনার রীতিনীতিকে অধ্যয়ন করা যায়। একটি পুরাণ কাহিনি অবলম্বন করে তাতে সঞ্চারিত করা যায় ‘আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা’। কারণ পুরাণের প্রতীকায়নে বিভিন্ন বাস্তবতা উন্মোচিত হয়। ‘এই বাস্তবতা পৃথিবীর আদিম উৎসে পাওয়া যায়, সে বাস্তবতা এমন সম্পূর্ণ, নিরাসক্ত ও নির্মম যে তার তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্য রিয়ালিজম- এর চরম নমুনাও মনে হয় দয়ার্দ্র।’ (ওই পৃ ১১৮) পুরাণের মধ্যে আমরা নিজস্ব সত্তা উপলব্ধি করতে পারি। এক্ষেত্রে নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষণবিন্দু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কবিতার কার্যকারণে কবিই একান্ত বিবেচ্য কিন্তু কবিতা অস্তিত্ব পরিগ্রহণের বাহ্যিক হেতুরূপে নরথ্রপ ফ্রাই প্রত্নপ্রতিমাকে নির্দেশ করেছেন: The poet is only the efficient cause of the poem, but the poem, having a form, has a formal cause that is to be sought. On examination, Frye find this formal cause to be the archetype.( Wimsatt & Brooks, 1970 : 709)
ফ্রাই total history বলতে পুরাকল্প থেকে আধুনিক সত্য, পরিশীলিত অবস্থা পর্যন্ত যে ইতিহাসের ধারা তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তিনি সাহিত্যকে আদি সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে জটিলতা ও দুরূহতার প্রান্তিকতা বৃদ্ধি করেছেন। এই সম্ভাবনার আলোকে আদি মৌলরূপ (Archetype) সাহিত্যে নৃতত্ত্ব পরিধি থেকে রূপলাভ করেছে এবং প্রত্নপ্রতিমার অনুচিন্তনই সাহিত্যকে পুরাণ, লোকসাহিত্য, লোকগীতি প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং উপকরণ হিসেবে সেসব আধুনিক সাহিত্যের আভাস সৃষ্টি করেছে। একারণে বুদ্ধদেব বসু বিশ্বপুরাণের বিবর্ধমান-জ্ঞানালোকে পরিস্নাত হয়ে সৃষ্টি করেছেন ‘মহাভারতের কথা’ এবং অন্যান্য নাট্য ও কাব্যগ্রন্থসমূহ। তাঁর ভাষ্য-
‘… সেখানে আমার অধ্যাপনার একটি প্রসঙ্গ ছিলো তুলনামূলক ইন্দো য়োরোপীয়া এপিক- একদিকে ইলিয়াড, অদিসি, ঈনীড, অন্যদিকে মহাভারত ও রামায়ণ। সেই সূত্রে কিছু পুঁথিপত্র ঘাঁটতে হয় আমাকে, আমার গোচরে আসে অনেক তথ্য, সংকেত, প্রতিসাম্য, অনেক সম্বন্ধ স্থাপনের সম্ভাবনা আমাকে চঞ্চল করে…’(বুদ্ধদেব, ১৯৯০ : মুখবন্ধ)
পুরাণের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে আদিম মানুষের স্বপ্ন-কামনা-আশা-আকাঙ্ক্ষা। মানুষের আদিমতম ধ্যানধারণার-অভ্যাস-আতঙ্ক। এই আদি মানব অভীপ্সা আমাদের চেতনায় সংগুপ্ত থাকে। একবিংশ শতাব্দীর একজন নাগরিক কর্মস্থলে ধাবিত হয় অটোমোবাইলের মাধ্যমে, ব্যবসা বাণিজ্যের কার্যাদি সম্পন্ন করে টেলিফোনের মাধ্যমে, ইলেকক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা চালিত বিলাসবহুল উপকরণ সামগ্রী থেকে আনন্দ আহরণ করে এবং নিজেকে প্রস্তুত করে ঘুমের জন্য। আদি পুরাণের ‘ধ্যানধারণা’রাত্রে ঘুমের মধ্যে অবচেতনে প্রতীকায়িত হয়। এদিক থেকে বিচার করলে মনে করা হয় পুরাণ বিজ্ঞানের আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহিত্যকে অনতিক্রমণীয় আশ্রয় প্রদান করে থাকে।
বুদ্ধদেব বসুর স্বীয় রচনায় ‘তাঁর অভিজ্ঞতা ও ধ্যানের একটা যোগ্য আর্কিটাইপ’প্রতিচিত্রিত হয়েছে। তিনি ‘ইউলিসিসে’লক্ষ্য করেছেন- ‘মানব জাতির বহুযুগব্যাপী অভিজ্ঞতা’‘চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনাকালে’ বর্ণিত হতে। কিন্তু তিনি কাব্য বা নাটকে পৌরাণিক বা ভৌগোলিক উপমার যথেচ্ছ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। ভাব ও রসের কেন্দ্রচ্যুত মিথ বা পুরাণকাহিনির বিপক্ষে ছিলেন তিনি। অবশ্য তাঁর মানসরাজ্যে বিভিন্ন দেশের ও কালের উত্তম সাহিত্যের অঙ্গীকরণে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর প্রতীতি জন্মেছিলো যে, ‘বাংলার ঐতিহ্য জানতে হলেও বিশ্বের পথে বেরিয়ে পড়া’আবশ্যক। এ কারণে ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’রচনার পটভূমি বর্ণনায় তাঁর পুরাণ অভিজ্ঞানের তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয় :
‘… ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’- ঐ নাটকটাকেও কাব্যজাতীয় রচনা ব’লে ধরে নিচ্ছি- সেটা আমি লিখেছিলাম আটান্ন বছর বয়সে, কিন্তু প্রথম যখন ভেবেছিলাম তখন আমি সবেমাত্র উত্তরতিরিশ। সেই আমি প্রথম নিচ্ছি কালীপ্রসন্নর মহাভারতের আস্বাদ; সব বিস্তার ও অনুপুঙ্খসমেত ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান প’ড়ে চমকে উঠেছি- এর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ‘পতিতা’র বাইরে কিছুই জানতাম না। দুর্ভিক্ষের পশ্চাৎপট, গাঁয়ের মেয়েরা, অজ্ঞান কিশোর, তপস্বী ও বিদগ্ধ চতুর বারাঙ্গনার প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ের আশ্চর্য মুহূর্ত- এই সবই আমার কল্পনায় ধৃত হয়েছিলো তখন। রূপকল্পের আভাস জুগিয়েছিলো এলিয়টের ‘মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রেল’নাটকটা। মনে পড়ে লিখেও ফেলেছিলাম গাঁয়ের মেয়েদের মুখে প্রথম দুটোলাইন- সে দুটো দিয়েই ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’র আরম্ভ, যদিও সাতমাত্রা ছন্দ ও প্রথম দুটো শব্দ ছাড়া আদি লেখনের আর কিছুই সেখানে রক্ষিত হয় নি। এ ক্ষেত্রে আমি বোধ হয় জানি আগে লিখে উঠতে পারিনি কেন, কেন আমাকে- বা রচনাটিকে- এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। প্রথম পরিকল্পনার সময় আমি ঋষ্যশৃঙ্গ বিষয়ে যথেষ্ট জানতাম না, বিষয়টির মর্মস্থলে প্রবেশ করিনি তখনও, সেটিকে একটি স্বকীয় রচনায় জীবন্ত করে তোলার মতো তহবিল আমার ছিলো না। সেগুলি সংগৃহীত হলো নানা দেশে ঘুরে বেড়াবার ও ক্লাশ পড়াবার সময়, পড়াবার জন্য অনেক বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে, আর বিশ্বপুরাণে আমার বিবর্ধমান কৌতূহলবশত।’ (বুদ্ধদেব, ১৯৭৪ : ৬৭-৬৮)
বুদ্ধদেব বসুর নাটকের মিথ-পুরাণ, আঙ্গিক, ভাষা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষক-পণ্ডিত-সমালোচক আলোচনা ও মূল্যায়ন করেছেন। তবে এ মুহূর্তে এই আধুনিক কবির একটি শ্রেষ্ঠ রচনাকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ করতে চাই। বিশেষত প্রাচীন ভারতীয় সমাজে প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ককে মাতা-কন্যা ও পিতা-পুত্র সমীকরণে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে তাঁর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ নাটকটির চরিত্র ধরে ধরে।
৪.
প্রাচীন ভারতীয় সমাজে প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক হচ্ছে সামন্ত আদর্শের একটি রাজনৈতিক সম্পর্ক।সামন্তসমাজে শাসকের মতাদর্শগত শ্রেষ্ঠত্বের কাছে নিচুজাত সবসময় ভক্তি নত ছিল। এমনকি উঁচুজাতের প্রভুর জন্য নিচু জাতের দাসের জীবন উৎসর্গ করার ঘটনা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত ক্ষমতার মতাদর্শ সমাজের শক্তিশালী স্তম্ভ যা অধীনকে প্রভু থেকে পৃথক করে দিয়েছে। আর এটাই তার অস্তিত্বের একটি প্রাকৃতিক শর্তে পরিণত হয়েছে। এ সমাজে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলা এবং শোনার মাধ্যমে অধীনের স্বরূপ চিহ্নিত করা যায়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক কিংবা অধীনতার সম্পর্ক নিরূপণে নির্দিষ্ট শব্দের ব্যবহার, নাম ধরে ডাকা, নামকরণ, সম্বোধন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সম্মানিত ব্যক্তির নাম ধরে ডাকা নিষিদ্ধ যেমন পিতা-মাতা, চাচা-চাচী, শ্বশুর, বড় ভাই প্রভৃতি। এমনকি ভারতীয় সমাজে স্ত্রী তার স্বামীর নাম ধরে ডাকতে সংকোচ বোধ করে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে, মনুর বিধানে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভাষাগত বৈষ্যমের নিদর্শন পাওয়া যায়।
শ্রেষ্ঠ বা উত্তম মর্যাদার জন্য একজন তার অধীন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার সময় ঘৃণার ভাব প্রকাশ করতে পারে। কারণ কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার মানদণ্ডে সে উচ্চবর্গ অন্যদিকে অধীন নিম্নবর্গ। ব্রাহ্মণকে লক্ষ করে অপ্রাসঙ্গিক কথা, অসম্মানজনক মন্তব্য প্রভৃতির জন্য মনু শাস্তির বিধান দিয়েছেন। ক্ষত্রিয়ের জন্য ১০০ পণ দণ্ড, বৈশ্যের জন্য ১৫০-২০০ এবং শূদ্রের জন্য তাড়নাদি শারীরিক দণ্ড হবে। (মনু, ১৯৯৩ : ২২৯) মনুর বিধান অনুসারে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে তাহলে ওই শূদ্রের জিহ্বা কেটে ফেলা হবে কারণ তার জন্ম জঘন্য স্থান হতে হয়েছে। নাম এবং জাতি তুলে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের ওপর আক্রোশ করে, তবে এক গাছা জ্বলন্ত ও উত্তপ্ত লোহ তার মুখে নিক্ষেপ করা হবে। এমনকি শূদ্র যদি দর্পিতভাবে ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ করে তবে রাজা তার মুখ ও কর্ণে তপ্ত তেল ঢেলে দেবার ব্যবস্থা করবেন।(পৃ ২৩০) ভারতীয় সমাজে বিধান রয়েছে বড়রা কথা বললে ছোটরা চুপ থাকবে। নতুন বৌ স্বামী গৃহে এসে বেশি কথা বলবে না। এই চুপ করে থাকার মধ্যে অধীনতার লক্ষণ নিহিত। কৃষকরা ভূস্বামীর মুখের ওপর কথা বললে তা ভূস্বামীকে অপমান করার সামিল হত।
ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় আচার উৎসবে উঁচুজাতের প্রভুশ্রেণি অধীনগোষ্ঠীকে সীমিত অধিকার প্রদান করে। তারা চায় অধীন প্রশ্নাতীতভাবে আনুগত্য প্রকাশ করুক। এজন্য ধর্মীয় উৎসবে বা আচার-আচরণে ক্ষমতার সম্পর্কের প্রথাগত রূপই বহাল থাকে। যে কোন সমাজে আধিপত্যশীল সংস্কৃতি কমবেশি সামন্ত চরিত্রের হয়। মনুর বিধানসমূহের দিকে দৃষ্টি দিলে ভারতের সামন্ততন্ত্রে জাতভেদের ক্রমোচ্চবিন্যাসে ক্ষমতার সম্পর্ক স্পষ্ট হয়।
পারিবারিক অধীনতা :
মাতৃভগিনী, মাতুলানী, পিতৃভগিনী ও শ্বশ্রূ মা বা গুরুপত্নীর সমান।
(পৃ ৩৭)
পিতৃভগিনী, মাতৃভগিনী এবং স্বকীয় জ্যেষ্ঠা ভগিনী- এদের সঙ্গে মাতৃবৎ ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু মাতা এঁদের অপেক্ষা গুরুতরা।
(পৃ ৩৭)
দেবরের পক্ষে জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া মাতৃতুল্যা এবং কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পক্ষে পুত্র-বধূতুল্যা।(পৃ ২৫৫)
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব :
ব্রাহ্মণ যদি দশবর্ষ বয়স্ক হন, আর ক্ষত্রিয় শতবর্ষ বয়স্ক হন, তবু উভয়ের মধ্যে মান্যতা বিষয়ে পিতা পুত্রের ন্যায় পৃথক জানবে ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিকট পিতার ন্যায় মান্য হবেন। (পৃ ৩৭-৩৮)
যিনি সত্যস্বরূপ বেদমন্ত্র দ্বারা উভয় কর্ণ পরিপূর্ণ করে (বৈদিক গুরু) কৃতার্থ করেন, তিনি মাতা, তিনিই পিতা, তার ওপর কদাচ দ্রোহাচরণ করতে নেই।(পৃ ৩৯)
যিনি বেদ অধ্যাপনা দ্বারা ব্রহ্মজন্মের কারণ হন, যিনি বেদাদি ব্যাখ্যান দ্বারা স্বধর্মের উপদেশ করেন, সেই ব্রাহ্মণ, বালক হলেও বৃদ্ধ জনেরও ধর্মত পিতৃবৎ মাননীয়।(পৃ ৩৯)
নারীর অধীনতা :
শীলরহিত, পরদাররত, বিদ্যা-গুণ বর্জিত হলেও পতিকে উপেক্ষা না করে সাধ্বী স্ত্রী সর্বদা দেবতার ন্যায় তাঁর সেবা করবেন।(পৃ ১৫১)
স্ত্রীলোক সম্বন্ধে স্বামী বিনা পৃথক যজ্ঞ নেই ; স্বামীর অনুমতি বিনা ব্রত এবং উপবাস নেই ; – কেবল পতিসেবা দ্বারাই স্ত্রীলোক স্বর্গে গমন করেন।(পৃ ১৫১)
রাজা/ শাসন কর্তা :
রাজা বালক হলেও সামান্য মনুষ্যবোধে তাঁকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়; পরন্তু তিনি মহান দেবতা, মনুষ্যরূপে অবস্থান করছেন।(পৃ ১৬৮)
মনুর বিধান থেকে ভারতীয় সমাজে আধিপত্য ও অধীনতার স্বরূপটি পরিষ্কার হচ্ছে। তাঁর বিধানসমূহ স্পষ্টত অধীনকে চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। আধিপত্যশীলদের সংস্কৃতিতে ধর্ম চর্চা ও আচার পালন তাদের সুবিধার দিককে বিবেচনা করে প্রণীত হয়েছে। ধর্মের প্রত্যয় হচ্ছে মর্যাদা ও আধিপত্যের সংস্কৃতি।
অধীনতার সূত্রে শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, অভিবাদন, অগ্রগণ্যতা ও দূরত্ব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অভিবাদনের অঙ্গভঙ্গি হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের উত্তম জীবনের একটি দিক। যেমন কোনো স্থানে বয়স্ক ব্যক্তির আগমন ঘটলে যুবক স্বীয় আসন ছেড়ে বসতে দিবে। মনুর ভাষায় : বয়ো-বিদ্যাদি-বৃদ্ধ ব্যক্তি আগমন করলে যুবার প্রাণ ঊর্ধ্ব দিক দিয়ে বহির্গত হতে চেষ্টা করে ; কিন্তু প্রত্যুত্থান এবং অভিবাদনাদি দ্বারা সে আবার প্রাণ লাভ করে।(পৃ ৩৫) উঠে দাঁড়ানো, প্রণত হওয়া/ সাষ্টাঙ্গপাত, পা জড়িয়ে ধরা, করমর্দন- এসবই অধীনতার লক্ষণ; আবার অধীনের কর্তব্য হিসেবেও চিহ্নিত। এগুলো পুরোহিততন্ত্রের নির্দেশনা যা রাষ্ট্রের ক্ষমতা থেকেও আসে। শরীরের স্বতশ্চালন ব্যবস্থার ভিন্নতা চিত্র পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, জমিদার-প্রজা, উঁচুজাত-নিচুজাত প্রভৃতি সম্পর্কের সদৃশ। ভারতবর্ষে এখন অনেক গ্রামে ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পেলে মাটিতে মাথা ছুঁয়ে প্রণাম করতে হয়। কপালে জোড় হাত করে নমস্কার করা হয়। ব্রাহ্মণরা বর্ণবিন্যাসে শ্রেষ্ঠ জাত। এজন্য শূদ্র পথ চলার সময় দেখে চলবে, ব্রাহ্মণের গায়ে যেন শূদ্রের ছায়া না পড়ে। অগ্রাধিকার বা অগ্রগণ্যতার মাধ্যমেও অধীনতা চিহ্নিত করা যায়। একজন স্ত্রী তার স্বামীর পরিবারে বিচিত্র সাহচর্য সত্ত্বেও পরিবারের অন্যান্য নারীর মতই তার খাদ্য গ্রহণ করবে স্বামী বা গৃহ কর্তার পরে। আমাদের সমাজে এই অগ্রগণ্যতা সর্বব্যাপী। উৎসব, পালাপার্বণ, আচার-আচরণে প্রধান ব্যক্তি বা গোত্র প্রধানই প্রথম ক্রিয়ার সূচনাকারী হয়। শিকারীদের বর্শা নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় গোত্র প্রধান একটি বর্শা নিক্ষেপ করে উদ্বোধন করবে। ফসল কাটার গানে, ফসল ভরা গরুর গাড়ির সারিতে সে-ই প্রথম যাত্রাকারী। ফসল কাটার সময় কৃষিশ্রমিক প্রথমে উঁচুজাতের ক্ষেত্রের ফসল কাটবে তারপর অন্যান্য ও নিজের জমির ফসল। গ্রামীণ সমাজে বয়স এবং জাত অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতা নির্ণিত হয়। যুবক বয়োজ্যেষ্ঠর সঙ্গে হাঁটার সময় সম্মানজনক পদক্ষেপে দূরত্ব বজায় রেখে পিছনে পিছনে হাঁটবে। ভারতের উত্তরপ্রদেশে গ্রাম্য অনুষ্ঠানে মঞ্চ বা খাটে বসার ব্যবস্থা হল- একই জাতের (যে জাত অনুষ্ঠানের আয়োজক) বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি প্রধান হিসেবে খাটে বসবে, অন্যান্যরা সম্মান অনুযায়ী বসবে। ব্রাহ্মণ থাকলে সে প্রধান আসনে বসার অধিকার পায়। নিচু জাতের মানুষ এবং কখনো আবার দরিদ্র রাজপুত মেঝেতে বসে এবং অস্পৃশ্যরা এই গোষ্ঠী থেকে দূরে বসে। যেখানে ব্রাহ্মণরা খাটে বসার অধিকার রাখে সেখানে নিচে বসে দরিদ্র রাজপুত ও অস্পৃশ্যরা অশ্রেষ্ঠের পরিচয় দেয়। এই বসার স্তরের মধ্যে ক্রমোচ্চ পদবিন্যাস লক্ষণীয়। একই সঙ্গে অধীনতার। The subordinate must not be seated above the superordinate.(Ranajit, 1983 : 59) মনুর বিধানে গুরু-শিষ্যের আসন হল : গুরু-সমীপে শিষ্যের আসন ও শয্যা সর্বদা গুরু অপেক্ষা অনুন্নত হওয়া উচিত। গুরু দেখতে পান এমন স্থানে শিষ্যের যথেষ্ঠাসন অর্থাৎ যথেচ্ছ-করচরণাদি প্রসারণ করে উপবেশন করা উচিত নয়। (পৃ ৪৬)
৫.
প্রাচীন ভারতের সমাজকাঠামোয় প্রভু ও অধীনের সম্পর্ক ক্ষমতার সম্পর্কের দ্বারা বৃত্তায়িত। আমরা জানি রাষ্ট্র ক্ষমতা বা কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার বাইরেও ক্ষমতার কাজ চলে। রাষ্ট্রবহির্ভূত ক্ষমতা ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’র প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতার সার্বভৌমিক বা ব্যক্তিগত রূপের বাইরে যে অদৃশ্য অবয়ব সে-সম্পর্কে বলা যায়, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাই একমাত্র ক্ষমতা নয়। কিন্তু এক ধরনের ক্ষমতা প্রতিনিয়ত আমাদের সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিচ্ছে। আমরা শুধু কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার কথা বললে, আমরা শুধু তার স্ট্র্যাটেজির কথা ভাবি। তার সঙ্গে কীভাবে লড়াই করতে হবে-এসব ভাবনা জাগ্রত হয়। কিন্তু আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কে যে সব ক্ষমতা তৈরি হয়, পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যা, ছাত্র-শিক্ষক, বাড়িতে-রাস্তায়, সাধারণ-স্বাভাবিক আদান-প্রদানে, সেই ক্ষমতার সম্পর্ক সবসময় চলমান। অর্থাৎ আধিপত্য ও কর্তৃত্বের মনোভঙ্গি দেখা যায় সমাজের সর্বত্র। প্রত্যেক মানুষ ক্ষমতা ব্যবহার করে, আবার একইসঙ্গে সে ক্ষমতার দ্বারা অধীন হয়। রাষ্ট্র নয় সমাজের ভেতর ক্ষমতার এই পারস্পরিক আদান-প্রদান ও গতিবিধি ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ নাটকের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে আলোচনা করা যায়। নাট্যকারের ভাষায় : ‘কখনো-কখনো (বিশেষত প্রথম অঙ্কে) লোলাপাঙ্গী আমাদের মৃদু কৌতুক জাগাতে পারে, কিন্তু সমগ্র নাটকে তার বেদনার দিকটা ভুলে গেলে চলবে না; মনে রাখতে হবে তার পক্ষে অর্থলোভ ও প্রগলভতা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি তার মাতৃস্নেহ অকৃত্রিম। কন্যার সঙ্গে ব্যবহারে তার চরিত্রের এই দুই দিক সম পরিমাণে সক্রিয়, যেমন ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে ব্যবহারে বিভাণ্ডকেরও পরিচালক যুগপৎ তাঁর পিতৃস্নেহ ও পুণ্যলাভ।’ (বুদ্ধদেব রচনাবলী, পৃ ৩২৬)
পিতা বিভাণ্ডকের পরিসর থেকে বেরিয়ে গেছে পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ, আশ্রম ত্যাগ করে তরঙ্গিণীর সঙ্গে অঙ্গরাজ্যে উপনীত হওয়া ও শান্তার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের নৈকট্য প্রত্যাহার করে বেরিয়ে পড়া তপস্বী নিঃসঙ্গ পথিক। অন্যদিকে লোলাপাঙ্গীর বৈষয়িক ভাবনা, পেশাদারিত্ব মনোভঙ্গী, বাস্তবতা সম্পর্কে অতিসতর্কতা কোন কিছুই তরঙ্গিণীকে নিবৃত্ত করতে পারেনি তার আশ্রয়হীন নিঃসঙ্গ বেরিয়ে পড়াকে। এই উভয় যাত্রা পথিকদ্বয়কে যথাক্রমে পিতা ও মাতার কর্তৃত্ব ও বিকীর্ণ ক্ষমতার বাইরে নিয়ে গেছে। আধিপত্যকামী পিতার বলয়কে অস্বীকার ও মাতার স্নেহপরতন্ত্র, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার বৃত্ত অতিক্রম করে পৃথক পৃথক পথে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা শূন্যতার পথযাত্রা।
৬.
মাতা-কন্যা : লোলাপাঙ্গী–তরঙ্গিণী
আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব বেদনা ও রোমান্টিক আবেগ প্রকাশে এই নাটকে গৃহীত কাহিনী দেহকে কেন্দ্র করেও দেহাতীত ভাববাদে পরিণতি লাভ করেছে। মানুষের সব কামনার চরম সার্থকতা ত্যাগে- এই দৃষ্টিকোণ একান্তই প্রাচীন ভারতীয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে যেখানে নারীর পরিসর ছিল ক্ষুদ্র, লৈঙ্গিক পরিচয় মুখ্য সেখানে নারীর ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি, তার নিজস্ব উঠোন খুঁজে পাওয়ার ইতিবৃত্ত এই নাটকে খুঁজতে যাওয়া ঠিক নয়। কারণ গৃহলক্ষ্মী হয়ে ওঠা কিংবা জৈবিক নিপীড়নের শিকার নারীর নিজস্ব জগৎ ছিল পুরুষের প্রতাপে নিয়ন্ত্রিত। আমরা খুঁজতে চাই মাতা-কন্যার সম্পর্কের বৈপরীত্য তথা বিরোধগুলোকে।
তরুণী বারাঙ্গনা তরঙ্গিণীর মা লোলাপাঙ্গী। চম্পানগরের গণিকাদের মধ্যমণি তরঙ্গিণী। তার মা তাকে সর্বকলায় বিদগ্ধ করে তুলেছে। তাছাড়া রূপে, লাস্যে, ছলনায় তার তুলনা নেই। লোলাপাঙ্গী অঙ্গরাজ লোমপাদের রাজমন্ত্রীকে তরঙ্গিণীকে সর্ব বিদ্যায় পারদর্শিনী করে তোলার ফিরিস্তি দিয়েছে। তাতে রূপ, স্বাস্থ্য, সাজ সজ্জা থেকে শুরু করে শাস্ত্রপাঠ, ধর্মতত্ত্ব , শিল্পকলা ও রতিশাস্ত্র পর্যন্ত বিচিত্র বিষয়ের কথা বলে বলেছে : ‘আমরা সময় বুঝে মধুকুণ্ড, সময় বুঝে বিষভাণ্ড। এই সবই আমি তরঙ্গিণীকে শিখিয়েছি। যে-পুরুষ ওকে ভাগ্যবতী করে, তার কন্যার সঙ্গে ওর আচরণে ফোটে মাতৃভাব, তার স্ত্রীকে বলে চাটুবাক্য, তার দাসীদের দেয় পার্বণী; কিন্তু যদি পুরুষটির মুঠো কখনো আঁট হয়, তাহলে ওর তীব্র গঞ্জনা থেকে স্ত্রী, কন্যা, পরিজন কেউ নিস্তার পায় না।’ (বুদ্ধদেব, ১৩৯৩ : ২১-২২) স্পষ্টত লোলাপাঙ্গী তাদের দেহব্যবসার বাস্তবতা তুলে ধরেছে। তাদের ধর্ম বহুর পরিচর্যা। রোগী, উন্মাদ, নপুংসক ও ভিখারি ব্যতীত তাদের শরীরের অধিকারী সকলে, যথা শূদ্র, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, যুবা, রূপবান, কুৎসিত সকলে তাদের কাছে সমান। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সমাজ, সংস্কার ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বাইরে তারা, অন্তেবাসী, কিন্তু সাহসী। তবু কিশোর তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের কথা শুনে আঁতকে উঠেছে সে। লোলাপাঙ্গী ভীত হয়েছে ঋষিপুত্রের অভিশাপের কথা স্মরণ করে। বণিক ধনিকদের আদরিণী তরঙ্গিণী অভিশপ্ত হলে তার আশ্রয়চ্যুত হবার আশঙ্কা আছে কারণ তারা অনন্তযৌবনা নয়, তাদের অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই। দৈবক্রমে জীবন দীর্ঘ হলে জীবিকার নিশ্চয়তা কোথায়? অবশেষে তার বাস্তব বুদ্ধি জয়ী হয়েছে ‘দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা- আর যান, শয্যা, আসন, বসন, স্বর্ণালঙ্কার আর সিংহলের মুক্তা, বিন্ধ্যাচলের মরকতমণি’ পাওয়ার প্রত্যাশায় সে কন্যাকে বুঝিয়েছে ‘শোন, ঋষ্যশৃঙ্গ তপস্বী হতে পারেন, কিন্তু তাঁরও দেহ রক্তেমাংসে গড়া। বয়সে নিতান্ত তরুণ, আর… জানেন না, কাকে বলে নারী।’ (পৃ ২৪) মার কথায় তরঙ্গিণী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। রাজমন্ত্রীকে তার কার্য সিদ্ধির প্রস্তুতির পূর্ণ বিবরণ দিয়েছে।
প্রথম অঙ্কে মাতা-কন্যার সম্পর্কের মধ্যে যে পেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে তা তরঙ্গিণী কর্তৃক ঋষ্যশৃঙ্গের ধ্যান ভঙ্গের পর অব্যাহত থাকে নি। মাতা কন্যার দ্বন্দ্ব উচ্চকিত হয়ে উঠেছে।
দ্বিতীয় অঙ্কে তরঙ্গিণী ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে প্রথম উপলব্ধি করে চম্পানগরে সুন্দরী বলে তার খ্যাতি থাকলেও ‘আনন্দ তোমার নয়নে, আনন্দ তোমার চরণে’…(পৃ ২৮) প্রভৃতি অর্চনা কখনো সে পায়নি, ঋষি দৃষ্টি তার ভাগ্যে এই প্রথম। ঋষ্যশৃঙ্গের সান্নিধ্য তাকে নবচেতনায় উদ্দীপিত করে, দ্বন্দ্বের সূচনা সৃষ্টি হয় মাতার সঙ্গে।
তৃতীয় অঙ্কে রাজ্য জুড়ে আনন্দ সমাবেশে যোগদান থেকে বিরত থাকে তরঙ্গিণী। তরঙ্গিণীর পরিবর্তন যুবক চন্দ্রকেতুর কাছে মুনির শাপ ও ঋষি কর্তৃক বশীভূত হওয়ার পর্যায়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। লোলাপাঙ্গী চন্দ্রকেতুর প্রস্তাব জানাতে গিয়ে এত দিনের লালিত বিশ্বাসে অভিঘাত লাভ করে। চন্দ্রকেতুর তরঙ্গিণীকে ধর্মপত্নী করতে চাওয়া, এর পূর্বে যবন(গ্রীক) পণ্ডিত কৃশস্তোম, চীনদেশের দুই অমাত্য ও গান্ধারদেশের রাজপুত্রের আগমন, যবদ্বীপের বণিকের হীরক খচিত মুক্তোর মালার উপঢৌকন নিয়ে অপেক্ষা ও হতাশ হয়ে ফিরে যাওয়া প্রভৃতি ঘটনা মাকে চিন্তান্বিত করে তোলে। ঋষ্যশৃঙ্গকে জয় করার গর্বে গরবিনী তরঙ্গিণী ভেবেছে সে জয় করতে পারেনি।
এসময় তার মাতা বৈষয়িক দিকগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। তার সারাক্ষণ ভাবনার প্রসঙ্গে বলেছে তাদের ধর্ম পরিচর্যা, ইহকাল-পরকাল সম্পর্কেও তাদের সতর্ক থাকতে হবে। তখন তরঙ্গিণী বলেছে :‘মা, আমি পাপপুণ্য জানি না, ইহকাল-পরকাল জানি না; আমি যে কে তাও জানি না এখনো।’ (পৃ ৪৮) অর্থাৎ পূর্বে সে নিজের সম্পর্কে সচেতন ছিল কারণ তার পেশাদারিত্ব। বর্তমানে কন্যা নিজেকে ‘দুঃখিনী’ মনে করে। তার জন্মদাতা পিতা সম্পর্কে উৎসুক হয়ে উঠেছে। এই আত্মানুসন্ধানের পথে তার মা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ‘বারাঙ্গনারা স্মৃতি নিয়ে বিলাস করে না’। ‘অনুরাগ, অভিমান, মনোবেদনা এই পদার্থগুলো সারবান নয়, কর্পূরের মতো উবে যাওয়া ওদের স্বভাব।’(পৃ ৪৯)
তরঙ্গিণী জ্যোতির্ময়ী সতী কিংবা বারমুখীদের মুকুটমণি উভয় হবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু সে মনে করে কুলবধূ অর্থ প্রতি রাতে একই পুরুষ। কিন্তু সে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে না, সিদ্ধান্তহীনতায় আত্মপীড়ায় ভুগছে সে। তার হৃদয় উদ্বেল, কোথায় তার আশ্রয় তা অজানা। দাবি নিয়ে, ভালবাসার অধিকার নিয়ে দাঁড়ানোর সাহস তার নেই। লোলাপাঙ্গী তাকে এক গূঢ় কথা শুনিয়েছে : ‘সব নারী পত্নী হতে পারে, সতী হতে পারে না। বহুচারিণী হতে পারে, বারাঙ্গনা হতে পারে না। এক পুরুষে আসক্ত থাকলেই সতী হয় না; বহুচারিণীও সতী হতে পারে, কিন্তু বহুচারিণী মাত্রই যথার্থ বারবধূ নয়। সতী, বারাঙ্গনা- দুয়েরই জন্য হতে হয় গুণবতী, প্রাণপূর্ণা। দুয়েরই জন্য অসামান্য প্রতিভা চাই।’(পৃ ৫০) তরঙ্গিণী তার বেদনার কথা মাকে বলে নি। কোন পুরুষেরই পত্নী হতে চায় না সে। কারণ সে স্বভাবস্বৈরিণী। তার নিজের মুখের তলায় অন্য এক মুখ ছিল যা সে হারিয়ে ফেলেছে। সেই মুখ অন্বেষণ করছে সে। আর সেই দৃষ্টি যা তাকে বদলে দিয়েছে। ‘আমি চাই আনন্দ- প্রতি মুহূর্তে আনন্দ। আমি চাই রোমাঞ্চ- প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চ। আমি চাই সেই দৃষ্টি, যার আলোয় আমি নিজেকে দেখতে পাবো। দেখতে পাবো আমার অন্য মুখ, যা কেউ দ্যাখেনি, অন্য কেউ দ্যাখেনি।’(পৃ ৫৩)
লোলাপাঙ্গী সংস্কারাচ্ছন্ন মনের অধিকারী। তরঙ্গিণীর আবেগতাপিত হৃদয়ের উচ্চারণকে সে ভেবেছে তান্ত্রিক দিয়ে জাদু করা হয়েছে। তরঙ্গিণীর জন্মদাতা জনৈক ব্যক্তি, লোলাপাঙ্গীর সঙ্গে যার কিছুদিন একান্ত সম্পর্ক ছিল এবং যে লোলাপাঙ্গীর অন্য পুরুষের সংসর্গ পছন্দ করত না, সেই পুরুষ তরঙ্গিণীর জন্মের পর বাণিজ্য করতে বিদেশে যায় কিন্তু ফেরত আসেনি। পরে লোলাপাঙ্গী জানতে পারে উদার, অকৃতদার, ঈর্ষাপরায়ণ পুরুষটি বাণিজ্যে না গিয়ে অন্যত্র বিবাহ করে কোশল দেশে চলে গিয়েছে। তাকে লোলাপাঙ্গীও মন থেকে মুছে ফেলে। দেখা হয়নি, মনেও পড়েনি। মা’র যুক্তি ‘স্বকর্মে যাদের নিষ্ঠা আছে, তারা অন্য সব ভুলে যায়।’(পৃ ৪৯) প্রেমের কোন বাক্যও তার কাছে অসার। ‘কারণ দেহ যখন কামনায় তপ্ত, জিহ্বা তখন কী না বলে?’(পৃ ৪৯) মা’র মুখের তলায় অন্য মুখ লুকিয়ে আছে যা তরঙ্গিণীর পিতা দেখেছিল কন্যার একথায় মা বলেছে এসব ‘মনের বিকার’। আরো বলে ‘তরু তুই সংযত হ, সর্বনাশা অলীকের হাতে ধরা দিস না। আমি সরল মানুষ- আমার কাছে সার কথা শোন। আমরা যে যার কর্ম নিয়ে সংসারে আসি, কর্ম শেষ হলে চলে যাই। একের কর্ম অন্যের সাজে না- এই হলো চতুর্মুখের অনুশাসন।’(পৃ ৫০) স্থূলাঙ্গী লোলাপাঙ্গী তার স্থূল বুদ্ধি থেকে ভেবেছে তরঙ্গিণী শাপগ্রস্ত হলে পশু বা পাষাণ কিছু একটাতে রূপান্তর হত, কিন্তু তা হয়নি। এজন্য ঋষ্যশৃঙ্গের পায়ে পড়ে শাপমুক্ত করার অভিলাষী সে। ‘যুবরাজ দেবতার মর্ত্য প্রতিনিধি। ধর্মের অভিভাবক। তরঙ্গিণীকে আদেশ ও বাধ্য করতে পারেন তিনিই।’(পৃ ৫৪)
অন্যদিকে তরঙ্গিণী তার স্বগতোক্তিতে ভেবেছে শান্তার শয্যায় যুবরাজ তৃপ্ত কি? এসময় সে নিজেকে রিক্ত, সর্বস্বান্ত ভাবে। প্রথম সাক্ষাতের দৃষ্টিপাত প্রত্যাশায় উজ্জীবিত সে। এই দৃষ্টিকে তার স্বপ্ন, মতিভ্রম মনে হয় কিন্তু বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারে না সে। বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখার জন্য সে ভেবেছে ‘প্রিয়, আমার প্রিয়, আমার প্রিয়তম, কেন আমি তোমাকে নিয়ে চলে যাইনি- দূরে, বহু দূরে- যেখানে শান্তা নেই। লোলাপাঙ্গী নেই, চন্দ্রকেতু নেই- যেখানে তোমার নামে কেউ জয়কার দেয় না।’(পৃ ৫৫) আত্মপ্রত্যয়ী সে। সে একদিন তপস্বীকে লুণ্ঠন করেছিল, তরঙ্গিণী এখন এক তুচ্ছ জামাতাকেও জয় করতে পারে। মূলত ‘তৃতীয় অঙ্কে তরঙ্গিণীর সম্পূর্ণ রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। বহুবল্লভা বারবনিতা একনিষ্ঠা প্রেমিকায় পরিণত হয়েছেন। এখানেও নাট্যকারের নিজস্ব ভাবনা কার্যকরী। লোলাপাঙ্গী ও তরঙ্গিণীর পারস্পরিক কথোপকথনের মাধ্যমে বাস্তব-জীবনের স্তরগত ভেদ ফুটে উঠেছে। একান্ত গদ্যভাষিণী মা তাঁর কন্যাকে বুঝতে পারেন না; তাঁর কথায় ফুটে উঠেছে লৌকিক ভীতি, স্বভাবসিদ্ধ অর্থলোভ, অসহায়তা জনিত বেদনা ও মাতৃস্নেহ। অপরপক্ষে তরঙ্গিণীর কথায় অকল্পনীয় আনন্দ ও বেদনা যুগপৎ আভাসিত। উভয়ের আচরণেই পরিবর্তন ঘটে গেছে।’( কণিকা, ১৯৯৪ : ১৪৩)
চতুর্থ অঙ্কে লোলাপাঙ্গী যুবরাজের কাছে উপস্থিত হয়েছে ‘দীনা রমণী সামান্যা গণিকা’ রূপেই। তার কন্যা বংশগত বারাঙ্গনাবৃত্তি ত্যাগ করতে উদ্যত, পুরুষের সংস্রবও। এটা তার কাছে কন্যার নারীকুলের কলঙ্কিনীতে পরিণত হবার সামিল। সে নিশিদিন উন্মনা, একাকিনী থাকে। ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তার এই অবস্থা মা জানায়। বারাঙ্গনার শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য করেছে সে- আশ্রম থেকে চম্পানগরে এনেছে যুবরাজকে। এখন সে মর্মপীড়ায় পাণ্ডুর, মুমূর্ষু। পরিত্রাণ করতে পারেন যুবরাজ। তরঙ্গিণী সেই মুহূর্তে আশ্রমের সেই দৃশ্য স্মরণ করে তার দিক থেকে সেই দৃষ্টি প্রত্যাশা করেছে। নিজেকে নিয়ে এসেছে সে সম্পূর্ণ একান্ত নিজেকে। তাকে নন্দিত করতে বলে সে। ঋষ্যশৃঙ্গ অনাবিলভাবে তাকে তার অধিকারিণীরূপে স্বীকার করেছে। তরঙ্গিণী তার হৃদয়ের বাসনা, শোণিতের হোমানল। আশ্রম থেকে তরঙ্গিণী ছলনা করে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনতে গিয়ে যে দৃষ্টি দেখেছিল সেই দৃষ্টি আর আজ খুঁজে পায়নি সে।
‘আনন্দ- আমার আনন্দ সেদিন। আমি স্বর্গের দূত, আমি ছদ্মবেশী দেবতা। আমার অধরে বিশ্বকরুণার বিকিরণ। আর তোমার চোখ। সেই হৃদয়প্লাবী দৃষ্টি তোমার। ঋষ্যশৃঙ্গ, তোমার চোখের আলোয় আবার আমি নিজেকে দেখতে চাই। চাই রোমাঞ্চিত হতে, আনন্দিত হতে। আমাকে তুমি করুণা করো।’ (বুদ্ধদেব, ১৩৯৩ :৭১) স্বপ্নে, জাগরণে সেই দৃষ্টি দেখেছে সে, সেই দৃষ্টি আর নেই। শান্তার দৃষ্টিতে এই যুবতী প্রগলভা, মদমত্তা, উন্মাদিনী। আর অংশুমান বলেছে দুঃসাহসী, পাপিষ্ঠা।
লোলাপাঙ্গী তার সন্তানকে হারাতে চায়নি কিন্তু কন্যা স্বেচ্ছাচারিণী। তার ইচ্ছা তাকে যেখানে নিয়ে যায় সেখানে সার্থক হবে। উদ্বিগ্ন হতে নিষেধ করেছে ঋষ্যশৃঙ্গ। তরঙ্গিণীর কাছে চিরকাল ঋণী থাকবে সে। তরঙ্গিণী ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে যেতে চেয়েছে। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে ‘মেধা নয়, শাস্ত্রপাঠ নয়, অনুষ্ঠান নয়- আমাকে হতে হবে রিক্ত, ডুবতে হবে শূন্যতায়।’(পৃ ৭৪) অন্যদিকে তরঙ্গিণীকে লোলাপাঙ্গী জিজ্ঞেস করেছে ‘সন্নেসিনি’ হতে চলল কিনা তার উত্তরে সে বলেছে : ‘আমি কী হবো জানি না। আমার কী হবে তা জানি না। শুধু জানি, আমাকে যেতে হবে।’(পৃ ৭৫) মাকে বলেছে ভুলে যেতে, তাকে আর ফিরে পাবে না কেউ। তার মা যা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে তার অভাব নেই। অঙ্গরাজ্যে মা-মেয়ে উভয়ে স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র ছিল। এজন্য তার মার কাছে উৎসবের রাত্রিকে কালরাত্রি মনে হয়। তরঙ্গিণী রত্নালংকার ভূমিতে পরিত্যক্ত করেছে আর তার মা তা আঁচলে বেঁধে নিয়েছে। কারণ এই উজ্জ্বল স্মৃতি মূল্যবান।
৭.
পিতা-পুত্র :
বিভাণ্ডক আশ্রমে থাকবেন না এই সুযোগে তরঙ্গিণী ধ্যানভঙ্গ করবে ঋষ্যশৃঙ্গের। এই তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে পিতার কর্তৃত্বপরায়ণতা। দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতে পিতা সম্পর্কে ঋষ্যশৃঙ্গ নিজে যা অভিব্যক্ত করেছে তাতে তার তপস্যায় পিতার দাপট চিহ্নিত হয়েছে। ‘অপরাহ্ণে পিতার সঙ্গে আমার অধিবেশন; আমাদের চর্চার বিষয় বেদ, বেদাঙ্গ ও বেদান্ত। পিতা বলেন, ঐ তত্ত্ব অতিশয় সূক্ষ্ম, কিন্তু আমার মনে হয় সবই সরল, সব এই দিবালোকের মতো সহজ ও প্রতীয়মান। আমি আমার পিতার মতো মেধাবী নই, কোনো তর্কের বিষয় আমার বোধগম্য হয় না। স্বায়ংকালে, ক্ষুণ্নিবৃত্তির পর, আমরা যখন অজিনশয্যায় বিশ্রান্ত, আমি তখন পিতাকে দু-একটা প্রশ্ন নিবেদন করি। তিনি বলেন, ব্রহ্মতত্ত্ব সর্বজনের অধিগম্য নয়; তার জন্য চাই নির্জনতা ও একান্ত অভিনিবেশ। বলেন, নদীর ওপারে জনাকীর্ণ নগরে যারা বাস করে, তাদের বাক্য অনৃত, ব্যবহার প্রগলভ, সাধনাও অসাধু। কিন্তু আমি ভাবি: এমন কোন প্রাণী আছে, যে আনন্দিত হতে না চায়? আর আনন্দ যার লক্ষ্য, সে কি ব্রহ্মকেই আকাঙ্ক্ষা করে না? ঈপ্সাযোগ্য অন্য কিছু তো নেই। পিতা বলেন, এই অরণ্যে বহু রাক্ষস ও পিশাচ সঞ্চরণশীল, তাঁর অনুপস্থিতিকালে আমি যেন সতর্ক থাকি। কিন্তু আমি ভয় করি না। রাক্ষস, পিশাচ, শ্বাপদ-আমাকে তারা আঘাত করবে কেন? আর কোন রাক্ষস ছদ্মবেশী দেবতা, কোন শ্বাপদ শাপগ্রস্ত ঋষি- তা-ই বা আমি কেমন করে জানবো?’ (বুদ্ধদেব, ১৩৯৩ :২৬-২৭)
স্পষ্টত পিতার সঙ্গে পুত্রের মতপার্থক্য সূচিত হয়েছে যা নাটকীয় দ্বন্দ্বের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। মাঝে মাঝে পুত্রের সাধনায় দুর্দিন আসে। দিনব্যাপী ক্রিয়াকর্ম অভ্যাসমাত্র মনে হয়, অন্তঃকরণে অনুভূত হয় না। এরকমই দিনকে শুভদিন বলেছে ঋষ্যশৃঙ্গ। তরঙ্গিণী তার মধুর গভীর উদার সংগীত ও রূপ লাস্যে ছলনায় বিমোহিত করে তাকে। তরঙ্গিণী চির অপরিচয়ের গণ্ডী মুক্ত করে দেয় সুগন্ধি নিশ্বাস, আলিঙ্গন ও মুখচুম্বনের মধ্য দিয়ে।ফলে শাপভ্রষ্ট দেবতারূপী তরঙ্গিণীকে দেখে দুর্লভ চিত্তপ্রসাদ লাভ করে সে। তার মনে হয় এতকাল যেন সে তারই অপেক্ষায় ছিল। পশু, পক্ষী, বৃক্ষের সঙ্গে একাত্ম, নিখিলের সঙ্গেও। তাকে তরঙ্গিণী তার ছলাকলায় আবিষ্ট করে।
কর্কশদর্শন পিতা তার আবিষ্টভাবে ও কর্তব্যে অবহেলা দেখে রুষ্ট হন। পিতা-পুত্র সম্পর্ক বিবৃত হয় বিকীর্ণ ক্ষমতার উজ্জ্বল স্বাক্ষরে।
‘তোমার তো অন্য কোনো ব্রত নেই। তুমি আমার পুত্র-আমার শিষ্য। আমার ব্রহ্মচারী। কঠিন আমাদের নিষ্ঠা, দুর্জয় আমাদের নিয়ম। আমাদের ক্রিয়াকাণ্ডে কোনো ব্যত্যয় আমরা সহ্য করি না। পুত্র, তুমি যখন নিতান্ত শিশু, আমি তখনই তোমাকে তপশ্চর্যায় দীক্ষা দিয়েছিলাম। তারপর থেকে এমন কখনো ঘটেনি যে তুমি কোনো অনুশাসন লঙ্ঘন করেছো। কিন্তু আজ তোমাকে অন্যরূপ দেখছি কেন? কেন তুমি উন্মন। চিন্তাপরায়ণ, দীন-ভাবাপন্ন।…’(পৃ ৩৩-৩৪)
পুত্রকে উন্মন, চিন্তাপরায়ণ, দীনভাবাপন্ন, মলিন ও কণ্ঠে পুষ্পমাল্য পরিহিত দেখে যেমন জিজ্ঞাসু হয়েছেন তেমনি অনুপুঙ্খ আশ্চর্য ব্রহ্মচারীর গল্প শুনে চক্ষু রোষরক্তিম হয়ে উঠেছে পিতার। তরঙ্গিণীকে দেখে তার জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল হয়েছে জেনে পিতা বলেছেন : ‘ব্যর্থ। আমার সব সতর্কতা ব্যর্থ।’(পৃ ৩৪) পিতার কাছে পুত্রের অভিনিবেশ, প্রীত হওয়া, স্পন্দন জাগা ভ্রান্তি, অবিদ্যা। ব্রতের বিবরণ শুনে, তার অদর্শনে খিন্ন ব্যাকুল জেনে এবং সর্বোপরি তারই ব্রতে তার অভীষ্ট শুনে প্রতারিত-প্রলুব্ধ পাপস্পৃষ্ট বলেছেন পিতা। এ ঘটনার পর পুত্রকে নারী সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেন পিতা। পুত্রের কাছে নারী মানে- রূপমাধুরীর পরাকাষ্ঠা, পিতার কাছে উপযোগিতা মাত্র। মাতৃত্বের একটি যন্ত্র- সুগঠিত- তারই নামান্তর হলো নারীদেহ। নারীগর্ভে জন্মের কথা শোনান পিতা। বিন্ধ্যাচলের সানুদেশে তপস্যার সময় বসন্তে অকস্মাৎ আকাশপথে ঊর্বশীকে দেখে ধ্যানভঙ্গ হয় তাঁর। ব্রহ্মকে ধ্যান করেন তিনি। তাঁর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। মেঘ ও রৌদ্রালোকে দৃষ্টিভ্রান্তি অথবা গুপ্ত কামনার প্রতিচ্ছায়া, মরীচিকামাত্র অথবা তা ছিল উপবাসক্লিষ্ট নিঃসঙ্গতার উপজাতক। চিত্তবিকার দুঃসহ হলে ধ্যানাসন ত্যাগ করে অরণ্যে এক কিরাতযুবতীকে গ্রহণ করেন তিনি। পুত্র প্রসব করলে স্ত্রীকে ফেলে নদীতীরবর্তী আশ্রমে নিয়ে আসেন, কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করে স্খলনদোষ মুক্ত হন। স্ত্রী সম্পর্কে অবিলম্বে আগ্রহ হারান তিনি। অন্য কোন নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করেননি। আশ্রমে পুত্রকে মাতৃস্নেহের অভাব জানতে না দিয়ে বড় করেছেন। নারী সম্পর্কে ধারণা অজ্ঞাত পুত্রের। পিতা বলেছেন : ‘মাতা, তাই প্রয়োজনীয়; কিন্তু প্রাণীর পক্ষে সর্পাঘাত যেমন, তপস্বীর পক্ষে নারী তেমনি মারাত্মক।’(পৃ ৩৭) তাই পুত্রকে সতর্ক হতে বলেছেন। নারী মোহিনী, তপস্বীরা তার মায়াজাল ছিন্ন করতে পারেন। শুদ্ধচেতা, ধীমান ঋষ্যশৃঙ্গকে জয়ী হতে বলেছেন। তিনি পিতা ও প্রবীণ বলেই তাকে আশা ভঙ্গ না করাতে পরামর্শ দিয়েছেন। মন্ত্রের স্রষ্টা হতে বলেছেন। পুত্র ত্রিলোকের পূজনীয় হবে, তাই পাপমূর্তিকে চিন্তা থেকে উৎপাটন করতে বলেছেন তিনি। ‘পুত্রকে নারীর মোহ থেকে প্রতিহত করার জন্যই বিভাণ্ডক তাঁর পূর্বজীবনের কাহিনীর অবতারণা করেছেন।…নাটকের মধ্যে যেন দ্বিতীয় এক ‘নাটক’ সৃষ্টি করে, বুদ্ধদেব মহাভারতের ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনীর অনুসরণে ঊর্বশী দর্শনে বিভাণ্ডকের যে চিত্তবিকলতা এবং কামতাড়িত রূপ অঙ্কন করেছেন- তার মধ্য দিয়েই মানবজীবনে কামের অনাদি এবং অনন্ত-শক্তির পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে।…বুদ্ধদেব বিভাণ্ডকের আত্মকথার ভিতর দিয়ে জীবনের যে মৌলিক দ্বন্দ্ব দেখালেন তার ফলেই একাধারে প্রাচীনতম ও আধুনিকতম মানুষের জীবনের রুদ্ধরতিপীড়িত কাম-তৃষ্ণার রূপ অমন সমৃদ্ধ-আয়তন লাভ করতে সক্ষম হলো।’ (কমলেশ, ১৯৮০ : ১৩১-৩২)
পিতার অতীত জীবনের সঙ্গে পুত্রের বর্তমান ঘটনার মিল থাকলেও তাদের বিপরীত ইচ্ছা নাটকীয় সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে নারী নতুন জপমন্ত্র, নতুন এক জগৎ। নারীর স্পর্শের পুলকে শিহরিত সে ভেবেছে পিতার প্রত্যাশার বিপরীত :
‘…আমি অস্নাত থাকবো, তোমার স্পর্শের শিহরণ যাতে জাগ্রত থাকে।আমি অভুক্ত থাকবো, তোমার চুম্বনের অনুভূতি যাতে লুপ্ত না হয়। আমি অনিদ্র থেকে ধ্যান করবো তোমাকে।… তুমি কোথায়? এখানে-এখানে- এইমাত্র ছিলে, এখন কেন নেই? আমি তোমার বিরহে কাতর, আমি তোমার অদর্শনে সন্তপ্ত। তুমি এসো, তুমি ফিরে এসো।’ (বুদ্ধদেব, ১৩৯৩ : ৩৮)
মূলত ‘ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিভাণ্ডকের চরিত্র এবং তাঁর জীবন-কাহিনির সংযোগে বুদ্ধদেব নাটকের দ্বন্দ্বরূপটি বিষয়ে আমাদের প্রথম সচেতন করে তোলেন। জীবনের একটি মৌল এবং উজ্জীবক শক্তি ‘কাম’ নাম দিয়ে সাধারণত নিন্দা করা হয়। সেজন্যই মানবজীবনে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব, অসঙ্গতি এবং স্ববিরোধের। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গকে মোহিত করে তরঙ্গিণীর প্রস্থানের পরেই বিভাণ্ডকের প্রবেশ এবং তাঁর বিতৃষ্ণাসম্পন্ন উক্তির মধ্য দিয়ে মানবজীবনের সেই স্ববিরোধের রূপ এবং নাটকের বিরোধী শক্তির প্রকাশ দেখানো হয়েছে। কিন্তু কোনো বাস্তববাদী নাটকে মানবজীবনের এই দ্বন্দ্ব বা পিতা-পুত্রের সংঘাত যেভাবে নাট্যরূপ লাভ করতো, মিথাশ্রিত ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’- নাটকে সেভাবে তা ঘটে নি।’ (কমলেশ, ১৯৮০: ১৩১)
পুত্রের জৈব জীবনের বিরুদ্ধে বিভাণ্ডক। অথচ অপাপবিদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিণীর ‘অনঙ্গব্রতে’র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জৈব জীবনে অনুপ্রবিষ্ট। তরঙ্গিণীর কারণে তার দেহে জ্বালা। তরঙ্গিণী তার ক্ষুধা, ভক্ষ্য, বাসনা, শোণিতে অগ্নি, লুণ্ঠন, প্রয়োজনরূপে সিক্ত। তরঙ্গিণীর সঙ্গে আশ্রম ত্যাগ করে রূপান্তরিত ঋষ্যশৃঙ্গ চম্পানগরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিতে সিক্ত হয় অঙ্গরাজ্য। দূর হয় খরা, দুর্ভিক্ষ। সকল অশুভ প্রত্যাহৃত হয়। যৌবরাজ্যে ঋষ্যশৃঙ্গকে অভিষিক্ত করার জন্য অর্ধমাসব্যাপী উৎসবের ঘোষণা হয়।
ইতোমধ্যে লোমপাদের কন্যা শান্তার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গের। তাদের বিবাহ দৈব নির্ধারিত। তাই রাজমন্ত্রী তার পুত্র অংশুমান শান্তার প্রণয়াকাক্সক্ষী জেনে পিতার কর্তৃত্ব জাহির করে। শান্তা ঋষ্যশৃঙ্গকে বিবাহ করতে অস্বীকৃতি জানায় কারণ বদ্ধপরিকর ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গ আদ্যাশক্তিকে অর্ঘ্যদান করে তাকে যদি ত্যাগ করেন। ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় নারী তুচ্ছ, জায়াপুত্র নিতান্ত অলীক হতে পারে তার কাছে। তাই প্রণয়ী, প্রণয়যোগ্য অঙ্গদেশের যুবক রাজমন্ত্রীপুত্র অংশুমানের পরিণীতা হতে চেয়েছে শান্তা। ক্ষত্রনারী তার পতি নির্বাচনে স্বাধিকার পায়। স্বনির্বাচিত হবে তার স্বামী। এসব জেনে রাজমন্ত্রী শান্তা-অংশুমানকে প্রতিহত করার জন্য বন্দি করেছেন নিজ পুত্র অংশুমানকে। পুরস্ত্রীদের শান্তার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে বলেছেন। ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনকালে তাকে থাকতে হবে অনাহত ও প্রস্তুত। তপস্বীকে রতিরহস্যে দীক্ষিত করবে তরঙ্গিণী, তার ফলভোগ করবে শান্তা।
রাজমন্ত্রী পিতার এই সিদ্ধান্তের বলি অংশুমান। সে অর্ধমাসব্যাপী উৎসবকে অসহ্য মনে করে। ‘ঋষ্যশৃঙ্গ আর তরঙ্গিণী। আর আমার পিতা। কুটিল চক্রান্ত। নির্বোধ আমি। আর তুমি- অবলা, নির্জিতা, অসহায়। না-আর নিষ্ক্রিয়তা নয়-অনুশোচনা নয়- এখন চাই উদ্যম।’ (বুদ্ধদেব, ১৩৯৩ : ৪৪) হৃদয়ে দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি চোখে নিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অংশুমান বলেছে : ‘অঙ্গদেশের অনাবৃষ্টির জন্য লোমপাদ দায়ী ছিলেন না। বৃষ্টিপাতও আপনার কীর্তি নয়। যা ঘটেছে, তা বিশুদ্ধ কাকতালীয়।’(পৃ ৬৪) যৌবরাজ্যে তার অধিকার নেই বলেছে সে। ‘আমার ভাগ্যে লোমপাদই অপহারক। স্বয়ং আমার পিতা অপহারক। এবং প্রধান অপহারক-আপনি।’(পৃ ৬৫) রাজনীতির যূপকাষ্ঠে অংশুমান শান্তাকে পায়নি, বেদনার্ত হয়েছে, দেশান্তরী হয়ে তীর্থে তীর্থে পর্যটন করেও ভোলেনি স্মৃতি। অংশুমান জয়ী হয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তাকে কৌমার্য প্রত্যর্পণ ও তাকে রাজত্ব দান করে নিরুদ্দিষ্ট হলে। অর্থাৎ ঋষ্যশৃঙ্গ-বিভাণ্ডক ও অন্যদিকে রাজমন্ত্রী-অংশুমান এই দুই পিতা-পুত্র নাটকে দ্বান্দ্বিক ঘটনা সৃষ্টিতে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
বিভাণ্ডক-ঋষ্যশৃঙ্গ দ্বন্দ্বের আর একটি দৃশ্য দেখা যায় শান্তার অন্তঃপুরে। এখানে পিতা শীর্ণ, ক্লান্ত পুত্রের যুবরাজ হওয়ার গৌরবকে তুচ্ছ মূল্য ভেবেছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গরাজ্যে উপনীত হলে আশ্রম থেকে ছুটে এসে অভিশাপ দিতে গিয়েও উপঢৌকনে তুষ্ট পিতা প্রচণ্ড বিভাণ্ডক ফিরে গিয়েছিলেন। এখন তাঁর কাছে অলঙ্ঘনীয় নিয়তি। এক বৎসর পর পুত্রকে ফিরে নিতে এসেছেন পিতা তাঁর আশ্রমে। লোমপাদের অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। একদা পঞ্চদশ গ্রাম পেয়ে তুষ্ট হওয়া পিতাকে পুত্র যা বলেছে তা থেকে তাদের বিরোধ সচকিত হয়ে উঠেছে।
‘ঋষ্যশৃঙ্গ। আপনার তপস্যার মূল্য পঞ্চদশ গ্রাম, সে তুলনায় শ্লাঘনীয় এই রাজত্ব। পিতা, আপনারই সুযোগ্য পুত্র আমি।
বিভাণ্ডক (কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পরে- ভঙ্গুর স্বরে)। না, ঋষ্যশৃঙ্গ- পঞ্চদশ গ্রামের জন্য নয়, সে-সময়ে অঙ্গদেশের দুর্দশা দেখে আমি দয়াপরবশ হয়েছিলাম। তাই তোমাকে বলপূর্বক প্রত্যাহরণ করিনি।
ঋষ্যশৃঙ্গ(নির্মমভাবে)। অর্থাৎ- আপনি যাকে বলেন পাপ, আপনি তারই সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করেছিলেন।
বিভাণ্ডক। আমি যাকে বলি পাপ, অন্যেরা তাকে বলে জীবন। মাঝে-মাঝে সন্ধিস্থাপন তাই অনিবার্য হয়ে পড়ে।…’(পৃ ৬২)
ঋষ্যশৃঙ্গের জ্বলন্ত বাসনা ও তৃপ্তিহীন তৃষ্ণার কথা শুনে পিতা পুত্রকে তার আশ্রমের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মন্ত্রের স্রষ্টা হবার স্বপ্ন, অফুরাণ পথের নির্দেশ কোনোকিছুই টলাতে পারেনি পুত্রকে। তার কণ্ঠে পিতার বিরুদ্ধে তিক্ততা ঝরে পড়ে। পিতা অধীর আশ্রমে, একাকী নিঃসঙ্গ। হোমানল জ্বেলে মনে পড়ে পুত্রকে, যোগাসনেও। সাধনায় তার আনন্দ নেই, সংকল্পে স্থৈর্য নেই। তার পতন হচ্ছে, উদ্ধার করতে অনুরোধ করেন পিতা পুত্রকে। পুত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে চান পিতা। পিতা রিক্ত, পুত্রের ভবিতব্যে অংশ নিতে চান। পিতা মনে করেন পুত্র অঙ্গরাজ্যে আগন্তুক মাত্র। কর্ম সমাপন করেছে, এখন তার এখানে থাকা অনাবশ্যক। পুত্র পিতার সকল আকুল আহবানকে দৃঢ়স্বরে প্রত্যাখ্যান করেছে। ‘আমি এখানেই থাকবো। অন্য এক প্রতীক্ষায়- অন্য এক প্রতিজ্ঞায় আমি আবদ্ধ। আপনি আমাকে মার্জনা করুন।’(পৃ ৬৪)
দুর্বল ও উদ্ভ্রান্তভাবে পা ফেলে যাওয়া বিভাণ্ডককে আরো একবার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় পুত্রের সামনে। পুত্রের শেষ সিদ্ধান্তে তিনি তৃপ্ত হয়ে পুত্রের কাছে এগিয়ে গেছেন। আশ্রমে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছেন। পুত্রের অনুগামী হতে চেয়েছেন। ‘তোমার শিষ্য করে নাও।’(পৃ ৭৪)
ঋষ্যশৃঙ্গ (পিতাকে প্রণাম করে মৃদুস্বরে)। পিতা, আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনি আমার গুরু পূজনীয়, কিন্তু আমার পক্ষে গুরু আজ গুরুভার, শিষ্য প্রতিবন্ধক।’(পৃ ৭৪) তপস্যায় নিবেদিত থাকার কথা বললে সে বলেছে তার সামনে সব অন্ধকার। অন্ধকারে নামতে চেয়েছে সে। তরঙ্গিণীকে সে বলেছে কেউ কি কোথাও ফিরে যেতে পারে, আমরা যখনই যেখানে যাই, সেই দেশই নূতন। আমার সেই আশ্রম আজ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সেই আমি লুপ্ত হয়ে গিয়েছি। আমাকে সব নূতন করে ফিরে পেতে হবে। আমার গন্তব্য আমি জানি না, কিন্তু হয়তো তা তোমারও গন্তব্য। যার সন্ধানে তুমি এখানে এসেছিলে, হয়তো তা আমারও সন্ধান। কিন্তু তোমার পথ তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে তরঙ্গিণী।’(পৃ ৭৫)
আশ্রমের প্রসঙ্গে পুত্র যা বলেছে তা পিতার পরিসরের বাইরে চলে যাবার ইঙ্গিত। অনন্ত নিঃসঙ্গতায়, শূন্যতায় ডুবতে চাওয়ার ইশারা। অংশুমানের চোখে ঋষ্যশৃঙ্গ মহর্ষি হয়েছে । রাজপুরোহিতরা গেয়েছেন-
‘মুক্ত হলো স্রোতস্বিনী, অঙ্গদেশ রজস্বল,
পুত্র এলো স্বরাজ্যে, পূর্ণ হলো প্রতীক্ষা;
শান্তার পতি অংশুমান, যেমন সত্যবতীর শান্তনু,:
-উৎসব করো জনগণ, ধ্বনিত হোক জয়কার।
কিন্তু এই চক্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো দু-জনে,
অলক্ষ্য পথে, আত্মবশ, নিঃসঙ্গ:
তাদের ভূমিকা আজ বিচূর্ণিত ঘট, ঘটনার অধীন তারা নয় আর-
এক তপস্বী-যুবরাজ, এক বারাঙ্গনা-প্রেমিকা।’(পৃ ৭৭-৭৮)
ধূর্ত, হৃদয়হীন রাজনীতির জন্য যে জটিলতা ক্ষমতার কেন্দ্রে সংঘটিত হয়েছে তা ব্যক্তির স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কারণ হয়েছে এ নাটকে। এজন্য চন্দ্রকেতুর কাছে তরঙ্গিণীশূন্য জগৎসংসার নিরানন্দময় মনে হয়। শেষে লোলাপাঙ্গীর সান্নিধ্য প্রত্যাশায় জারিত হয় তার কাম্যতা।
৮.
বস্তুত ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’তে মাতা-কন্যা ও পিতা-পুত্র উভয় সম্পর্ককে অভিনবত্ব প্রদানে বুদ্ধদেব বসু কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। নাটকীয় বিরোধগুলোকে শিল্পিত রূপ প্রদান ও টেক্সট অন্তর্বুননে বহুমাত্রিক সূত্র সংস্থাপন এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
সূত্র নির্দেশ :
কণিকা সাহা, ড. আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য উদ্ভব ও বিকাশ, কলকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৯৪
কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, ড. বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার বুদ্ধদেব বসুর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’র ভূমিকা, কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা: লি:, ১৯৮০
বিশ্বজিৎ ঘোষ, বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭
বুদ্ধদেব বসু :
বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, নবম খণ্ড, নিরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), কলকাতা : গ্রন্থালয় প্রা: লি:, ১৩৯১
: বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, একাদশ খণ্ড, নিরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), কলকাতা : গ্রন্থালয় প্রা: লি:, ১৯৯০
: তপস্বী ও তরঙ্গিণী, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৩৯৩ : কবিতার শত্রু ও মিত্র, কলকাতা : এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা: লি:, ১৯৭৪
: মহাভারতের কথা, কলকাতা : এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৫
: রামায়ণ, প্রবন্ধ সংকলন, কলকাতা : দ্বিতীয় দেজ সংস্করণ, ১৯৮২
মনু, মনুসংহিতা, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত), কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৩
সুদক্ষিণা ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৭
Ranajit Guha, Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, Delhi : Oxford University Press, 1983
Wimsatt & Brooks : Literary Criticism: A Short History, India : Oxford & IBH Publishing Com Fourth Indian Reprint, 1970
(লেখক : ড. মিল্টন বিশ্বাস, বিশিষ্ট লেখক, কবি, কলামিস্ট, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরাম, নির্বাহী কমিটির সদস্য, সম্প্রীতি বাংলাদেশ এবং অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, email-drmiltonbiswas1971@gmail.com)