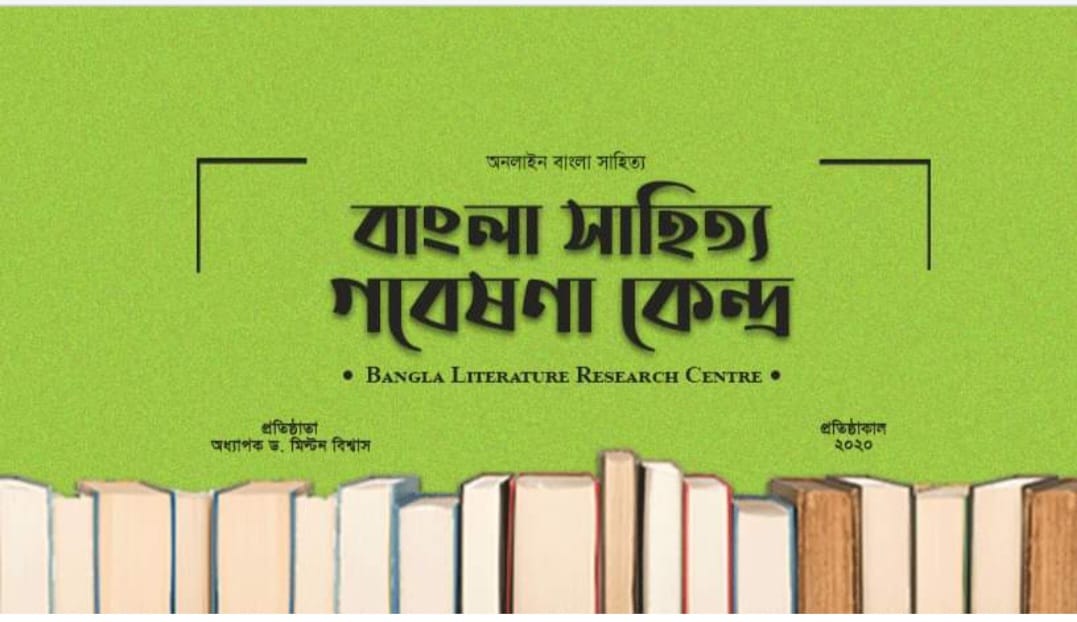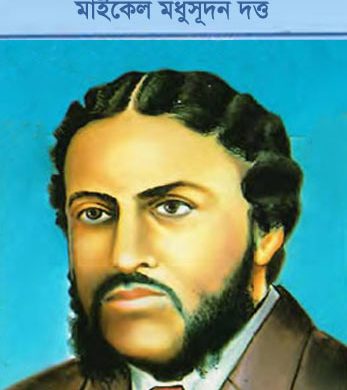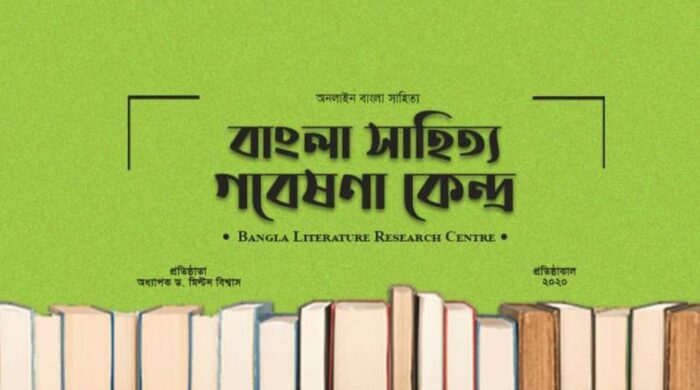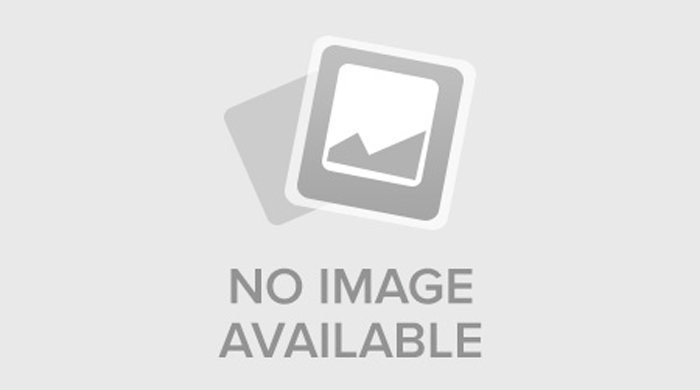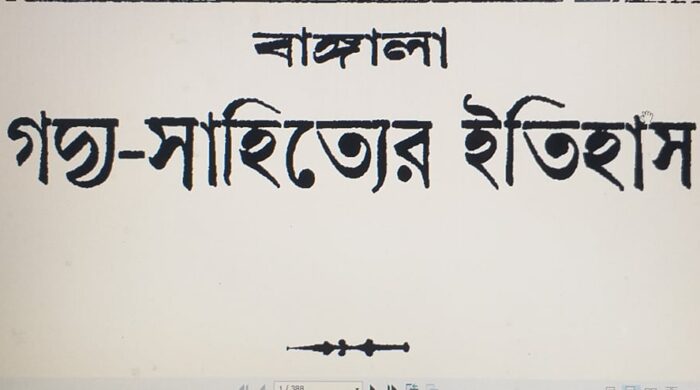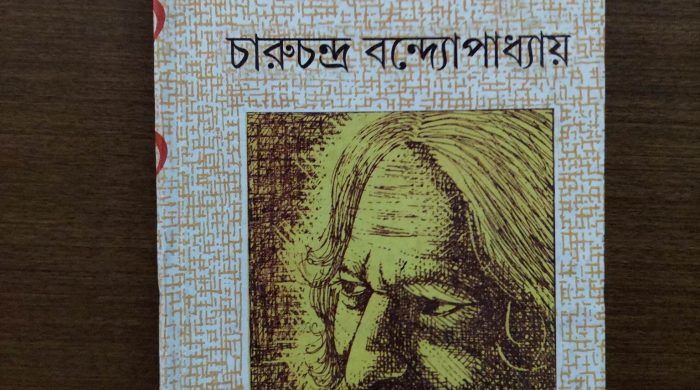আমার আর পাপড়ীনের বিয়েতে ইলিয়াস ভাই যে উপহারটি এনেছিলেন তার বাক্সটি ছিলো সবচেয়ে বড়। খুলে দেখি তার ভেতর একটা স্টাফ করা কবুতর। সেই কবুতর আমার বসার ঘরে ঠায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকেছে বহুকাল। তার জন্মদিনে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে নিয়ে ভাবতে গিয়ে সেই কবুতরটার কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে তার হুইল চেয়ারের পাশে একলা পড়ে থাকা এক-পাটি স্যান্ডেলটার কথাও। অন্যপাটি স্যান্ডেলের প্রয়োজন তখন তার ফুরিয়েছে। অপারেশন করে তার অন্য-পা তখন তিনি কলকাতায় রেখে সদ্য ফিরে এসেছেন ঢাকায়। মনে আছে মুখে পাইপ চেপে তার কেটে ফেলা পা নিয়ে স্বভাবসুলভ কৌতুক করছিলেন ইলিয়াস ভাই, বলছিলেন—‘জানো আমার যে পা টা নাই সেখানে প্রায়ই মশা কামড়ায়। মশা মারতে যাই, মশা কোথায়, পা-ই তো খুঁজে পাই না।’ তারপর হৃদপিণ্ডের সবকটা জানালা খোলা পরিচিত হাসিটি হাসেন। মনে ভাবছি এইসব স্যান্ডেল, কবুতরের স্মৃতি আসলে আমার সাহিত্যযাত্রা পরম্পরায় ইলিয়াস ভাইয়ের ঋণেরই অনুসঙ্গ বুঝি বা।
ইলিয়াস ভাইয়ের সাথে যখন পরিচয় আমি তখন মেডিকেলের ছাত্র, কিন্তু সওয়ার হয়েছি সাহিত্যের পাগলা ঘোড়ায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সেমিনারে সংক্ষিপ্ত আলাপেই টের পাই সাহিত্য অঙ্গনে এ-যাবৎ অগ্রজ যে লেখক-শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে উনি সে ধাতুর নন। ঘটনা অন্য। আলাপের পর মনে হয় দিকভ্রান্ত ঘোড়সওয়ারের সামনে যেন তিনি বিছিয়ে দিলেন একটা লাল সুড়কির পথ। সেই পথ ধরে আমি ছুটলাম তার ঢাকা কলেজে, মিউজিক কলেজের অফিসে, তার টিকাটুলির বাড়িতে। অপার প্রশ্রয়ে তিনিও আমার সামনে খুলে বসলেন তার আড্ডার ঝাঁপি। এর পর্যায়ে তিনিও উল্টোযাত্রা করে এলেন আমার আস্তানায়। ডাক্তারি পাশ করে উত্তরবঙ্গে যখন কাজ করছি তখন ইলিয়াস ভাই বহুবার আসেন আমার ওখানে। তাকে মটর-সাইকেলের পেছনে নিয়ে ঘুরি উত্তরবঙ্গের নানা জনপদ। পরবর্তীকালে সেই জনপদকে দৃশ্যমান দেখি তার ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাইরে তিনি আমার গল্পের প্রথম পাঠক হন, তার দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি যেখানে পাঠক ইলিয়াসকে আবিষ্কার করে নতুন আলোকে, তার মৃত্যুশয্যার পাশে থাকি, মৃত্যুর পর বসি তার ব্যক্তিগত ডায়রিগুলো সম্পাদনার কাজে। এই যে তাকে এমন নিরন্তর অনুসরণ করেছি তার কারণ এখন টের পাই। বুঝি তিনি আসলে সেই সাহিত্যিক ক্রান্তির দিনগুলোতে আমার ভাবনার নানা জট খুলতে সাহায্য করেছিলেন বিস্তর।
একটা জট তখন ছিলো সাহিত্য আর রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে। সেই আশির দশকের মাঝামাঝি যখন সাহিত্যচর্চা শুরু করি, পৃথিবীতে তখন সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী এই দুই শিবিরের ঠান্ডা লড়াই, বাংলাদেশ তখন সামরিক শাসনের কবলে। আমাদের সাহিত্য ভাবনার ভেতর তখন স্থানিক এবং বৈশ্বিক রাজনীতির এইসব ডামাডোল উপস্থিত ছিলো প্রবলভাবেই। তৃতীয় বিশ্বের একজন সংবেদনশীল তরুণ হিসেবে দেশকে সামরিক শাসনমুক্ত করে একটা বৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তখন আমাদের অনেকের কাছেই একটা জরুরি অভিষ্ট বলে মনে হয়েছে। শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদকে নন্দনতত্ব বিচারের মাপকাঠি হিসেবে চিনতে শিখছিলাম, যার মূল প্রবণতা হচ্ছে শ্রেণি সচেতনতা এবং পৃথিবীর সমাজতন্ত্রিক ভবিষ্যতের ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা। সেই মানদণ্ডে তখন বিচার্য হতো কে প্রগতিশীল আর কে প্রতিক্রিয়াশীল লেখক। আমরা এই পাঠ নিতাম যে কাফকা কিংবা কামু শক্তিমান লেখক হলেও প্রগতিশীল নন কারণ সমাজের ভবিষ্যত বিষয়ে তারা দিশাহীন। বরং আমাদের কাছে গুরুত্ব নিয়ে উপস্থাপিত হতেন ম্যাক্সিম গোর্কী বা নিকোলাই অস্ত্রভস্কি, যারা শ্রমজীবী মানুষের দ্রোহ আর সংগ্রামের ওপর আলোকপাত করেছেন। আমাদের বামপন্থি রাজনীতিবিদ বন্ধুরা বোঝাতেন কেন জীবনানন্দ দাশ পেটি-বুর্জুয়া প্র্রতিক্রিয়াশীল এক কবি। এইরকম একটা ভাবনা-পরিমণ্ডলের ভেতর সাহিত্যচর্চা শুরু করলেও আমার মনে একটা খটকা ছিলো বরাবরই। যে প্রবল বৈষম্যমূলক একটা সমাজে বাস করি সমাজতান্ত্রিক ভাবনার ভেতর তা থেকে মুক্তির একটা ইশারা যে আছে তা বুঝতে বেগ পেতে হতো না। কিন্তু জীবনের যে জটিল জঙ্গমতা আর বৈপরীত্য আছে শিল্পসাহিত্যে তা কেবলই প্রগতি আর প্রতিক্রিয়ার এই যান্ত্রিক বিভাজন দিয়ে বিচার্য হবে সে কথাতে সায় দিতো না মন। এ নিয়ে বামপন্থি বন্ধুদের সাথে বিতর্ক হতো। সেই খটকা থেকেই আমি মার্ক্সবাদী নন্দনতাত্ত্বিকদের ভেতর অপেক্ষাকৃত উদার লেখক আনেস্ট ফিশারের ‘আর্ট অ্যান্ড ক্যাপিটালিজম’ বইটা অনুবাদ করি। সেটাই ছিলো আমার প্রথম কোনো সাহিত্যকর্ম। সাহিত্য রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে আমার ভেতর যখন এই টানাপোড়েন চলছে সেই সময়টাতেই আমার পরিচয় ঘটে ইলিয়াসের সাহিত্যের সাথে এবং অল্পকাল পরে ব্যক্তি ইলিয়াস ভাইয়ের সাথে। ইলিয়াস ভাইয়ের সাথে আড্ডা রাজনীতি আর সাহিত্যের সেই জট খুলতে সাহায্য করে আমাকে।
ইলিয়াস ভাই একেবারে স্পষ্ট করেই বলতেন সাহিত্যে কোনো নীতিবাগিশতায় বিশ্বাস করেন না তিনি, চিন্তায় মার্ক্সীয়-বিশ্ববীক্ষায় বিশ্বাসী হলেও জীবনকে তিনি দেখেছেন একেবারে ম্যাটার অব ফ্যাক্ট হিসেবে। মানুষকে তিনি তার সামগ্রিকতায় ধরতে চেয়েছেন। ইলিয়াস মনে করতেন একজন মানুষ তার সংগ্রাম, ক্লান্তি, বেদনা, ক্ষুদ্রতা নিয়েই সম্ভাবনাময়। ইলিয়াসের ‘চিলেকোঠার সেপাই’য়ে হাড্ডি খিজির শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি কিন্তু তাকেও আমরা মিথ্যাবাদী, জোচ্চর হিসেবে দেখি। ইলিয়াস মজা করে বলতেন শ্রমজীবী মানুষ সবাই যদি মহানই হবে তাহলে তো আর বিপ্লবের প্রয়োজন নাই। তিনি খিজিরের একাধারে সংগ্রাম এবং জোচ্চুরি দুটোকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। বামপন্থি রাজনীতির অসাধারণ ঐতিহ্য, ত্যাগের কথা স্মরণ করেও বামপন্থি সাহিত্য-বিতর্ক নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, এদেশের বামপন্থিদের নানা জ্ঞান থাকলেও কাণ্ডজ্ঞান নাই। পরে খোঁজ পেয়েছি কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সৃজনশীল লেখক-শিল্পীর কত বিচিত্র দ্বন্দ্বের ব্যাপার ঘটেছে পৃথিবীর নানা দেশেই। কিন্তু নানা স্ববিরোধীতা আর বৈপরীত্য নিয়েও যে জীবন সম্ভাবনাময় সে কথা ভাববার সাহস আমি পেয়েছিলাম ইলিয়াস ভাইয়ের কাছ থেকে। নিজে সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে ধীরে ধীরে টের পেয়েছি রাজনীতি এবং সাহিত্যের মিথস্ক্রিয়াটি জটিল। রাজনীতিবিদের একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য প্রয়োজন, তার কাছে ক্ষমতার প্রশ্নটি জরুরি ফলে তাকে হয় সাদা না-হয় কালো জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়, তাকে স্পষ্ট করে শক্র-মিত্র চিনতে হয়। কিন্তু লেখক তার সমস্ত সংশয়, দ্বিধা নিয়ে জীবনের এক ধূসর এলাকায় দাঁড়িয়ে জীবনের বিপুল বৈপরীত্ব দেখেন। জীবনের নানা স্ববিরোধীতা, সম্ভাবনাকে নির্মোহভাবে দেখাই তার রাজনীতি। কালের যাত্রার পরিবর্তনে সাহিত্যের ভুমিকা মানুষের সংবদেনশীলতার পরিধিটিকে বাড়িয়ে দেয়ার ভেতরেই। সে প্রক্রিয়া জটিল, সুক্ষ্ম।
আমার সাহিত্যযাত্রার সেই শুরুর কালে আরেকটি জট ছিলো পশ্চিমবাংলার সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে। সেসময় অনেক লেখকদেরই দেখতাম পশ্চিমবাংলার সাহিত্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে, ঐ বাংলার লেখক-সাহিত্যিকদের সঙ্গে সস্পর্ক তৈরি করা, সেখানকার পত্রিকায় লেখা ছাপানো, তাদের স্বীকৃতি পাওয়ার ব্যাপারে ছিলো তাদের ব্যাপক উৎসাহ। বলা বাহুল্য, বাংলাভাষার অধিকাংশ শক্তিমান লেখকরা সাহিত্যচর্চা করেছেন পশ্চিম বাংলায়, মূলত কলকাতাকে কেন্দ্র করে। সেখানেই বাংলাসাহিত্য পুষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমার বরাবরই মনে হতো দেশভাগের পর আমাদের এই অঞ্চলের সাহিত্যযাত্রার যে পথ-পরিক্রমা তার পক্ষে কলকাতার দিকে তাকিয়ে থাকার কোনো কারণ নেই। দুই বাংলার একই আকাশ একই বাতাস হলেও নানা সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কারণে আমাদের দুই বাংলার জীবন অভিজ্ঞতার ভেতর একটা বড় ফারাক তৈরি হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে তার প্রতিফলন দরকার। কলকাতার সাহিত্যচর্চার স্বভাবের সাথে তা মিলবে না। লক্ষ্য করেছি ইলিয়াস ভাই তার লেখক জীবনের শুরুর দিকে কলকাতার কল্লোলগোষ্ঠীর কোনো কোনো লেখক দিয়ে প্রভাবিত হয়ে ‘শিল্পের জন্য শিল্প’ ভাবধারার কিছু সাহিত্যচর্চা করলেও ক্রমশ তিনি এই বাংলাদেশ ভূখণ্ডের জীবন-জনপদের নানা চড়াই উৎরাইকে সাহিত্যে ধরবার ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। কলকাতার বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও তিনি স্পষ্টতই মেনে নিয়েছেন যে, এই বাংলাদেশের জনপদের একটা নিজস্ব জীবন, ভাষা, বৈচিত্র আছে এবং সেটিকে সাহিত্যে তুলে আনা জরুরি। তিনি তার লেখায় মুক্তিযুদ্ধ, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, এবং সাতচল্লিশের দেশভাগের সময়ে এই পূর্ববাংলা অঞ্চলের মানুষের ভিন্নতর অভিজ্ঞতার উপর আলো ফেলবার চেষ্টা করেছেন। তিনি তার লেখায় তুলে এনেছেন পুরান ঢাকার কিংবা বগুড়া অঞ্চলের ভাষাভঙ্গি। বাঙালির নানা ধর্মের মিলিত জীবনের সাহিত্যে তুলে এনেছেন তিনি এবং অনেক ক্ষেত্রেই জোর দিয়েছেন বাঙালি মুসলমানের উপক্ষিত জীবনের বয়ান তৈরিতে। তবে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য নামে বাড়তি সুবিধার কোনো ক্যাটাগরিতে বিশ্বাস করতেন না তিনি। ইলিয়াস ভাই তার ডায়েরির ১৯৭০-এর ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে এক কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখছেন—‘বাংলা কবিতায় নজরুল ইসলাম, সঙ্গীতে আলাউদ্দীন খাঁ ও আব্বাসউদ্দীন, নৃত্যকলায় বুলবুল চৌধুরী ও চিত্রকলায় জয়নুল আবেদিনের আবির্ভাব ঘটে পকিস্তান হওয়ার আগেই। এমনকি বাঙলার রাজনীতিতে ফজলুল হকের প্রভাব বিস্তার ১৯১৬-১৭ সাল থেকেই শুরু হয়েছে। হিন্দু আধিপত্য মুসলমান সাংস্কৃতিক বিকাশের পথে অন্তরায় একথা ঠিক নয়, তার প্রমাণ এদের সাফল্যেই বোঝা যায়… এই আসন কেউ তাদের দয়া করে দান করেনি, কিংবা কোনো অগ্রসর সম্প্রদায়ের উদর মনোভাবের কল্যাণে তারা এই প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি, এই মর্যাদা তারা অর্জন করেছিলেন নিজেদের প্রতিভা এবং কৃতিত্বের সাহায্যেই…বাংলা গদ্যেও বাঙ্গালি মুসলমানের মর্যাদা অর্জন খুব সাম্প্রতিক নয়। মীর মশাররফ হোসেন তো খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবদ্দশাতেই।’ মোটকথা ইলিয়াস ভাই কোনো বঞ্চিতের বোধ নিয়ে সাহিত্যচর্চা করতেন না, কলকাতার সাহিত্য সমাজের প্রশ্রয়ের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই নিরাসক্ত। কলকাতার সাথে তার বিশেষ কোনো যোগাযোগও ছিলো না। তার সেই পায়ের চিকিৎসা করতে যাওয়ার আগে তিনি কলকাতায় কোনোদিন যানওনি। আড্ডায় বলতেন, কলকাতার লেখকরা তাদের কাজ করছেন আমাদের কাজটা আমাদেরই করতে হবে। কাজে কাজে কথা হবে। হয়েছিলোও তাই। কলকাতার সাহিত্য সমাজ খুঁজে নিয়েছেন তার কাজ। ইলিয়াস ভাইকে আনন্দ পুরস্কার দিয়েছেন তারা, তার নামে মঞ্চ হয়েছে কলকাতা বইমেলায়। সেখানকার প্রকাশক নিজ উদ্যোগে এসে বই প্রকাশ করেছেন তার। ইলিয়াস ভাইয়ের এই স্থানিক বাস্তবতার প্রতি আত্মবিশ্বাস অনুপ্রাণিত করতো আমাকে।

শেষ জটটি সাহিত্যিক জীবনচর্চা বিষয়ে। কেমন হবে লেখকের জীবন এ নিয়ে নানা ভাবনার দোলচাল ছিলো তখন? একজন প্র্যাকটিসিং লেখককে চোখের সামনে দেখে দীক্ষা পেয়েছি নানা মাত্রাতেই। ইলিয়াস ভাই আড্ডায় মজা করে বলতেন, আমার রক্তের গ্রুপ ‘পি’ অর্থাৎ পোয়েট। অন্যের রক্তের সাথে মিলবে না। বলতেন লেখকদের রক্ত আলাদা কিন্তু তাই বলে লেখকদের জন্য জীবনের একটা সিংহাসন তিনি দাবি করতেন না। লেখক হয়েছেন বলে তার যাবতীয় বেপরোয়া জীবনযাপনের লাইসেন্স আছে তিনি তা মনে করতেন না। তিনি মনে করতেন জীবনের অনেক গুরত্বপূর্ণ কাজের মতো লেখাও একটা কাজ। আর লেখা দাবি করে ব্যাপক শ্রম আর নিষ্ঠা। যে নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি শিক্ষকতা করতেন সেই নিষ্ঠার সাথে লিখতেন। সাহিত্যিক দলাদলিতে তার কোনো আগ্রহ ছিলো না। ডায়েরি সম্পাদনা করতে গিয়ে দেখেছি তার সমসময়ের দলবাজ লেখকদের নিয়ে তার তীব্র ক্ষোভ। নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডায়েরির সেই অংশগুলো আমি ছাপাইনি। ইলিয়াস ভাই প্রথম জীবনে সাহিত্যিকদের সাথে প্রচুর আড্ডা দিলেও পরবর্তীকালে দেখেছি তার বাসায় যাদের সাথে তিনি সময় কাটাতেন তাদের অধিকাংশই কোনো লেখক-সাহিত্যিক নন। দেখতাম তিনি তার সব লেখার অনুমোদন নিতেন তার বন্ধু মাহবুবুল আলম জিনুর কাছ থেকে, সাহিত্যজগতে যার কোনো পরিচিতিই নেই। জিনু ভাইকে তিনি তার ‘খোয়াবনামা‘ উৎসর্গ করেছিলেন। লেখক শিবিরের সাথে যুক্ত ছিলেন একধরনের সামাজিক অঙ্গীকার থেকে। সেই সংগঠনের সংশ্লিষ্টরা অধিকাংশ রাজনীতি অঙ্গনেরই মানুষ। লিখতেন খুব নিয়ম মেনে। অনেকসময় হয়েছে ফোন দিয়ে আড্ডা দিতে আসতে চেয়েছি তিনি বলেছেন আজ একটা চ্যাপ্টার লেখা শেষ করতে হবে, কাল এসো। তারপর যখন গেছি আড্ডা দিয়েছন প্রাণ খুলে। জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে আগ্রহ ছিলো ইলিয়াস ভাইয়ের। মার্ক্সের প্রিয় একটা উদ্ধৃতি প্রায়ই দিতেন, সম্ভবত এক প্রাচীন রোমান কবির কথা—‘নাথিং হিউম্যান ইজ এ্যালিয়েন টু মি।’ রাজনীতি থেকে যৌনতা সব বিষয়ে কথা হতো তার সঙ্গে। নিজের জীবনযাপন, তার বৈপরীত্ব নিয়ে অকপট ছিলেন। ঢাকা শহরে নিজের কোনো বাড়ি ছিলো না ইলিয়াস ভাইয়ের, থাকতেন ভাড়া বাড়িতে, চলাফেরা করতেন পাবলিক বাসে, তার সঙ্গে পাবলিক বাসে চলাফেরার অনেক মজাদার স্মৃতি আছে আমার। খুব সাদামাটা জীবনযাপন করলেও বিলাতীদের মতো পাইপ টানতেন, লিখতেন টাইপরাইটারে। এসব ছিলো তার শখ। অথচ সেই পাইপটানা মানুষটিকে গোবিন্দগঞ্জের হাটে যখন এক গরুর ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ করতে দেখেছি মনে হয়েছে যেন তারা কতকালের আপনজন। পরিষ্কার মন ছিলো তার, অপার কৌতুহল ছিলো মানুষের ব্যাপারে। আমি তখন মুক্তাগাছায় এক গ্রামীণ স্বাস্থ্যপ্রকল্পে ডাক্তার হিসেবে কাজ করছি, তিনি একবার ঢাকা থেকে এসে রাতে থেকে গেলেন আমার ওখানে। আড্ডা দিতে দিতে মাঝরাত হলো। আমার থাকবার জায়গার পাশেই এক মফস্বলী সিনেমা হল। আমাদের কথার ফাঁকেই শুনলাম মানুষের কোলাহল। সিনেমার নয়টা বারোটার নাইট-শো শেষ হয়েছে তখন। ইলিয়াস ভাই হঠাৎ বললেন চলো সিনেমা ফেরতা মানুষগুলোর সাথে একটু আড্ডা দেই। আমরা হলের পাশের এক চা স্টলে গিয়ে বসলাম। কোনো এক ঢাকাই ছবি চলছে তখন। মাঝরাতে চা খেতে খেতে শো-ভাঙা লোকগুলোর সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন সিনেমার গল্প। তারপর ঘরে ফিরে অনেক রাত অবধি আমরা আড্ডা দিলাম পপুলার কালচার আর জনমানসের মানসগঠন নিয়ে।
ইলিয়াস ভাই প্রায়ই বলতেন আমি বোধহয় খুব বুদ্ধিমান মানুষ না, কারণ বুদ্ধিমান মানুষেরা অবাক হয় না। অথচ আমি প্রতি পদে পদে অবাক হই। ইলিয়াস ভাইয়ের সান্নিধ্য থেকে টের পেয়েছি লেখকের কাজ বোকা বোকা চোখে জীবনের দিকে বরাবর এই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা। এই বিশ্বয়বোধ ইলিয়াস ভাইকে আশ্চর্য এক নিরহঙ্কার আর বিনয়ী মানুষ করে রেখেছিলো আজীবন। তার ডায়রির সেই পৃষ্ঠাটা আমি পড়ি মাঝে মাঝে যেখানে তার ৩৩ বছরের জন্মদিনের পাতায় তিনি স্মরণ করছেন যিশুকে। যিশু এই ৩৩ বছর বয়সে এসেই ঈশ্বরকে বলেছিলেন তার কর্তব্য সাঙ্গ হয়েছে এবার ঈশ্বর যেন তাকে তুলে নিয়ে জগতের এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেন। ইলিয়াস ভাবছেন সে তুলনায় ৩৩ বছরে তার অর্জন কী অকিঞ্চিতকর, তার জীবন কী তুচ্ছ। তিনি লিখছেন:
‘This caricature of an artist was born tired and he is exhausted since his normal and so called legitimate birth on 12Feb 1943. The bugger is now married and a father and a writer of no fame or authority. And he is yet to start his life. How does he justify his existence? Or does he have any?’