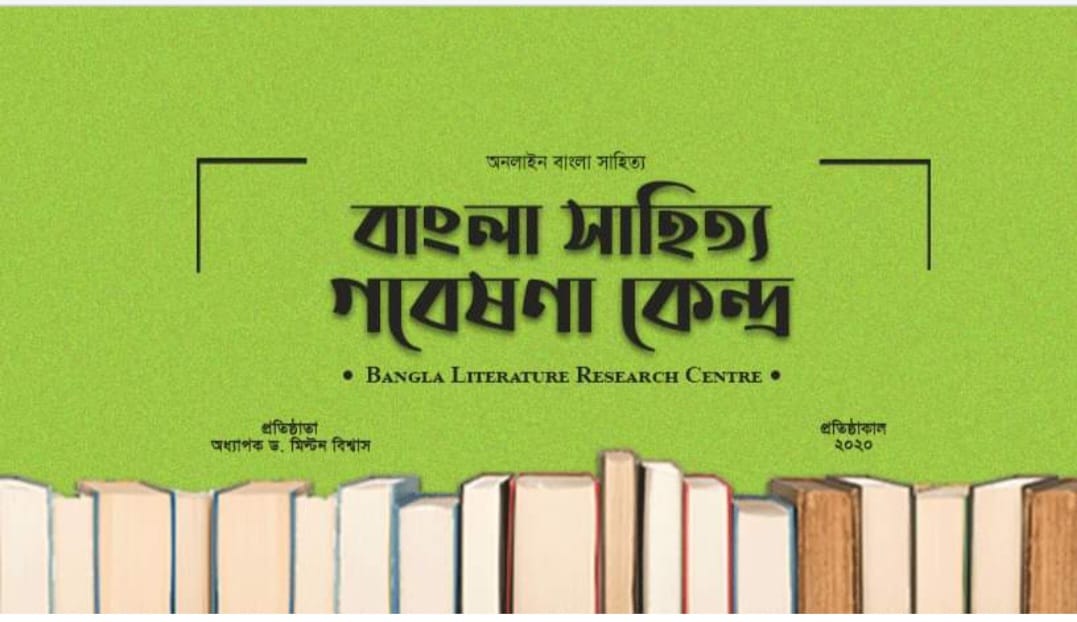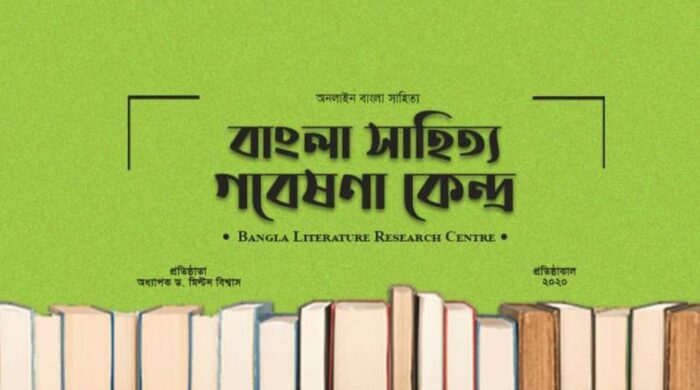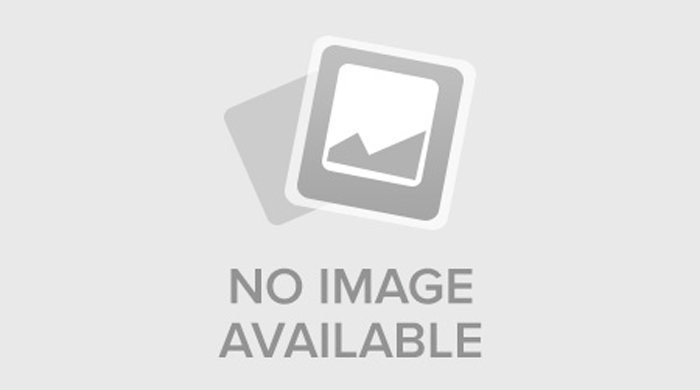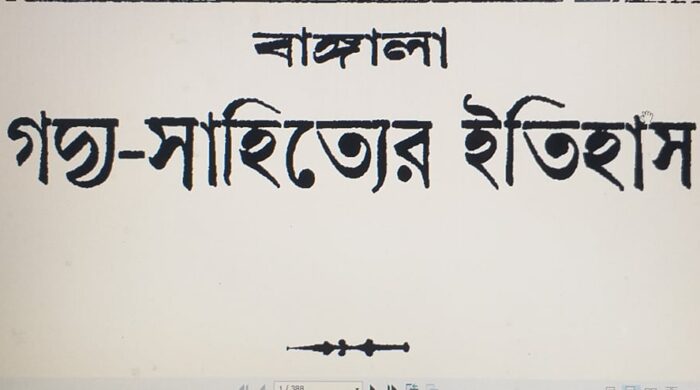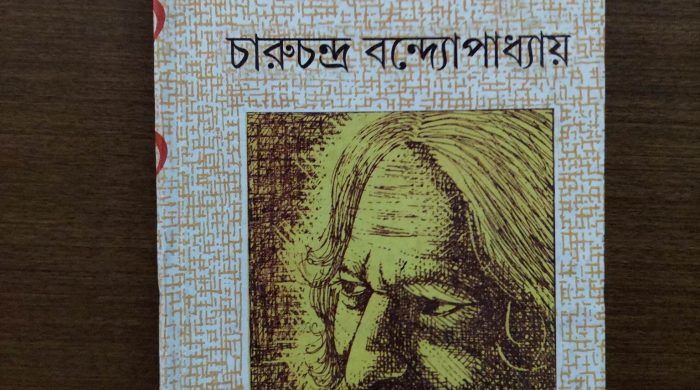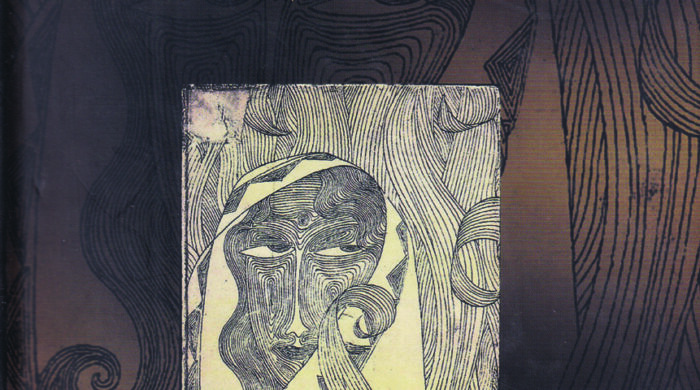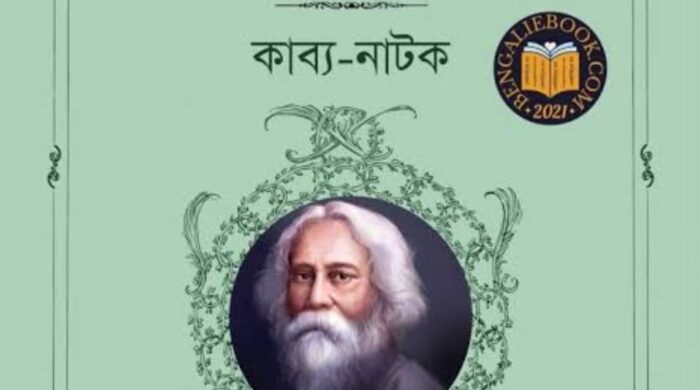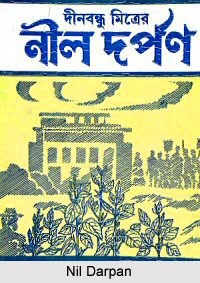সময়টা ঊনবিংশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের প্রথম অর্ধেক ধরে নিলে ওঁকে নিয়ে কথা বলতে সুবিধে বেশি। কারণ এই সময়টাই রবীন্দ্রনাথের জীবনকাল আর বলা বাহুল্য সৃষ্টির কাল।এখন আমরা সেই সময়টা থেকে অনেকটাই দূরে। বড়ো বেশি নৈকট্য একটা বাধা সৃষ্টি করে, ঠিক চোখের ওপরেই উত্তুঙ্গ পর্বত থাকলে কিছু ঠাহর করা যায় না। অনেকটা দূরে না গেলে আর দূর থেকে কাছে না এলে ঠিক দেখাটা হয় না। অতি স্পষ্টতা দেখায় বিঘ্ন ঘটায়- যেমন করে বারবার ঘটিয়েছিল কবির জীবনকালে। তবে অতি-প্রত্যক্ষতার আলাদা একটা আলো আছে, সেটার সাথে সমঝোতা করা কঠিন। বারবার চোখ কচলাতে হয় আর যা ঘটছে, ঘটে গেল এইটুকুই দেখা হয়, জানা হয়। পরে কি ঘটবে তা-ও একটু আন্দাজ করা যায়; কিন্তু তারপর সময় পার হয়ে গেলে কি ঘটল তা দেখার সুযোগ হয় না। বলতেই হবে প্রত্যক্ষতার কোনো বিকল্প থাকুক না থাকুক, যে সূর্য জ্বলছে, যে তারা ফুটে আছে, যে চাঁদ জ্যোৎস্না ঢালছে, যে কালবৈশাখী বিশাল মহীরুহ উৎপাটন করে ফেলল, এসবের প্রত্যক্ষতার তুলনায় এদের স্মৃতি কত ম্লান। এ যেন একদা যে টাটকা গোলাপের সুঘ্রাণ নিয়েছি, সেই সুঘ্রাণের স্মৃতি মনে জাগানোর চেষ্টার মতো। পূর্ব ইউরোপের কোনো এক দেশে বৃক্ষরোপণের সময় রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখে এসেছিলেন, ‘ভালোবেসেছিল কবি, বেঁচে ছিল যবে।’ নিজের সম্বন্ধে অন্তত এইটুকুই বলার ছিল তাঁর। সত্যি করেই এইরকম করে একটুখানি কিছু বলা ছাড়া স্বল্প বা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার বাইরে চলে গেলে আর কি-ই বা ভবিষ্যতের কাছে গচ্ছিত রাখা যায়?
কি জানি, বোধহয় এইভাবেই দেখি বলে মূল্যায়ন, নতুন নতুন মূল্যায়ন, পাল্লা দিয়ে মাপা স্থায়ীমূল্য নির্ণয় করা, কালের বিচার, বিচারক মহাকাল এইসব গৎ-বাঁধা কথার ওপর আমার স্থির আস্থা নেই। এতে সবচেয়ে গোলমেলে ব্যাপারটা ঘটে অন্যের মুখে ঝাল খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকা। এরকম করে ঝাল খাওয়ানোর জন্য সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন সমালোচকবৃন্দ নিজের নিজের ভা- হাতে নিয়ে। কবির সমকালে যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁকে শুনেছিলেন, পড়েছিলেন সে তো বেশির ভাগ স্বেদ-শ্রম-রণরক্তে ভরা বা অথৈ ক্ষীরের সমুদ্র। শেষ পর্যন্ত এই কথাটা কি একটা প্রায় প্রতিক্রিয়াশীল কথায় দাঁড়ায় যে সৃষ্টির কাজ যেমন একা আর নির্জন, তার ভোগ-ভোগান্তি উপভোগও তেমনি একার? এ সিদ্ধান্ত গুরুতর এবং নিষ্ঠুরভাবে বিশ্লেষণযোগ্য জানি! কথাটা তুলেই আমি ক্ষান্ত হচ্ছি।
ইচ্ছে করেই এ বক্তৃতার শিরোনাম রাখা হয়েছে সীমানাবিহীন। তাতে ইচ্ছেমতো যেমন খুশি যা খুশি, কোনো একটা কথা বা বিষয় নির্দিষ্ট করে নিয়ে কোনো প্রসঙ্গের বিশেষ প্রসঙ্গের রাস্তা ধরা যাবে। দেখাই যাচ্ছে কবির বর্তমানের সুবিধে আমরা পাচ্ছি না। উনিশ শতকের শেষভাগ কবে পেছনে ফেলে এসেছি, বিশ শতকের প্রথম ভাগও এখন অতীতের ধুলোয় ধূসর। শুধু তাঁর জীবনকালের হিশেব নয়- তাঁর মৃত্যুর পরেও তো কেটে গেল প্রায় পৌনে এক শতক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি গানে লিখেছিলেন, লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি হারিয়ে গিয়েছে তোমার আখরগুলি। কিন্তু দেখুন অশোকের শিলালেখগুলি আজও হারায়নি। সবই যে হারায় তা তো নয়, যা হারায় না তার সবই যে একই রকম তা-ও নয়। আদি মানবের হাতের কাজ গুহার গায়ে আজও রয়ে গেছে, যারা করেছে তারা স্পষ্টতই শিল্প করেনি, সৌন্দর্যকে স্থিররূপ দিতে চায়নি, যাপিত জীবনই এঁকেছে আদিম কোনো এক জাদু-বিশ্বাসে কিন্তু এখন আমাদের কাছে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিরামিডগুলি রয়ে গেছে- সেসবও ঠিক শিল্পকর্ম নয়। তবু এখন তাদের শিল্পস্বরূপ খুঁজতে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।
তাহলে কাকে থাকা বলে, অজর অনশ্বর হওয়া আসলে কী? কথাটা যখন সাহিত্যের কাছে এসে পৌঁছায়, তখন জটিলতা যেন আরো বাড়ে। রবীন্দ্রনাথ অমর প্রতিভা, মৃত্যুহীন সৃষ্টির স্রষ্টা- একথায় কেউ আপত্তি হয়ত করবে না কিন্তু কেমন সেই অমরত্ব, কেমন করে কালজয়ী? অত জোরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের থাকা না-থাকা নিয়ে কথা বলি কেমন করে? শুধু যে শিলালেখই থাকে তাই নয়- লেখার জন্যে যে শিলাখ- তৈরি করা হয়েছিল পরে আর তাতে লেখা হয়নি, তেমন শিলাখ-টিও থেকে গেছে। এদের একটা কিছু বলে, অন্যটা বোবা। তবে চিরদৃশ্যমানগুলির থাকাটাই আমাদের মনোযোগ দখল করে বেশি যদি তারা মানুষের হাতের গভীর দাগে দাগি হয়ে যায়। সেগুলি চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদি কতভাবে যে ভাগ হয়ে যায় তার অন্ত নেই। মানুষের হাতে তৈরি হয়েই যে আণবিক বোমায় হিরোশিমা নাগাসাকি কয়েক মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে গেল বা হিটলার আউশভিৎসে যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে জ্বালিয়ে অঙ্গার করে দিলেন এরকম মানুষকৃত কর্মও কম স্থায়ী নয়। এইসবকেই তো ইতিহাস বলে, সেজন্যে শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা গিয়ে ঠেকে খোদ ইতিহাসকে নিয়েই।
তাহলে চট্জলদি যে জিজ্ঞাসাগুলি তোলা হয়, অমুক মহাশিল্পী অমরত্বের চিরস্থায়ী আসন পাবেন কিনা, এই কাব্য মহাকালের অংশ হিশেবে বিবেচিত কেন হবে না, চরম বিদ্বেষবাদী মানুষটিও কালের অচ্ছেদ্য হয়ে গেলেন কিনা তখন এই প্রশ্নগুলি তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব হারায় না বটে তবে তখন না প্রশ্নগুলি না উত্তরগুলি সত্যিকার অর্থে জীবিত থাকে, না পারে তারা জীবিতদের সরাসরি সম্বোধন করতে। এই একই সূত্রে এখন বলি রবীন্দ্রনাথও চিরজীবিতদের দলভুক্ত এই সরল নির্দ্বিধ স্বীকৃতি কিন্তু জটিল হয়ে ওঠে। তার জন্য বহু ব্যাখ্যার দরকার হয়ে পড়ে, চিরজীবিত থাকার অর্থটাকে বার বার পরখ করে নেওয়ার কথাও চলে আসে। কথাটা এই নয় যে রবীন্দ্রনাথের অমরত্বের স্বীকৃতিতে কোনো প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, কথাটা এই, কোন্ তীব্র নির্দিষ্ট সজাগতা থেকে এই প্রশ্ন করা হচ্ছে। কে অস্বীকার করবে যে প্রাচ্যে হোমারের ‘ইলিয়াড’ ও ‘আদিসি’ এবং প্রতীচ্যে ‘মহাভারত’ ও ‘রামায়ণ’ অমর গ্রন্থ, এদের মৃত্যু নেই? এরকম কত যে কাব্য সাহিত্য শিল্প ভাস্কর্য স্থাপত্যের কথা আমরা বলতে পারি তার অন্ত নেই। এদের সবার নামই অমরত্বের পাকা খাতায় সোনার অক্ষরে লেখা আছে। বলতেই পারা যায় মানবজাতির বিলুপ্তি পর্যন্ত। সে সম্ভাবনা যদি থাকে আর হয়ত আছে, মানুষের সৃষ্টি মহাকীর্তিও এই সম্ভাবনার সীমানার মধ্যেই থেকে যাবে। একজন ভার্জিলের ঈনীড, একজন দান্তের ডিভাইনা কমেডি, একজন নাট্যকার শেক্সপিয়রের নাটকগুচ্ছের মৃত্যু নেই। কিন্তু তাদের স্রষ্টারা সবাই সরে পড়েছেন চিরকালের মতো। এমনকি আমাদের নিকট-অতীত, রেওয়াজ অনুযায়ী যা আধুনিক কাল বলে চিহ্নিত, সেখানেও আমরা স্বীকার করে নিই একজন ভাস্কর রদ্যাঁ, একজন ঔপন্যাসিক তলস্তোয়, একজন শিল্পী পিকাসো মৃত্যুঞ্জয়ী স্রষ্টা হিশেবে সকলের কাছে স্বীকৃত হয়েছেন। আর এইসঙ্গে এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলি রবীন্দ্রনাথও তাই। উনিশ-বিশ শতকের রবীন্দ্রনাথ জীবিত থেকেও যদি চিরজীবিতের স্বীকৃতি না পেয়ে থাকেন, অনুপস্থিত সেই কবি আজ একবিংশ শতাব্দীতে অমরত্বের আসনটি পেয়ে গেছেন। আগ বাড়িয়ে কথা বলা আমাদের সকলের অভ্যেস, একবিংশ শতাব্দীর কথা না হয় আমরা বলতেই পারি, এর মধ্যে আমরা রয়েছি, কিন্তু তাঁর অমরত্বের ভবিষ্যদ্ববাণী দ্বাবিংশ, ত্রয়োবিংশ ইত্যাদি ইত্যাদি কালের জন্যও করতে পারব কোন্ আন্দাজ থেকে?

একটু এখন আন্দাজ করার চেষ্টা করা যায় কি প্রক্রিয়ায় ঠিক কি জাতীয় মানবীয় ভাবনা পদ্ধতিতে আমরা ইতিমধ্যে উল্লিখিত তকমাগুলি নির্দিষ্ট কিছু স্রষ্টার জন্য স্থির করে দিয়েছি? কোন্ ভরসায়? কে মানবে? কতজন মানবে? কতকাল মানবে? কেনই বা মানবে? গড়পড়তা যে বিবেচনা, যে মূল্যারোপে অভ্যস্ত থেকে, মনুষ্যসৃষ্টি সম্বন্ধে ঐকমত্যে পৌঁছানো গেছে ভেবে নিয়ে স্রষ্টাদের আসন বণ্টন করে দিয়েছি সেগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী অন্তরে সময়ের নির্দয় ধ্বংসকা-, পরিবর্জন আর ভাঙচুরের মধ্যে অটুট কি থাকবে? এই প্রশ্নের জবাব নেই। আমরা বর্তমানের দিকে চেয়েই কাজ করি- অস্তিত্বের জীবন্ত বিবেচনার বাইরে যাবার কোনো উপায় আমাদের নেই। প্রকারান্তরে আমাদের এই বর্তমানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কি তাই? পরিবার সমাজ সংস্কৃতি রাষ্ট্র সমাজ ও রাষ্ট্র এই একই কথা দাঁড়াবে যে মানুষ তার অতীতটাকে, অতিক্রান্ত সময়টিকে খুঁজতে থাকবে, তার নাম দেবে উত্তরাধিকার, তাকে বলবে মহান সম্পদ, ঐতিহ্য ইত্যাদি ইত্যাদি এবং তার হিশেবে মহার্ঘ যা কিছুই পাবে বা মহার্ঘ মহামূল্যবান বলে ধরে নেবে তাকেই একটা চন্দনকাঠের সিন্দুকে ভরে রাখবে। বাবার সোনার পুত্র-পৌত্ররা ঘড়িটা রাখে, অন্যের কাছে তার তার মূল্য কি হতে পারে চিন্তাও করে না। বধূ রাখে তার শাশুড়ির ভারি ভারি পুরনো গহনা, পুরনো বেনারসি এইসব। এগুলিকে চিরস্থায়ী ভাবে আর সবাই তাই ভাবতে ইচ্ছে করে। এক একবার আমার মনে হয় সব সভ্যতার এইরকম একটা করে চন্দনকাঠের সিন্দুক থাকে। গোটা সভ্যতা যা সাধারণভাবে মানুষের সভ্যতা হিশেবেই ধরি আর আলাদা আলাদা বা নানান বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা কিংবা রাষ্ট্র বা সমাজ হিশেবেই ধরি আমাদের সমস্ত মহার্ঘ সম্পদ রাখার জন্য আমরা সিন্দুক তৈরি করবই। ভারতবর্ষ রামায়ণ মহাভারত রাখবেই সেখানে, গ্রিকরা ইলিয়াড আদিসি রাখবে, ইতালীয়রা ভার্জিল দান্তে রাখবে। যাদের এইরকম কোনো সিন্দুক নেই তারাই পৃথিবীর জাতিপুঞ্জে রাষ্ট্রপুঞ্জে হতভাগ্য, করুণার পাত্র। এই কথার সঙ্গে একথাটাও সহজে যায় যে গোটা মানবজাতি এর অংশভাক্- সেখানে ভাগাভাগি করা সংকীর্ণতা। এই উত্তরাধিকার সমগ্র মানবজাতির এটা বলাই চলে।
অস্বীকার করা যাবে না যে এসব সিন্দুক কেউ প্রত্যেকদিন খোলে না। কিছুতেই তাতে প্রাত্যহিকতার দাগ লাগতে দেয় না। হয়ত মাঝে মাঝে বের করে ঝাড়পোঁছ করে, হাত দিয়ে স্পর্শ করে, বুঁদ হয়ে থাকে অপার্থিব কোনো সৌন্দর্যে, সৌগন্ধে। কিন্তু কিছুতেই তাকে নিত্যব্যবহার্যের মধ্যে আনতে চায় না। তাদের কাছে যাবার জন্য নানা উপলক্ষের অপেক্ষা করে থাকে।
এখন আমরাও রবীন্দ্রনাথের জন্য একটা সুবাসিত চন্দনকাঠের সিন্দুক বানাব কি, আর সেটাকে কুক্ষিগত করে রাখব না, পৃথিবীর হাটে ফিরি করে বেড়াব। এই একবিংশ শতাব্দীতে আমরা আর কি করব। কিন্তু ইতিমধ্যে কি অনেকটাই দেরি হয়ে যায়নি? এই বর্তমানের পৃথিবী কি এতটাই বদলে যায়নি যে অন্য অনেক কিছু নিয়ে দরজায় দরজায় ফিরি করতে আমাদের বাধ্য হতে হচ্ছে? রবীন্দ্রনাথ নিয়ে নয় কি? এই সময়কার হাটে তিনি বিকোবেন কি? সারা পৃথিবীর কথা দূরে থাক, নিজের দেশেই এখন ‘তোমারই নাম বলব, বলব নানা ছলে’ গাইতে গাইতে রবীন্দ্রনাথকে গাও, তাকে হৃদয়-মনে গ্রহণ করো বলে ফিরি করে বেড়ালেই কি খুব কাজ হবে? কি মনে হয় আপনাদের? যে প্রত্যক্ষতা, সমকালীনতার, জাজ্বল্যমান শারীরিক উপস্থিতির কথা বলেছিলাম- উনিশ শতকের শেষ, বিশ শতকের প্রথম ভাগ- আজ আর তা নেই। এখন আর তাঁকে সরাসরি ডেকে আনার উপায় নেই। এখন একটা সত্য উচ্চারণ করতে হবে : উপস্থিত রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনুপস্থিত রবীন্দ্রনাথের শক্তি বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে, উপস্থিতির দৈনন্দিন বাদ প্রতিবাদ, ক্লেদ গ্লানি, স্তুতি ভক্তি প্রশংসা, কঠিন বিদ্বেষ কিছুই আর এখন প্রত্যক্ষ নয়- যা পড়ে আছে তা হলো রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। সত্যিই সেটা কি সিন্দুকেই তোলা আছে? বিপদ তো সেখানেই। যা সিন্দুকে তোলা থাকে তাকে নিত্য ব্যবহারের কাজে লাগে না- তার পরশ মেলে না, সে কিছুতেই মনে মস্তিষ্কে কাজ করে না। তাঁর ঐ গানটাই আর গাইতে পারি না : ‘তোমার কাছে এ বর মাগি মরণ হতে যেন জাগি।’ আমরা তন্দ্রাহীন চোখে জ্বলতে জ্বলতে ঘুমিয়েই থাকি। এই কথাটাকে অভিযোগ হিশেবে নিলে কয়েকটি কথা বলাই যায়- এক. ব্যবহৃত হতে হতে এতই পুরনো হয়ে গেছে যে আর ব্যবহার যোগ্য নেই; দুই. কোনোদিন ব্যবহার যোগ্য ছিলই না, মহার্ঘ জিনিশের মতো তা চিরকাল তুলে রাখারই জিনিশ। তিন. ব্যবহারযোগ্য ছিল, যতদিন তা ছিল ব্যবহার করা হয়েছে, এখন তার প্রয়োজন নেই। এসব কথা বলার পরও অমরত্বের তকমা তাঁকে দেওয়া যায়, দিচ্ছি, বলা যায়, রবীন্দ্রসাহিত্য আজ চিরকালের বিশ্বসাহিত্যের অংশ।
এই কথাটা বললে একটা কিছু বুঝি। অন্তত কবিগুরু, বিশ্বকবি, কবি সার্বভৌম বললে যা বুঝি তার চেয়ে খানিকটা বেশিই বুঝি কিন্তু খুব তেমন নির্দিষ্ট কিছু নয়, অন্তত তাঁর জন্মের দেড় শ বছর, আর মৃত্যুর প্রায় পৌনে একশতক পরে। এরকম করে বহু শব্দ, বহু বাক্যবন্ধের অর্থ ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। তবু আমরা যে সব শব্দ বা বাণী কিছুতেই ছাড়ি না, আঁকড়ে ধরে থাকি, আর এঁদের কারো সম্মুখীন হতে ভয় পাই, তখন সেই ভয় অস্বীকার করার জন্য প্রাণপণে এই শব্দগুলোকেই অবলম্বন করে থাকি। শুধু রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই তো এমন নয়, অমরশ্রেণি চিহ্নিতদের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে উটপাখির মতো তাঁদের আড়ালে মুখ গুঁজে থাকাই স্বস্তিকর। একবিংশ শতাব্দীতে এসে রবীন্দ্রনাথের পরিণাম কি এই জায়গায় এসে দাঁড়াল? গত দু-বছর ধরে রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষ জন্মবার্ষিকী পৃথিবী জুড়ে উদ্যাপনের কথা ভাবুন। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে তরুণ রবীন্দ্রনাথ যখন সৃষ্টির কাজে ঢুকে পড়েন, কবিতা লিখতে থাকেন, গান রচনা করতে এবং গাইতে শুরু করেন, অবিশ্রান্ত গদ্য-ভ্রমণ ডায়েরি বা উপন্যাস রচনায় নিমগ্ন হয়ে যান, লিখতে থাকেন ছোটোগল্প, তখন তিনি নবীন, তাঁর দৃষ্টিও নবীন আর নবীন চোখে দেখা তাঁর চারপাশের পৃথিবীটাও নতুন। অথচ চিরকালের মতোই পৃথিবী একই সঙ্গে যেমন লম্বা পা ফেলছে সামনের দিকে, হাজার লক্ষ লুকানো সম্ভাবনা বাস্তবে দেখা দিচ্ছে, তেমনি ঠিক একইসঙ্গে সে ক্লান্ত শ্রান্ত হৃতসর্বস্ব, ভারবহনে অক্ষম, অন্ধকারে অন্ধকারে দৃষ্টিহীনও হচ্ছে বই কি! স্বতন্ত্র বিচিত্র স্ব-স্বভাববিশিষ্ট ইতিহাস সব সভ্যতার, সব জাতি রাষ্ট্র ধর্মেরই আছে, আর তা থেকেই যাবে কিন্তু সাধারণভাবে অস্বীকার করা যায় না যে য়োরোপে শিল্প বিপ্লবের পরে অন্তত গত তিন শ বছর পশ্চিম পৃথিবীই গোটা পৃথিবীর নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রবল শক্তিতেই পশ্চিম পৃথিবী তার দিকে এই দৃষ্টি ফেরানোটা ঘটিয়ে ফেলেছে। এই কথাটা নিয়ে দীর্ঘ অন্তহীন আলোচনায় লিপ্ত হওয়া যায় কিন্তু এখানে আমি নিজেকে ক্ষ্যামা দিচ্ছি আর কথাটাকে স্বীকার্য আপ্তবাক্য বলেই মেনে নিচ্ছি। প্রাসঙ্গিকতা, প্রত্যক্ষতা কি আর তার জোরই বা কতটা এটা খুঁজে দেখাই আসলে সৃষ্টির কাজের সবচেয়ে জীবন্ত ব্যাখ্যা। রবীন্দ্রনাথের সামনে উনিশ শতকের শেষভাগের পৃথিবী, আর প্রায় সওয়া একশ বছরের উপনিবেশ ভারতবর্ষ। তখনো পর্যন্ত পৃথিবীজুড়ে ইংরেজ উপনিবেশ অটুট, বেশ সুস্থিত অবস্থায় রয়েছে। সিপাহি বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ পেরিয়ে ভারত কোম্পানি রাজ ছাড়িয়ে মহারানি ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের পিছনের পশ্চাৎপট-টা এইরকম। এখান থেকেই তাঁর লেখা শুরু।
কিন্তু য়োরোপে শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই দেখা দিতে শুরু করেছে মৃদু অস্বস্তি। কালের অজুহাতে বহু তফাত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে যখন বলা হয় উনিশ-শেষ আর বিশ-প্রথম শতকের লেখক রবীন্দ্রনাথ, তখন কিন্তু খুব বড়ো ধরনের ভুল করার সম্ভাবনা থেকে যায়। অথচ আমরা অবলীলায় য়োরোপের দিকে চেয়ে সম্ভবত য়োরোপীয় চোখ দিয়েই উনিশ শতকের সাহিত্যের কথা আর একই অভ্যেস থেকে বিশ শতকের সাহিত্যের কথাও বলি একটি কল্পিত বিশ্বসাহিত্যের সমগ্রতার কথা ভেবে নিয়ে। এইরকম করে করেই হয়ত বাধ্যতই আমাদের সাহিত্য বিচারেরর দৃষ্টি মানদ- সবই য়োরোপীয় হয়ে গেছে। বাধ্যতই বলছি বাধ্য হয়েই- আমাদের রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজচিন্তা, শিল্পচিন্তা, দর্শনভাবনা সেই উনিশ শতক থেকেই য়োরোপীয়, বিশেষ করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানিকেন্দ্রিক হয়ে যায়নি কি? নিজের ভাষার চেয়ে পরভাষার ওপর নির্ভরতা বেড়ে যায়নি কি? বাংলা গদ্য ভাষারই জন্ম বিকাশ বৃদ্ধি উপনিবেশি কালের সঙ্গে সমান-বয়েসি নয় কি? আভিজাত্য, শক্তি শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে ভাষা একাকার হয়ে যায়নি কি? রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এসবের কোনো দাগ পড়বে না তেমন আশা করা যায় না। কিন্তু বাস্তবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও অনেকটা তা-ই ঘটতে দেখা যায়। উনিশ শতকীয় মানবতাবাদ, ইহজাগতিকতা বুদ্ধিবাদিতা নতুন সমাজ, নতুন ব্যক্তি, নতুন বোধ আদর্শ ও লক্ষ্য বলে গৃহীত হয়ে যায়নি কি? এ সবই উপনিবেশকালেই অর্জিত। যে সমাজ থেকে এসব উঠে এসেছে তা ভিন্ন, সাধারণভাবে য়োরোপীয়, বিশেষভাবে উপনিবেশের মালিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্জ্যজাত। ঐ সাম্রাজ্জ্যের মালিকের দেশটির দিকে নজর দিলে কিন্তু তারও ভিন্নতর একটা চেহারা বেরিয়ে আসে যা আর কৃষিপ্রধান, গ্রামীণ শিল্পপ্রধান, সামন্ততান্ত্রিক ইংল্যান্ড নয়। শ্রম আর ভূমিমালিকের ভূমির সঙ্গে বাঁধা-পড়া মোটামুটি সতের শতক আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বজায় ছিল। বণিকতন্ত্র পুঁজিতন্ত্রে রূপান্তরিত হতে থাকে- শিল্পবিপ্লব একরকম সু-সম্পন্নই হয়ে যায়। ইংল্যান্ডের জনগণের বড়ো একটা অংশ ভূমিবন্ধন থেকে ছাড়া পেয়ে কলকারখানায় পরিপূর্ণ নগরগুলির দিকে ধেয়ে আসে। তারা স্বাধীন হয়, মানে শ্রম মুক্ত হয়, শ্রম বিক্রয়যোগ্য পণ্যে রূপ নিয়ে পণ্যনির্মাণেই নিযুক্ত হয়ে যায় যা ভারতে ঘটার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। তাই উনিশ শতকের শেষে ইংল্যান্ডের সমাজই বিষিয়ে উঠতে থাকে। কলকারখানাগুলি উপচে ওঠে ভূমিচ্ছিন্ন শ্রম বিক্রি করতে আসা মানুষে- শ্রমের অতি প্রাপ্যতায় তার দর কমতে থাকে- শ্রমিক বস্তিতে বস্তিতে শহরগুলো ঘেরাও হয়ে যায়, অসুস্থ নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি হয়- আর এইসব মানুষ গৃহ শিক্ষা চিকিৎসা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হতে থাকে। ইতিহাসের ধারাটাই তাই। নতুন সমাজের জন্ম হয়, সে বড়ো হতে থাকে, তার শ্রীবৃদ্ধি-সংকট ঘটে, অসুখ হয়, একসময় তার নাভিশ্বাস ওঠে। উনিশ শতকের প্রথমদিকে যে ইংল্যান্ড তা শতাব্দীর শেষপাদে পৌঁছে তীব্র সংকটেই পড়ে। এই সময়কার প্রধান লেখকদের রচনায় এর প্রমাণ মেলে। কীট্স শেলী ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে ইংল্যান্ড দেখেছিলেন হার্ডি তেমন দেখেননি, ডিকেন্স তো নয়ই। গৌরবম-িত রোমান্টিক পিরিয়ড আর অক্সিজেন পাচ্ছে না বাতাস থেকে, ইঞ্জিনের ধোঁয়া, কলকারখানার ধোঁয়া ততদিনে বাতাস দূষিত করে তুলেছে। আমার মনে হয় সলিটারি রীপার, দ্য ড্যাফোডিলস্ বা উই আর সেভেন-এর মতো কবিতা বা এমনকি কীট্স শেলীর ওড্ টু অ্যান অটাম্ন বা দ্য স্কাইলার্কের মতো কবিতাও শতাব্দীর শেষদিকে লিখিত হওয়া সম্ভব ছিল না। কোলরিজও অসম্ভব। পোয়েট লরিয়েট হলেও টেনিসনও বেমানান। উপন্যাসের বেলায় রোমান্টিক হাওয়া তার একটু আগেই শুকিয়ে যায়! শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বেরুতে শুরু করে ডিকেন্সের উপন্যাসগুলি। লন্ডন শহরটার ভেতর দিয়ে গোটা ইংল্যান্ড দেখা যায়। দেখা যায় সেই বালকটিকে অলিভার টুইস্ট যার নাম- এই ছেলেটির ভিতর দিয়ে শুধু শ্রমজীবী মানুষের জীবনের চেহারাটাই দেখা যায় তা তো নয়- নানাবৃত্তির, নানা পেশার মানুষ, ছোটোবড়ো কলকারখানায় নিযুক্ত শিশু কেমন যে শিক্ষাবঞ্চিত, স্নেহবঞ্চিত কঠিন নিষ্পেষিত বাল্যকাল কাটাচ্ছে তার চেহারাটাও ধরা পড়ে। ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষের জন্যে শিক্ষাব্যবস্থাটা কি ভয়ংকর ভীতিজনক ছিল তার আন্দাজও মেলে। তবে এই লেখকের সেরা লেখা ডেভিড কপারফিল্ড পড়ে ওঠাও কঠিন। আমি তাঁর হার্ড টাইমস বা গ্রেট এক্সপেকটেশন-এর কথাও ভুলি না। দাগি অপরাধীদের জায়গা দিতে চাইছিল না ইংল্যান্ড- এমনকি শাস্তি দেবার জন্যও তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছিল অস্ট্রেলিয়ায়। শিল্প বিপ্লবের ফলে যে পরিবর্তন সমাজে আশীর্বাদের মতো আসে- ব্যক্তির সম্পূর্ণ মুক্তি, তার শারীরিক মুক্তি, সেটাই দেখা দেয় কঠিন বেড়ির বন্ধনের মতো। সমাজ সংসার উচ্ছন্নে যেতে থাকে। চার্লস ডিকেন্সকে আমি তবু রোমান্টিক দৃষ্টিবদলের সাহিত্যিক বলেই জানি। আবেগ ভালোবাসা মমতা করুণা মানবতার চাষ তিনি প্রাণপণে করে গিয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু শতাব্দীর শেষে পৌঁছেই আমরা বুঝতে পারি এবার নতুন কবি লেখক সাহিত্যিক শিল্পী দার্শনিকদের আসতেই হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্জ্যের আকাশের নানা কোণে মেঘ জমতে শুরু করেছে। কিছু উপনিবেশ হাতছাড়া হবার উপক্রম হয়েছে। আশির দশকের প্রথমেই প্রথম বোয়ার যুদ্ধ ঘটে গেল, ট্রাসেভাল প্রিটোরিয়া হাতছাড়া হয়ে যায় প্রায়, শতাব্দীর শেষে বিশ শতকের শুরুতেই দ্বিতীয় বোয়ার যুদ্ধ। তবু যত তাপই শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরে সঞ্চারিত হতে থাকুক না- বাইরে থেকে পুরো শতকটা ঠিকঠাকই মনে হচ্ছিল।
এত অবান্তর কথা আমার এখানে বলা উচিত হলো না বুঝতে পারছি, তবু রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যেসব সূক্ষ্ম সুতোগুলি এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকে কিংবা ছিল, সে সম্বন্ধে আমি নিজে যে আঁচটা পাই, সেটাই আপনাদের কাছে বলা গেল। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে জন্ম-রোমান্টিক ঘোষণা করতেন, সেটা যে উনিশ শতকের শুরুর বায়রন কীটস শেলী ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের উজ্জ্বল কালের সেটা মেনে খুব আপত্তি কারো হবে না। তিনি ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন আশির দশকের গোড়াতেই। তখন সদ্য তরুণ। তাঁর নিজের তারুণ্যের কারণেই শ্রান্ত পরিশ্রান্ত ইংল্যান্ডকেও তিনি নতুন বলে গ্রহণ করতে পারছেন। যে রোমান্টিকতা তখন অবসিত হতে চলেছে, তিনি তারই দীপ্ত ঔজ্জ্বল্যের কালের প্রভাবে খানিকটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আমার একটা কথা মনে হয়, স্থান কাল সমাজ রাষ্ট্র ইতিহাস ভুলে স্রষ্টাদের তুলনামূলক বিচার করতে গেলে কত বিভ্রান্তি ঘটতে পারে! কালের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতা উনিশ শতকের প্রথমদিকের রোমান্টিক সৃষ্টি থেকে অনেক দূরে অথচ ‘আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল প্রাণের পর’, রবীন্দ্রসৃজনের প্রথম দিকের রচনাতেই প্রাণ ও ঔজ্জ্বল্যের কি উৎসারণই না ঘটিয়েছে। কিন্তু তারপর থেকেই, বলতে গেলে প্রথম থেকেই, কি ধীরে ধীরে তিনি পাখা মেলছেন না? দূরে পক্ষ সঞ্চালনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন আর তাঁর ওপর য়োরোপীয় প্রভাব প্রান্তিক হয়ে যাচ্ছে? হাজির হয়ে যাচ্ছে তাঁর সময়কার উপনিবেশ ভারতবর্ষ আর সুবৃহৎ মহান ভারতবর্ষীয় প্রাচ্যতা। কে মেলাবে এদের? রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনার জন্য এই বক্তৃতা নয়, এখানে সেখানে তার উল্লেখ থাকলেও তা আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কিছুতেই বিকৃত করতে যাব না। শ্রোতাদের ভেবে দেখতে বলি ১৯০১ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে রচিত প্রধানত ‘নৈবেদ্য’ ও ‘গীতাঞ্জলি’র কবিতাগুলি। অপূর্ব এই গান-কবিতার সম্ভারকে নিশ্চয়ই খাঁটি রোমান্টিক কবিতা বলা যায় না। অথচ এইসব কবিতা দিয়েই ১৯১০-এ তৈরি হলো ‘গীতাঞ্জলি’-ই আর এ কবিতাগুলির সঙ্গে ‘নৈবেদ্য’ ও ‘গীতিমাল্যে’র আরো কিছু কবিতা যোগ হয়ে সেগুলির খানিকটা আপতিক খানিকটা খেয়ালি ইংরেজি অনুবাদ শেষ পর্যন্ত ১৯১৩-এ এনে দিল নোবেল প্রাইজ। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার তুলনায় যার দাম আমি একটা কানা কড়ির বেশি দিতে চাইব না। অথচ তাই তাঁকে এনে দিল মহত্ত্ব, বিশ্বস্বীকৃতি আর সেইসঙ্গে তৈরি করল দুঃখজনক একটা বিপত্তি যা রবীন্দ্রবিচারে জীবৎকালে এবং আজ এই একবিংশ শতাব্দীতেও প্রভূত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে আর তাঁকে সরিয়ে নিচ্ছে আমাদের কাছ থেকে। ঠিক যতটা তিনি বিশ্বকবি, ঠিক ততটাই তিনি আমাদের থেকে দূরে। ঘরের মানুষ হয়ে গেছেন বিশ্বের সবার মানুষ, মানে কারোর না। ঘোরের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি নিজেও। গীতাঞ্জলি, নোবেল পুরস্কার ইত্যাদি নিয়ে সম্প্রতি চমৎকার কাজ করেছেন সনৎকুমার সাহা, হাসান ফেরদৌস। তাঁদের বিচার করা কথাগুলি আমি এখানে আর আনতে চাই না- শুধু খেয়াল করুন রবীন্দ্রনাথ আর শুধু একজন বাঙালি কবি নন, ভারতীয় নন, এশীয় নন, তিনি বিশ্বসাহিত্যে পৌঁছে গেছেন। তিনি বিশ্বের মানে য়োরোপের স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন। এই হলো প্রতীচ্য, সেখানকার কল্কে পেলেই বিশ্বস্বীকৃতি। কথা দুটি যেন সমার্থক। উপনিবেশিত আমাদেরও তাতে পরম আহ্লাদ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও পড়ে গেলেন ঘোরের মধ্যে। রটেনস্টাইনের বাড়িতে ইয়েট্স্-এর উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের অনূদিত কবিতা পড়লেন। তার পরের ইতিহাসটা সবার জানা। ইয়েট্স্ একটু সংশোধন করলেন, স্টার্জ মূর খানিকটা হাত লাগালেন। ইয়েট্স্ একটি ভূমিকা লিখলেন, খুব চমৎকার তবে ঠিকঠাক কিনা, একপেশে কিনা আমার সন্দেহ হয়। ইয়েট্স্ তাঁকে ইংরেজি ভাষার কবি বলে স্বীকৃতি দিতে চাইলেন, রবীন্দ্রনাথও তাতে শ্লাঘা অনুভব করলেন, ওঁরা বলছেন, আমি ইংরেজি কবিতার ইতিহাসে জায়গা পাব। তাহলে আমি পারি। কাল এখন প্রমাণ করেছে তিনি ইংরেজি কবিতার কেউ নন। তিনি কেউ নন সেটা তাঁর মতো কা-জ্ঞানসম্পন্ন মহাপ্রতিভার বুঝতে বেশিদিন দেরি হয়নি। এজরা পাউন্ডের রবীন্দ্র-নিন্দা আমরা জানি, তিরিশের দশকে বিনা কারণে ইয়েট্স্ কটূক্তি করলেন, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি জানেন না, বলতে কি কোনো ভারতীয়ই তা জানেন না। অথচ তিনি নিজেকে ইংরেজ বলে ভাবেন।
বিচার করতে করতে এগোতে থাকুন। রবীন্দ্রনাথ সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। খুব বড়ো বড়ো সম্মান পেয়েছেন, ইংল্যান্ড গিয়েছেন, আমেরিকা গিয়েছেন, জার্মানি গিয়েছেন, ল্যাটিন আমেরিকায় গিয়েছেন, রাশিয়া গিয়েছেন, প্রাচ্যের দেশগুলিতে ইরান, জাপান, চীন বাদ রাখেননি কোথাও। এইসব দেশে তাঁর সাহিত্যের স্থায়ী অস্থায়ী প্রভাব লক্ষ করা গেছে। অনুসরণকারী জুটেছে, স্বীকরণ প্রভাব সবই মিলেছে।
আজ একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে একবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমে নতুন আগ্রহ তৈরি হয়েছে তাঁর সৃষ্টির প্রতি, স্বীকার করা হচ্ছে, তাদের উৎকর্ষ মহাদেশীয় সৃষ্টিকেও অতিক্রম করেছে। কিন্তু তিনি কখনো য়োরোপীয় সাহিত্যিক হননি। বিশ্বসাহিত্য বলতে আমি আগে যে মন্তব্য করেছি, ঠিক ঐ অর্থেই আজ তাঁর সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। তার বেশি নয়। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা ভাষায় য়োরোপীয় সাহিত্য লিখেছেন- সুধীন দত্তের এই উক্তিকে আমি অশ্রদ্ধেয় মনে করি।
রবীন্দ্রনাথ অতি দ্রুত গীতাঞ্জলি পর্যায়টা পার হয়ে যান, তবে পর্যায়টা মুছে যায় না। মহীরুহ যেমন তার সব বৃত্তান্ত, চারাগাছ থেকে তার পূর্ণবৃদ্ধি ও বিকাশের ইতিহাস নিজের কোষে কোষে আটকে রাখে, রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও ঘটে তাই।
য়োরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। অস্ট্রীয়-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্জ্য আগ্রাসী হয়ে ওঠে, বিশাল কিন্তু দুর্বল তুরস্ক সাম্রাজ্য নড়বড়ে হয়ে যায়, বলকান রাষ্ট্রগুলো অস্থির উত্তপ্ত হতে থাকে, জাতীয়তার চেতনা উগ্র বিদ্রোহের দিকে যায়, আরবরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, উপনিবেশগুলি হারানোর ভয়ে জার্মানি অস্ট্রিয়া ইতালি, ইংল্যান্ড ফ্রান্স রাশিয়া সবাই শেষ পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধে নেমে পড়ে। ইংরেজের উপনিবেশ ভারতবর্ষ তখন কি করবে? উনিশ শতকীয় শান্তি কোথায় উবে যায়- রবীন্দ্রনাথ লিখে ফেলেন এক একটি গান… আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি; আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে; ও আমার ও দেশের মাটি; সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদের উত্থান, ব্রিটিশ উপনিবেশ রক্ষার মরিয়া চেষ্টায় সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষের লালনপালন আর দীর্ঘস্থায়ী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা সব একসাথে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের ফিরিস্তি দিতে আমি বসিনি, আমরা শুধু জানতে চাইছি, বুঝে নিতে চাইছি, কোনো সাহিত্যিকের একটা বা অনেক তকমা তাঁকে গ্রহণ করার পক্ষে কতটা অন্তরায় হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যেমন তেমনিই থাকছেন, সব সময়েই তাঁকে রবীন্দ্রনাথ বলেই চিনে নেওয়া যাচ্ছে অথচ তিনি নানা রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন যাকে তিনি নিজেই বলেছেন নানা রবীন্দ্রনাথের মেলা। সাহিত্যের গায়ে কেমন করে সময় সমাজ রাষ্ট্রের দাগ লাগে সেটা বোঝা অত্যন্ত জরুরি যে! ১৯০৩-এ রবীন্দ্রনাথ যখন চোখের বালি লেখেন তখন নানা ব্যক্তিগত ঘটনা-দুর্ঘটনায় তিনি শান্তি স্বস্তি সব হারিয়ে ফেলেন। তিনি নিজেই কবুল করেছেন ‘চোখের বালি’র মতো উপন্যাস লিখতে তিনি পীড়িত বোধ করেন- আমারও মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ তাঁর স্মৃতিতে কোথাও থেকে থাকবে ‘চোখের বালি’ লেখার সময়। কিন্তু ১৯০৯-১৯১০ ‘গোরা’ নামে বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয় মহৎ যে উপন্যাসটি তিনি লেখেন, যার নায়ক তাঁর সমবয়সী- সিপাহি বিদ্রোহের কাল- তাতে তিনি দেশ মানুষ সভ্যতা বুঝে নিতে চাইছেন। উপন্যাসের শেষে যে ‘ভারতবর্ষ’ তিনি আপন-সত্যের মধ্যে গড়ে নিতে পারেন- সেটা গোটা বিশ্ব হতে আপত্তি কোথায়? শেষ পর্যন্ত মানুষের একত্ব, বিশ্বের একত্বে গিয়ে তো পৌঁছুতেই পারে।
সময় যতই এগোতে থাকবে ততই রবীন্দ্রনাথ এত বড়ো আর আলাদা হতে থাকবেন যে তাঁকে চেনা কঠিন হয়ে পড়বে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাঁকে গতি, পরিবর্তন সমূহবিনষ্টি, নৃশংসতা, স্বার্থ লোভ দখলদারি সব দেখিয়ে ছাড়ল। কোনোদিক থেকেই আর আগের রবীন্দ্রনাথ থাকলেন না। তবে উপনিবেশ ভারতবর্ষ যুদ্ধ দেখল না। ভাঙাচোরা ইয়োরোপ ধস্ত নষ্ট মানুষ নষ্ট পশ্চিম দেখল। রবীন্দ্রনাথও তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখতে পেলেন না। পশ্চিমের নতুন কবিতা তাঁকে ঠিক টানল না, শিল্প সাহিত্য কিছুই না। তাঁর পৃথিবী ভ্রমণও তাঁকে ঠিক বিষজর্জর পশ্চিম চেনাতে পারল না। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পরের য়োরোপের কবিতায় কথাসাহিত্যে শিল্পে যে ভয়ানক পরিবর্তন ঘটেছে, রবীন্দ্রনাথ তা বাস্তব বলে অনুসরণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। এসব প্রেতচ্ছায়ার মতো তিরিশের কবিদের ওপর ছায়া ফেলেছিল, দেশলগ্নতা উপড়ে ফেলেছিল। কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্য, শিল্পে সেই ধাক্কাটা স্বাভাবিক কারণেই আসেনি।
লেখাটির শিরোনাম দিয়েছি একবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ অথচ এখন পর্যন্ত বোধ হয় একবারও এ নিয়ে একটি কথাও বলা হয়নি। তার প্রধান কারণ এ নিয়ে বাগবিস্তারের কোনো ইচ্ছা আমার নেই। গত শতাব্দীর
’৪৭-এর স্বাধীনতার পরে পাকিস্তানের তেইশটি বছরের মধ্যে প্রথম এক যুগ আমাদের একরকম রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে একরকম মৌন অবলম্বন করতে হয়েছিল। কিন্তু একষট্টি সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ কত বড়ো কবি, বিশ্বকবি কিনা, তাঁকে কবি সার্বভৌম বলা যায় কিনা তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে হয়নি। যাঁকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, যাঁর সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করে থাকতে বলা হতো তাঁকে আমরা দারুণ যুদ্ধে অর্জন করে নিলাম। এ জায়গাটাতে বিস্তারিত আলোচনার কিছু নেই- ধমনিতে যে রক্তস্রোত বয়, তার ভেতর দিয়েই জানা হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথকে।